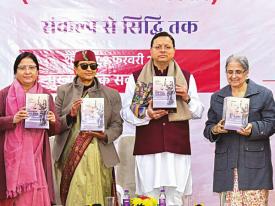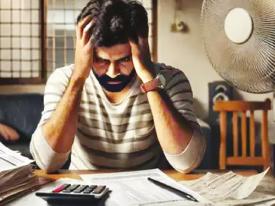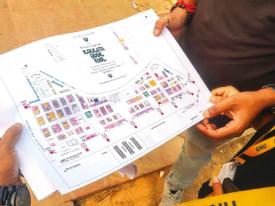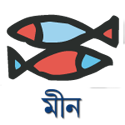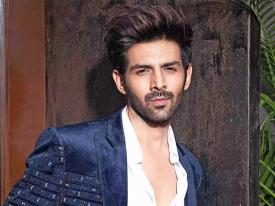কারও কাছ থেকে কোনও দামি উপহার লাভ হতে পারে। অকারণ বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ... বিশদ
বাঙালির সাহিত্য, শিল্প, আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি সবকিছুর মধ্যেই তিনি রয়েছেন। জয়রামবাটীর সারদা মাকে সকলে দুর্গা-জগদ্ধাত্রী মানলেও নামের অর্থের দিক থেকে তিনি সরস্বতী। আবার শারদা অর্থাৎ বাঙালির সব থেকে বড় উৎসবের একচালা দুর্গার সঙ্গেও দেবী আছেন কন্যারূপে। এবার হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা। সেখানেও রয়েছেন সরস্বতী, তবে নদীরূপে। এখন কলকাতায় চলছে আন্তর্জাতিক বইমেলা। সেখানে সরস্বতীর বরপুত্রদের অর্থাৎ সাহিত্যিকদেরই কদর বেশি। জানতে ইচ্ছা হয়, তাঁরা কীভাবে পালন করেন সরস্বতী পুজোর দিনটি? অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়েই শুরু করা যাক। কারণ এই বছর তাঁর জন্মসার্ধশতবর্ষ শুরু হল। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগেকার কথা। ১৯২৫ সালে সরস্বতী পুজোর তারিখ ছিল ২৫ জানুয়ারি। কাশীতে সেই দিনেই অনুষ্ঠিত বিশ্বনাথ লাইব্রেরির নবম বার্ষিক সারস্বত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি।
সদ্য ১২৫ বছর পেরনো সাহিত্যিক বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় আসি। প্রত্যেক বছর এই দিনে তিনি সরস্বতী বিষয়ক একটি স্তব রচনা করতেন। ১৯৭৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি, ঠিক এবছরের মতো সেই দিনও ছিল সরস্বতী পুজো। জীবন সায়াহ্নে সেই রচনায় তিনি লিখেছিলেন, ‘পদ্মাসনা দেবী সরস্বতী,/ আমি ক্ষুদ্র অতি/...ক্ষুদ্র এ প্রণাম...’। তারপরেই তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে সকলকে ছেড়ে চলে যান। দিনটি ছিল ৯ ফেব্রুয়ারি।
সরস্বতীর বন্দনা করেননি এমন কবি বিরল। কেউ কেউ মনে করেন, মহাকবি কালিদাসের নাম সারদাদাস হলে মন্দ হতো না। নানুরের কবি চণ্ডীদাসের পূজিত বাঁশুলী মূর্তিও সরস্বতীর সমান। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির প্রথম দিকেই সরস্বতীবন্দনা করেছেন কবি। সেই দেবীমূর্তির হাতে ছিল জপমালা-বীণা। তাঁর সাদা কাপড় বোঝাতে কবি লিখেছিলেন, ‘শুক্ল ধুতি পরিধান’। এই কাব্যে হুগলির মগরার নাম পাওয়া যায়। যেখানে সরস্বতী পুজো দুর্গাপুজোর মতোই সাড়ম্বরে পালিত হয়।
আসা যাক ‘মেঘনাদবধ কাব্য’প্রসঙ্গে। কবি মধুসূদন এই কাব্য শুরুই করেছিলেন ‘অমৃতভাষিণী’ সরস্বতীর সঙ্গে বলা কথার মাধ্যমে। হিন্দু বা প্রেসিডেন্সির ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষের ‘The Shair and Other Poems’ প্রকাশিত হয় ১৮৩০ সালে। সেখানে দেবীকে ‘Fair goddess of the arts’ নাম দিয়ে তিনি অঞ্জলি দিয়েছেন ‘These offerings of our hearts’। এ তো গেল বাঙালির ইংরেজিতে বাণীবন্দনা। এবার আসি খোদ ইংরেজ সাহেবের কথায়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স লিখেছিলেন ‘Hymns to Sereswaty’ নামে বিরাট এক সরস্বতীস্তোত্র। শুধুমাত্র সাহেবসুবো কেন? রাজা মহারাজারাও সারদাগীতি লিখেছিলেন। কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ উনিশ শতকে সরস্বতীকে নিয়ে একাধিক ভক্তিগান বেঁধেছেন। একটিতে দেবীর পাদপদ্মে ভোমরা হয়ে মধু পান করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।
কবিতার কথা শুরু করেছিলাম বনফুলকে দিয়ে। তাঁরই সমবয়সি কাজী নজরুলকে দিয়ে শেষ করি। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত ‘চন্দ্রবিন্দু’ বইটির শুরুই হয়েছে সরস্বতীর দুটি গান দিয়ে। ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতেই লিখেছিলেন সে দুটি গান। প্রথমটিতে ব্রহ্ম-বিদ্যা ও শিব-সরস্বতী নামে দেবীর জয়গান করেছেন। পরেরটিতে নির্ভয়ে বীণায় ঝংকার দিতে বলে জানিয়েছেন করুণ আর্তি—‘মৃতজনে সংগীত অমৃত দাও মা’।
আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসি। এবার আসি বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গল্পকথায়। রবীন্দ্রনাথের মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার কী কাণ্ডটাই না করেছিলেন! বাড়ির সরস্বতী প্রতিমার উপর দক্ষিণার টাকা গায়ের জোরে ছুড়ে দেন। তাতে ঠাকুরের মুকুট যায় ভেঙে। বড় হয়ে বাল্যকথায় অনুতপ্ত লেখক লিখেছেন, তখন হাতে হাতে শাস্তি না পেলেও পরবর্তীতে ফল ভোগ করতে হয়েছে। বুদ্ধি ও স্মৃতি যেতে বসেছিল তাঁর। সে কারণেই নাকি চাকরির সর্বোচ্চ পদ পাননি—‘সরস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে পারতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হ’ল না!’
এবার রবিকথা, সব ব্যাপারে তাঁর ছোট ভাই চলেই আসেন। ঠাকুরবাড়িতেই তাঁর লেখা ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ নাটকের অভিনয় হয়েছিল ২৬ জানুয়ারি ১৮৮১ সালে। বাল্মীকির চরিত্রাভিনেতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বরদাত্রী সরস্বতীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তিনি ছিলেন প্রতিভাসুন্দরী দেবী। রবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে প্রতিভা একাধারে রবির গানের ছাত্রী, আবার তাঁর গানের স্বরলিপিকারও। মাঘোৎসবের মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করা নারী ছিলেন তিনি। যাই হোক প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সেদিন প্রথম অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ এবং বনেদি গৃহস্থকন্যারূপে প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তার দর্শক। রবির সুর দেওয়া বঙ্কিমী বন্দেমাতরম্ গানের স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন প্রতিভা। প্রথম বাঙালি মহিলা স্বরলিপিকার, সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে সত্যি করেই তিনি যেন রাগরাগিণী ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী।
প্রবন্ধ ও নাটকের কথা বলা হল। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত পরশুরাম রাজশেখর বসুর ‘ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প’-এর বইটিকে কি বাকি রাখা যায়? সেখানে ‘লক্ষ্মীর বাহন’নামে একটি গল্পের চরিত্রের নাম ছিল সরস্বতীনাথ।
দেবীর কথা লিখব এদিকে মহিলা সাহিত্যিকদের কথা লিখব না তা হয় না। এই বছর ১৪ জানুয়ারি এমন একজন সাহিত্যিকের শতবর্ষ শুরু হয়েছে, যাঁর নামটাই হল সরস্বতীর অষ্টোত্তর শতনামের অন্যতম একটি নাম। হ্যাঁ, তিনি হলেন ‘হাজার চুরাশির মা’ মহাশ্বেতা দেবী।
শিল্পী নন্দলাল বসুর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রূপাবলী’র প্রচ্ছদে স্বয়ং চিত্রকরের আঁকা সরস্বতীকেও আমরা ভুলতে পারি না। ভোলা যাবে না বর্তমান পত্রিকায় আঁকা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরস্বতীকে। এবার আসব বাগ্দেবীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বাদানুবাদে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসেও সরস্বতীর কথা এসেছে। মৃণালিনী, রজনী, দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠ, সীতারাম-এ সরস্বতীর কথা থাকলেও আমরা চলে যাব তাঁর কলেজজীবনে। যে সময় তিনি ছিলেন কবি। ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় লিখে সেইসময় তিনজন কলেজছাত্র রংপুরের দু’জন জমিদারের দেওয়া পুরস্কার পান। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী, হিন্দু কলেজের ছাত্র নীলদর্পণ-এর লেখক দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কলেজের বঙ্কিম। তাঁদের তিনজনের কবিতা প্রতিযোগিতা সেইসময় ‘কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ’ নামে পরিচিতি পায়। তিলোত্তমা-দুর্গা নয়, সরস্বতীকে নিয়েই তাঁদের সেই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। দ্বারকানাথই প্রথম লিখেছিলেন ‘সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ’। এর জবাবে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের কবিতার পরে আবার প্রকাশিত হয় দ্বারকানাথের লেখা ‘সরস্বতীর খেদ ও দ্বিতীয় বরপুত্রের সহিত কথোপকথন’। সেখানে সেই দ্বিতীয় বরপুত্র দ্বারকানাথকে সরস্বতীর কাছ থেকে ‘গ্রামের কেশরী’ উপাধি পেতে দেখি আমরা।
বর্তমানে শিক্ষাদেবীর পুজোকে কেন্দ্র করে শিক্ষালয়ে নানারকম অশান্তির কথা শোনা যায়। কিন্তু ১৯২৮ সালে ব্রাহ্ম ধর্মভুক্ত সিটি কলেজের রামমোহন হোস্টেলের সরস্বতী পুজো নিয়ে যা হয়েছিল তা এককথায় অভূতপূর্ব। সেখানে কয়েকজন হিন্দু ছাত্র হঠাৎ পুজো শুরু করলে হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের বিরোধ চরমে ওঠে। হস্টেল সুপার ব্রজসুন্দর রায়, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র নাকি নিগৃহীত হন। ধীরে ধীরে তা সামাজিক আন্দোলনের রূপ নেয়। একটি পুজোকে কেন্দ্র করে দেশের রবি এবং দেশনায়ক সুভাষ নাকি পরস্পরের বিরুদ্ধে নাম না করে বচনে ও লিখনে মত প্রকাশ করেছিলেন। মাঘের পুজোর ঘটনার রেশ ছিল রবির জন্মমাস মে পর্যন্ত। এই আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়া, তার ফলে ঘটা অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার জন্য কিন্তু আবার চাকরি হারাতে হয় কবি জীবনানন্দকে।
যাই হোক, আমরা এবার মেতে যাব পুজোর আনন্দে। আচ্ছা, মর্তের সরস্বতী পুজোর তো অনেক অভিজ্ঞতা। স্বর্গে বা ইন্দ্রলোকে কীভাবে পুজো হয় সেই কল্পনার কথা জানা যাবে ১৮৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা পড়লে। জানি হয়তো অনেকেই এ প্রস্তাবে রাজি হবেন না। স্ক্রিনে অহরহ চলে আসা রিলস দেখা বাঙালির কেউ কেউ পারলে সরস্বতীর হাতেই মোবাইল ধরায়! তবু জেনে নিই কবির ‘কবিতাবলী’র প্রথম খণ্ডের প্রথম কবিতা ‘ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পুজো’র কথা। চারদিকে বীণাবাদনে এক সুরমুখর পরিবেশ। ইন্দ্রভবনে তখন উপস্থিত হয়েছেন ষড়ঋতুকে সঙ্গে নিয়ে কামদেব, মহাদেব, লক্ষ্মীসহ বাসুদেব, নারদ, কিন্নর, গন্ধর্বরা। ব্রহ্মার কপাল থেকে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর আবির্ভাব হল। ইন্দ্র দেবীর অর্চনা করলেন, পাঁচমুখে শিব গাইলেন বেদগান, ব্রহ্মা দেবীর হাতে তুলে দিলেন সাদা পদ্ম। বীণাসঙ্গতে, বেদসঙ্গীতে, দেবতাদের জয়গানে মর্তভারতও আনন্দে গেল ভেসে। কবি আশা করেছেন যে ভারতীর আলোতেই ভারতের আঁধার ঘুচবে। এর বহুকাল পরে দেবীর আরাধনা করে আদিকবি হয়ে যাওয়া বাল্মীকি, গ্রিক মহাকবি হোমার, মহাভারতকার ব্যাসদেব, মিলটনের মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন কবি। তারপর দেবীর কৃপায় স্বনামধন্য হলেন ভারতের কালিদাস, ইংল্যান্ডের শেক্সপিয়র। তাঁরাই তো যুগে যুগে যুগোত্তীর্ণ হয়ে সকল দেশকালের বেড়াকে তুলে দেন। সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন। সেই জ্ঞানের জ্যোতি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন বলেই তো দেবীর নাম সরস্বতী।