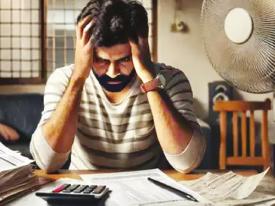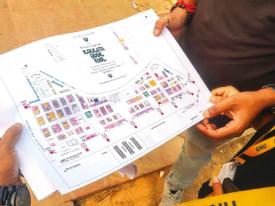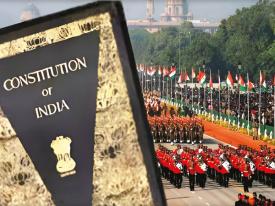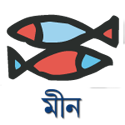প্রায় সম্পূর্ণ কাজে শেষ মুহূর্তে বাধা পড়ায় বিচলিত হয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে ... বিশদ
সেই ট্র্যাডিশন চলছে আজও। পাঁচ হাজার বছর পরও দিনরাত বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমের হেডিং দেখে ভিডিও বা খবর পড়তে উদগ্রীব হয়ে, শেষে কি না হচ্ছে অশ্বডিম্ব প্রসব! প্রতিমুহূর্তে বোকা বনছি আমরা। ঠিক যেমন বোকাটি বনেছিলেন দ্রোণাচার্য, পাণ্ডবদের কৌশলী (পড়ুন অপকৌশলী) শব্দ তিরন্দাজিতে। রীতিমতো বধ হয়ে খেসারত দিতে হয়েছিল তাঁকে।
না হলে দশকের পর দশক ধরে বাংলায় সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে বছরভর এক-দু’জন করে ভর্তি থাকা জি বি সিনড্রম নিয়ে দিনরাত মিডিয়ায় তারস্বর চেঁচামেচি শুনে উচ্চশিক্ষিত বধূও খাবার টেবিলে স্বামীকে শুধোন, ‘ঠিক বলছ তো? বলছ, আতঙ্কের কারণ নেই? আমাদের পরমটা সারা বছর অসুখবিসুখে কাহিল। ওকে আবার এইসব হলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।’
খাওয়া শেষ করে ব্যাগ গোছাচ্ছিলেন সন্দীপন। পেশায় ডাক্তার। ফোন এসে গিয়েছে। ছুটতে হবে হাসপাতালে। উদ্বিগ্ন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ‘এই জন্য দেশটার কিছু হওয়া মুশকিল। ছাইপাঁশ দেখছ দিনরাত। আমাদের গরিব দেশে বছরে তিন লাখ বাচ্চা মারা যায় শুধু ডায়ারিয়াতে। ডায়ারিয়া নিয়ে খবর দেখালে দেখতে? পাত্তাই দিতে না। বছরে দেশে তিন লাখের বেশি মানুষ মারছে টিবি। টিবি নিয়ে খবর দেখালে দেখতে? গুরুত্বই দিতে না। সেখানে যা দেখছ, সেটা পুনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা। কতজনের হয় জি বি সিনড্রোম? লাখে ১ জনেরও নয়। এরপরও বলছি, যার যায়, তাঁর যায়। যে কোনও মৃত্যুই অত্যন্ত দুঃখের। তাসত্ত্বেও বলছি, জি বি সিনড্রোম নিয়ে অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এমন নয় যে হঠাৎ করে এই রোগের উদয় হল। আমরা বছরভর এক-দু’জন করে এমন রোগী পেতেই থাকি!’
এই পর্বের কিছুদিন আগেই ছড়ানো চলল এইচএমপিভি বা হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক। তখন ডাঃ অপূর্ব ঘোষের মতো প্রথম সারির বিশেষজ্ঞরাই বারবার বলেছেন, ‘‘এটা মোটেই আজকেই হঠাৎ উদয় হওয়া কোনও ভাইরাস নয়। আগে জ্বরের কারণ কী দেখা হতো না। বলা হতো, ভাইরাল ফিভার হয়েছে। সিংহভাগ ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল, বিশ্রাম, জল আর ফল—এই সহজ সরল নিদানেই সেরে যেত। সেরে যায়ও।
শুধু আমরা চিকিৎসকরাই জানতাম রাইনো, ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, মেটানিউমো সমেত বিভিন্ন ভাইরাস হয়তো সেই জ্বরের কারণ। তা কিন্তু সাধারণ মানুষের না জানলেও চলে। তাঁদের তো সুস্থ থাকা, সুস্থ হওয়া নিয়েই কাজ। এখন ভাইরাল বা রেসপিরেটরি প্যানেলের মতো দামি পরীক্ষা এসেছে। জ্বরের কারণ ভাইরাসগুলির নাম জানা যাচ্ছে। আর রে রে করে ছড়ানো চলছে উদ্বেগ—আতঙ্ক!
আতঙ্কের খেসারতও দিতে হচ্ছে। কড়কড়ে ১৮ থেকে ২১ হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে এখন শুধু ভাইরাল বা রেসপিরেটরি প্যানেল টেস্ট করতেই! জটিল ও ব্যতিক্রমী রোগ লক্ষণ ছাড়া যার কোনও দরকারই নেই। ডাক্তাররাই বলছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্যানেল জেনে চিকিৎসা এবং প্যানেল ছাড়া চিকিৎসার মধ্যে কোনও ফারাক নেই।
জানেন কি, অতিরঞ্জিত খবর ছড়িয়ে হাজার হাজার মানুষকে আতঙ্কিত করার ‘অসুখ’-এর একটি নামও দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববন্দিত জার্নাল লাইব্রেরি পাবমেডে ঠাঁই পাওয়া এক গবেষণাপত্রে এর নাম দেওয়া হয়েছে‘ইনফরমেশন ডিজঅর্ডার সিনড্রোম’!
কী এই সিনড্রোম? জার্নালে বলা হয়েছে, ‘‘information disorder syndrome is the sharing or developing false information with or without the intent of harming and they are categorized as misinformation, disinformation and malinformation’’ (জেএনএমএ ২০২০ এপ্রিল)। এখানেই শেষ নয়, যাঁরা এই ‘মহান’ কাজটি করেন, তাঁদের তিনটে শ্রেণিতেও ভাগ করা হয়েছে। গ্রেড ১—যখন মানুষের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো বা শেয়ার করা হয়। গ্রেড ২—যখন আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে না। গ্রেড তিন—যখন কেউ সব জেনেবুঝে মিথ্যা তথ্য ছড়াতে থাকেন।
মহাভারতের যুদ্ধদৃশ্য কল্পনা করুন। দ্রোণাচার্যকে হারানোই যাচ্ছে না। পাণ্ডবরা যে অস্ত্রই ব্যবহার করছেন, সবই ব্যর্থ, সবই ব্যর্থ! ড্যামেজ কন্ট্রোলের শ্রেষ্ঠ কারিগর শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি দিলেন গুরুদেবকে কুপকাত করার জন্য একটি সেমিমিথ্যে বলতে হবে। আর তা বলাতে হবে এমন একজনকে দিয়ে, চরম শত্রুও যাঁকে কোনওদিন মিথ্যুক ভাবে না। এরপরই দ্রোণের প্রিয় পুত্র অশ্বথামা ‘হত’ হয়েছে, এমন একটি হেডিং ছড়িয়ে দিলেন যুধিষ্ঠির। দ্রোণ নিমেষে হয়ে পড়লেন হতাশ, অবসন্ন, বিপর্যস্ত। যুদ্ধ কেন, জীবনের প্রতিই তাঁর স্পৃহা উঠে গেল। সেই সুযোগে...।
একটি ভুল তথ্যকে সত্যির মতো পরিবেশন করে শেষে আবার নিজেকে কিছুটা নিষ্কলুষ রাখতে ‘ইতি গজ’ শব্দটি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেছিলেন ‘সত্যবাদী’। ততক্ষণে কাজ হাসিল। ঠিক তেমনই আমরাও ভুল ও অতিরঞ্জিত তথ্যের ফাঁদে পা দিয়ে নিমেষে উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। যখন খবর পড়া শেষ করি, ভাবি কী বোকাটাই না বনলাম।
হ্যাঁ, এমন বোকা আমরা রোজ হচ্ছি। না হলে দেশের মধ্যে একমাত্র পুনেতে স্থানীয় আউটব্রেক হয়ে ১১১ জন জি বি সিনড্রমে অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্নতার যোগ তৈরি হয় কীভাবে? সচেতন করার জন্য ক’টা খবর হয়! বিশেষত, বাংলায় যেখানে এমন কোনও আউটব্রেকই হয়নি। হঠাৎ করে এই বিরল রোগে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়েনি। হু হু করে করোনার মতো একজনের থেকে আরেকজনের শরীরে রোগ ছড়িয়েও যায়নি। তা সত্ত্বেও কেউ যেই আমাদের বিপন্নতা বোধে সুড়সুড়ি দিল, আমরাও হয়ে পড়লাম ঘায়েল। দ্রোণের মতোই অসহায় আমরা পুত্রের নাম শুনেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। পরে জানলাম পুত্র নয়, আসলে মারা গিয়েছিল ‘গজ’ অশ্বথামা!
এ প্রসঙ্গেই দুটি বিষয় বলতেই হয়। আমরা ভাবি, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার অনলাইন মিডিয়া মাধ্যমের দৌলতে এখন যা-ই দেখানো হচ্ছে, তারই বুঝি ব্যাপক প্রভাব। তা-ই বুঝি মানুষ বিশ্বাস করে। তা বুঝেই বুঝি মানুষ চলে।
আমরা ভুল ভাবি। অনলাইন মাধ্যম কথা বলা, ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে বড়জোর আর একটু স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু, ভরসার জায়গা? বিশ্বাসের জায়গা? এখনও কিন্তু সেই প্রিন্ট। না হলে তো আতঙ্কের ত্র্যহস্পর্শে রোগী নিয়ে বাড়ির বাইরেই বেরতেন না প্রিয়জন। কোনও বিরল রোগে যদি আক্রান্ত হয়ে যান!
রোজ রাজ্যের ২৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৪টি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ ডাক্তার দেখান। একদিন যে কোনও একটি জায়গার আউটডোরে যান। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে প্রশ্ন করেই দেখুন না, তাঁরা এইসব রোগ নিয়ে আতঙ্কের খবরে কতটা প্রভাবিত হয়েছে। সিংহভাগই আপনাকে বলবেন, ‘নামই শুনিনি’! রোজকার সমস্যায় জর্জরিত তাঁরা। নিজের রোগীকে দেখিয়ে চটপট ট্রেন, বাস বা অ্যাম্বুলেন্সে চেপে বাড়িমুখো হতে পারলে বাঁচেন। আতঙ্কে শামিল হওয়ার তাঁদের না আছে সময়, না সুযোগ!
আর সেটাই বাঁচোয়া। শহুরে শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিতদের বেডরুম-ড্রয়িংরুমে ঝড় তুলে, চেনা চিকিৎসককে ৭-৮ বার করে ফোন করে, স্কুলের অভিভাবকদের গ্রুপে উদ্বেগ বিলি করে, ছোটখাট জ্বর-সর্দি-কাশিতে ‘বড় ডাক্তার’কে দেখিয়ে (এমনকী সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিয়ে), গণ্ডাখানেক দামি টেস্ট করে ও হাজার পঞ্চাশের গচ্চায় ইতি টানেন আতঙ্কের।
ততদিনে আতঙ্ক আরও নতুন কোনও কম চেনা বিচিত্র অসুখের ছদ্মবেশী রূপ ধরেছে। আর মুচকি হাসছে টেস্টিং ল্যাব, মুচকি হাসছেন ওষুধ নির্মাতারা, প্রাইভেট হাসপাতালের কর্তারা। সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হল, এখন যেন যাঁরা যত বেশি শিক্ষিত, তাঁরা তত বেশি আতঙ্কিত হচ্ছেন! ছোট পরিবারের বিপন্নতাবোধ থেকেই বোধহয়।
দ্বিতীয় যে কথাটি না বললেই নয়, ন্যাড়া বেলতলায় বারবার যান না। টুইস্ট করা সংবাদের বাইরে ‘ধাঁধা’, ভিতরটা ফাঁপা—বারবার এমন কাঁচকলাটি পেয়ে একটা সময় মানুষ চালাকিটা ধরেই ফেলে। বারবার রোগ নিয়ে আতঙ্কের খবরের কানাগলির শেষে একদিন বামালসমেত ধরা পড়ে চোর! মানুষও ‘সানসনি’ হেডিং-এ পড়ে, ভিতরে কিছু না পেয়ে একসময় বিরক্ত হয়ে সেইসব খবর থেকে মনই উঠিয়ে নেয়। নিচ্ছেও। ভুললে চলবে না, বহু ব্যবহারে জরুরি অস্ত্রও হয়ে পড়ে ভোঁতা—অকেজো। তখন আর কেউ দ্রোণাচার্য হতেই চাইবেন না। অনেকে এখনই চাইছেন না।