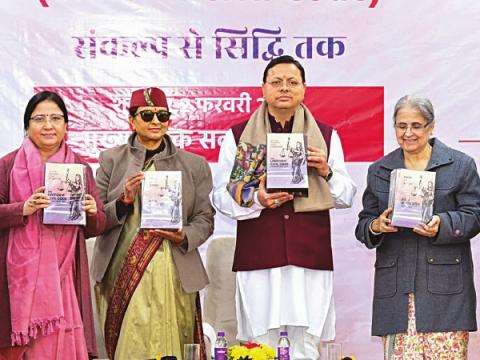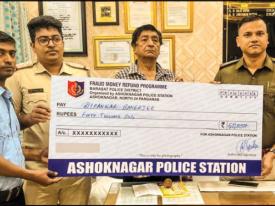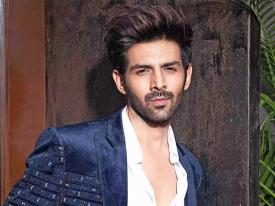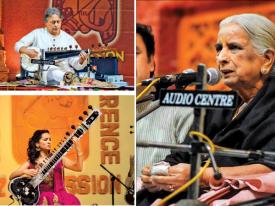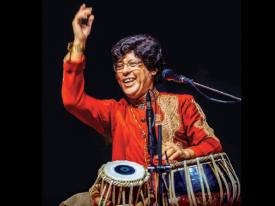কলকাতা, বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২২ মাঘ ১৪৩১
সংসার বা কর্পোরেটের বাজেটে ধাপ্পা চলে না
শান্তনু দত্তগুপ্ত

বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর তারপর থেকেই সাধু সাধু রব উঠে গিয়েছে। এমন বাজেট নাকি স্বাধীনতার পর এই প্রথম। নরেন্দ্র মোদি মা লক্ষ্মীকে আম জনতার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। আয়কর সংক্রান্ত যে ঘোষণা নির্মলাদেবী করেছেন, তাতে সত্যিই মাসে এক লক্ষ টাকা রোজগেরেদের অনেকটা সুরাহা হবে। কিন্তু এর মাঝেও একটা কঠিন বাস্তব লুকিয়ে আছে। তা হল, বাজেট মানে কিন্তু শুধু আয়করের স্ল্যাব ঘোষণা বা রিবেট দেওয়া নয়। এর পরিধি ঢের বেশি। বাজেটের আক্ষরিক অর্থ যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা ‘আর্থিক অনুশাসন’। ছোট-বড় সর্বত্র এই অনুশাসনটা দরকার। কোথাও বহর ছোট হয়, কোথাও বড়। একবার নিজেদের সংসারের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, আর্থিক অনুশাসন এখানেও পুরোদস্তুর রয়েছে। মাসের শুরুটা ভাবুন। প্রথমেই আমরা একটা হিসেব কষতে বসি। কেমন সেই হিসেব? মোদ্দা ব্যাপারটা হল, বেতন পাওয়ার পর হাতে কত টাকা আছে, আর তার ভিত্তিতে খরচ কী হবে। মাসের বাজার, গ্যাস, পরিচারিকা, বাড়ি ভাড়া বা ফ্ল্যাটের মেইন্টেনেন্স, ছেলেমেয়ের স্কুলের খরচ, যাতায়াত, ওষুধ এবং ইএমআই। এটা মাসের শুরুতেই আমাদের দিয়ে ফেলতে হয়। তারপর কিছু টাকা সরিয়ে রাখতে হয় বিয়েবাড়ি বা অন্য কোনও নিমন্ত্রণের জন্য। বাকি যা থাকল, তা হিসেবের বাইরে খরচযোগ্য, কিংবা ওটাই সঞ্চয়। আমরা, অর্থাৎ আম জনতা প্রত্যেক মাসেই বাজেট করে চলেছি। সোজা কথায়, আর্থিক অনুশাসনে নিজেদের বেঁধে ফেলছি। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বাজেট করছে মানে, সেও কিন্তু নিজের প্রশাসনকে আর্থিক অনুশাসনের মধ্যেই রাখতে চাইছে। তার মধ্যে যেমন আছে আয়ের সংস্থান, ঠিক তেমনই ব্যয়ের হিসেব। বছর শেষে ব্যালান্স শিট তাকে মেলাতেই হবে। একটা সরকারের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ যদি আমার-আপনার সংসার হয়, তাহলে আর একটু বড় ছাঁচ অবশ্যই কর্পোরেট সংস্থা। উল্টে বলা যায়, তাদের সঙ্গেই মিলটা সবচেয়ে বেশি। একটা কোম্পানির সঙ্গে সরকারি বাজেট প্রক্রিয়ার খুব একটা ফারাক নেই বললেই চলে। পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড—‘বাজেট প্রক্রিয়া’। বাজেটের ‘প্রয়োগ’ নয় কিন্তু! কারণ, প্রয়োগের শক্ত জমিতে দাঁড়ালে একটি মাঝারি মাপের সংস্থাকেও এতটুকু ফাঁক রাখলে চলে না। সেটাই সরকারি বাজেটে বিস্তর থাকে। কীভাবে? তলিয়ে দেখা যাক।
ধরে নিলাম, ‘ক’ নামে একটি সংস্থা আছে। সেখানে ৩০০ লোক কাজ করে। প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকা তাদের টার্নওভার। তাদের ম্যানেজমেন্ট হল সরকার, আর কর্মীরা হল নাগরিক। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন অর্থবর্ষের শুরুতেই আয়-ব্যয়ের হিসেব করে, বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করে, ‘ক’কেও তাই করতে হয়। প্রথমেই দেখতে হয়, ফেলে আসা বছরে তার উৎপাদন কিংবা পরিষেবার বহর কতটা ছিল, মার্কেটে ডিমান্ড কী ছিল, আয় কেমন হয়েছে, আর ব্যয়ই বা কতটা। অর্থাৎ, শুরুতেই লাভ অথবা লোকসানের হিসেবটা হয়ে যায়। সেই অনুযায়ী আগামী বছরের জন্য টার্গেট সেট করতে হয় তাকে। যাবতীয় রিস্ক ফ্যাক্টরও এর মধ্যে ধরা থাকে। বছরভরের রানিং কস্ট মেপে নিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় আয়ের টার্গেট। খরচ কেমন হয়? দু’ধরনের—এককালীন এবং মাসের। কোন কোন দপ্তরের জন্য এককালীন টাকা লাগবে, সেটার হিসেব কষা হয় আগে। তারপর কর্মীদের বেতন, অফিস চালানোর জন্য ইলেকট্রিক বিল, মেশিন সহ যাবতীয় মেইন্টেনেন্স খরচের মাসিক হিসেব। সেই মতো বরাদ্দ হয় অর্থ। কোন অ্যাকাউন্ট থেকে কোন খাতের টাকা যাবে, সেটা ঠিক করে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে হয়। আর এক দফার বাজেট করতে হয় দূরেরটা ভেবে। যেমন, ৩০ কোটি টাকা দামের যে মেশিন উৎপাদন করছে, সেটা তো সারা জীবন চলবে না! ধরা যাক, আজ থেকে ১০ বছর পর তার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু এই ১০টি বছর ধরেই একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক হিসেব কষে ওই খাতে সরিয়ে রাখতে হয়। এটাও কোম্পানি বাজেটের একটা বড় অংশ। সরকারের বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে একে পরিকাঠামো খাতে খরচ বা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলে ভাবা যেতেই পারে। আর নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়াটাকে কর্মীদের বেতন, স্বাস্থ্যবিমা, বোনাস ভেবে নিলে খুব ভুল হবে না। কিন্তু সরকারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একটি দায়িত্বশীল সংস্থার ফারাক কোথায় হয়? হঠাৎ ১০০ দিনের কাজের টাকা সরকার বন্ধ করে দিলে আম জনতা সংসদে ভাঙচুর চালায় না। কিন্তু সংস্থার বেতন বন্ধ হয়ে গেলে? কর্মীরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দেখিয়ে রোগী হাসপাতালে বেড না পেলে ঘটিবাটি বেচেও বাড়তি টাকা দিয়ে সে নার্সিংহোমে ভর্তি হবে। কর্পোরেট মেডিক্লেমের টাকা না পেলে কিন্তু কর্মী তার সংস্থার ম্যানেজমেন্টের কেবিনের দরজা ভেঙে দিয়ে আসতে দু’বার ভাববে না! নির্মলা সীতারামন গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারবেন, চলতি অর্থবর্ষে সরকারের আয়ের ২৪ শতাংশ এসেছে ঋণ থেকে। কিন্তু একটি সংস্থা যদি তার ৫০ কোটি টাকা আয়ের ১২ কোটি টাকা ঋণ দেখায়, কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে লাল বাতি জ্বলে যাবে। নির্মলাদেবী বাড়তি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলবেন, ‘টাকা তো দুর্বল হচ্ছে না! ডলার শক্তিশালী হচ্ছে।’ কিন্তু ‘ক’ সংস্থাটিকে ওই শক্তিশালী ডলার দিয়েই বিদেশ থেকে কাঁচামাল কিনতে হবে। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়বে। অথচ মার্কেটে চাহিদা না থাকলে পণ্যের দামও সে বাড়াতে পারবে না। সোজা কথায়, লাভ কমবে এবং লোকসান বাড়বে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের করের টাকা দিয়েই সরকার আমাদের জন্য ঘোষিত প্রকল্পের বরাদ্দ ঠিক করে। কোম্পানিকে কিন্তু তার পণ্য বা পরিষেবা বাজারে বেচেই কর্মীদের জন্য বেতন জোগাড় করতে হবে!
এই বিরাট তালিকা ধরে পার্থক্য বোঝানোর কারণ কী? একটাই—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, সরকারেরটা হল দায়। আর সংস্থার? দায়বদ্ধতা। সরকার একটা প্রকল্প ঘোষণা করে তা বেমালুম চেপে যেতে পারে। বরাদ্দ তো হয়েই রয়েছে। প্রকল্প কার্যকর না হলে ওই টাকাটা সরকারের কোষাগারে থেকে যাবে। এবার সেটা দিয়ে অর্থবর্ষের শেষে নির্দ্বিধায় বাজেট ঘাটতি কম দেখানো সম্ভব। কিংবা কোনও রাজ্যে যদি ভোট আসন্ন হয়, তাদের জন্য আলাদা প্যাকেজে সেটাই টাকা ‘সাইফন’ করে দিতেও অসুবিধা হবে না। অর্থাৎ, এক প্রকল্পের টাকা অন্য প্রকল্পে লেগে গেল। উল্টে ভোটেও নম্বর বাড়ল। প্রতিশ্রুতির ধাপ্পা না দিতে পারলে এই টাকাটা কি উঠবে? তার উপর লাগাতার ভোটের ঘোষণা চলছে... আড়াই হাজার টাকা মহিলাদের ভাতা, বাসে ভাড়া লাগবে না, বিদ্যুৎ ফ্রি... কোথা থেকে আসবে এসবের খরচ? আকাশ থেকে তো পড়বে না। বিজেপি, কংগ্রেস বা আম আদমি পার্টি নিজেদের পকেট থেকেও দেবে না। তার মানে, অন্য কোনও খাতের বরাদ্দ চুপিসারে ঢুকে যাবে রাজনীতিতে। তাই নয় কি?
এবারের বাজেট নরেন্দ্র মোদিকে দিল্লি ভোটে ডিভিডেন্ড দেবে বলেই মনে করছে বিজেপি। রাজধানীর ভোটারদের একটা বড় অংশের মাসিক আয় ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকার বেশি। এর নীচের চাকরিজীবীদের এমনিতেই এতদিন নতুন কাঠামোয় আয়কর দিতে হতো না। এবার ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের নাগরিকরাও এই সুবিধা পাবেন। মোদি সরকারের ইঙ্গিত এবার স্পষ্ট, যা করার করে দিয়েছি। এবার পালা মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের। এখন খরচ করুক! মোবাইল ফোন কিনুক, টিভি, ফ্রিজ, গয়না, গাড়ি, বাড়ি... মাসে ৭-৮ হাজার টাকায় এইসবের ইএমআই তো হয়েই যাবে। তাহলেই তো অর্থনীতির চাকা ঘুরবে। কিন্তু পেট্রল-ডিজেলের দামের জন্য সব্জি, মাছ এবং অন্যান্য নিত্যপণ্যের পরিবহণ খরচ বাড়ছে! সঙ্গে রয়েছে আনুষঙ্গিক আরও কত খরচ। সেই কারণেই তো মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। তার উপর জিএসটির বোঝা। একই জিনিসের রূপ বদলে জিএসটি বেড়ে যাচ্ছে। চালে জিএসটি, খাতায়, পেনে, শিশুর দুধে, বিমায়, ওষুধেও জিএসটি। লাভের গুড় তো শেষমেশ সরকারই খেয়ে যাবে। যে প্রেশারের ওষুধ এক বছর আগেও ৮৫-৯০ টাকা ছিল, সেটাই এখন ১২৫ টাকা। যে চালের দাম ৪০ টাকা কেজি ছিল, সেটা এখন ৪৮ টাকা। কিন্তু এই এক বছরে মূল্যবৃদ্ধির লাফের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আয় পাল্লা দিতে পারছে কি? যে মানুষটা ২০১৪ সালের মতো এখনও হাজার টাকা পেনশন পান, তাঁর ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হবে কীভাবে? যাঁরা বেশি টাকা আয় করেন, তাঁরা ছাড়া অন্যদের কি ভোগ্যপণ্য কেনার অধিকার নেই? সমাজে, সরকারে, অর্থনীতিতে তাঁদের কি একেবারেই কোনও ভূমিকা নেই? সরকারের এসবে কিছুই আসে যায় না। জাহান্নমে যাক সাধারণ মানুষ। শুধু একবার উঁকি মেরে দেখে নিতে হবে, ওই মানুষটির রাজ্যে কাছাকাছি কোনও সময়ে ভোট আছে কি না। করছাড় দিয়ে যদি এক লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়, তাহলে জানবেন, সরকার আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে এই টাকাটা কোথা থেকে ভরপাই হবে। প্রশ্ন হল, এই ক্ষতি কে পুষিয়ে দেবে? আমরা। আম জনতা। আমাদের করের টাকাতেই জনপ্রতিনিধিদের মাইনে বাড়বে, তাঁরা গাড়ি-বাড়ি পাবেন, তেল খরচ, সারা জীবনের জন্য ফ্রি গ্যাস সিলিন্ডার এবং পেনশন। আর সবিতা বাউরি উজ্জ্বলার কানেকশন করানোর পর ফিরে যাবেন সেই কাঠের জ্বালানিতে। গ্যাসের সিলিন্ডার কেনার টাকাটাই যে তাঁর কাছে নেই! বছর পঁচিশের অমিত বিশ্বাস একের পর এক দরজায় কড়া নাড়বেন চাকরির আশায়। সরকার কিংবা বেসরকারি... বোর্ড ঝুলবে ‘নো ভ্যাকেন্সি’র। তখন তাঁর কানে বাজবে একটা বাজেট ঘোষণা... ২ কোটি ৯০ লক্ষ চাকরির।
ধরে নিলাম, ‘ক’ নামে একটি সংস্থা আছে। সেখানে ৩০০ লোক কাজ করে। প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকা তাদের টার্নওভার। তাদের ম্যানেজমেন্ট হল সরকার, আর কর্মীরা হল নাগরিক। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন অর্থবর্ষের শুরুতেই আয়-ব্যয়ের হিসেব করে, বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করে, ‘ক’কেও তাই করতে হয়। প্রথমেই দেখতে হয়, ফেলে আসা বছরে তার উৎপাদন কিংবা পরিষেবার বহর কতটা ছিল, মার্কেটে ডিমান্ড কী ছিল, আয় কেমন হয়েছে, আর ব্যয়ই বা কতটা। অর্থাৎ, শুরুতেই লাভ অথবা লোকসানের হিসেবটা হয়ে যায়। সেই অনুযায়ী আগামী বছরের জন্য টার্গেট সেট করতে হয় তাকে। যাবতীয় রিস্ক ফ্যাক্টরও এর মধ্যে ধরা থাকে। বছরভরের রানিং কস্ট মেপে নিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় আয়ের টার্গেট। খরচ কেমন হয়? দু’ধরনের—এককালীন এবং মাসের। কোন কোন দপ্তরের জন্য এককালীন টাকা লাগবে, সেটার হিসেব কষা হয় আগে। তারপর কর্মীদের বেতন, অফিস চালানোর জন্য ইলেকট্রিক বিল, মেশিন সহ যাবতীয় মেইন্টেনেন্স খরচের মাসিক হিসেব। সেই মতো বরাদ্দ হয় অর্থ। কোন অ্যাকাউন্ট থেকে কোন খাতের টাকা যাবে, সেটা ঠিক করে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে হয়। আর এক দফার বাজেট করতে হয় দূরেরটা ভেবে। যেমন, ৩০ কোটি টাকা দামের যে মেশিন উৎপাদন করছে, সেটা তো সারা জীবন চলবে না! ধরা যাক, আজ থেকে ১০ বছর পর তার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু এই ১০টি বছর ধরেই একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক হিসেব কষে ওই খাতে সরিয়ে রাখতে হয়। এটাও কোম্পানি বাজেটের একটা বড় অংশ। সরকারের বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে একে পরিকাঠামো খাতে খরচ বা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলে ভাবা যেতেই পারে। আর নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়াটাকে কর্মীদের বেতন, স্বাস্থ্যবিমা, বোনাস ভেবে নিলে খুব ভুল হবে না। কিন্তু সরকারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একটি দায়িত্বশীল সংস্থার ফারাক কোথায় হয়? হঠাৎ ১০০ দিনের কাজের টাকা সরকার বন্ধ করে দিলে আম জনতা সংসদে ভাঙচুর চালায় না। কিন্তু সংস্থার বেতন বন্ধ হয়ে গেলে? কর্মীরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দেখিয়ে রোগী হাসপাতালে বেড না পেলে ঘটিবাটি বেচেও বাড়তি টাকা দিয়ে সে নার্সিংহোমে ভর্তি হবে। কর্পোরেট মেডিক্লেমের টাকা না পেলে কিন্তু কর্মী তার সংস্থার ম্যানেজমেন্টের কেবিনের দরজা ভেঙে দিয়ে আসতে দু’বার ভাববে না! নির্মলা সীতারামন গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারবেন, চলতি অর্থবর্ষে সরকারের আয়ের ২৪ শতাংশ এসেছে ঋণ থেকে। কিন্তু একটি সংস্থা যদি তার ৫০ কোটি টাকা আয়ের ১২ কোটি টাকা ঋণ দেখায়, কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে লাল বাতি জ্বলে যাবে। নির্মলাদেবী বাড়তি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলবেন, ‘টাকা তো দুর্বল হচ্ছে না! ডলার শক্তিশালী হচ্ছে।’ কিন্তু ‘ক’ সংস্থাটিকে ওই শক্তিশালী ডলার দিয়েই বিদেশ থেকে কাঁচামাল কিনতে হবে। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়বে। অথচ মার্কেটে চাহিদা না থাকলে পণ্যের দামও সে বাড়াতে পারবে না। সোজা কথায়, লাভ কমবে এবং লোকসান বাড়বে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের করের টাকা দিয়েই সরকার আমাদের জন্য ঘোষিত প্রকল্পের বরাদ্দ ঠিক করে। কোম্পানিকে কিন্তু তার পণ্য বা পরিষেবা বাজারে বেচেই কর্মীদের জন্য বেতন জোগাড় করতে হবে!
এই বিরাট তালিকা ধরে পার্থক্য বোঝানোর কারণ কী? একটাই—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, সরকারেরটা হল দায়। আর সংস্থার? দায়বদ্ধতা। সরকার একটা প্রকল্প ঘোষণা করে তা বেমালুম চেপে যেতে পারে। বরাদ্দ তো হয়েই রয়েছে। প্রকল্প কার্যকর না হলে ওই টাকাটা সরকারের কোষাগারে থেকে যাবে। এবার সেটা দিয়ে অর্থবর্ষের শেষে নির্দ্বিধায় বাজেট ঘাটতি কম দেখানো সম্ভব। কিংবা কোনও রাজ্যে যদি ভোট আসন্ন হয়, তাদের জন্য আলাদা প্যাকেজে সেটাই টাকা ‘সাইফন’ করে দিতেও অসুবিধা হবে না। অর্থাৎ, এক প্রকল্পের টাকা অন্য প্রকল্পে লেগে গেল। উল্টে ভোটেও নম্বর বাড়ল। প্রতিশ্রুতির ধাপ্পা না দিতে পারলে এই টাকাটা কি উঠবে? তার উপর লাগাতার ভোটের ঘোষণা চলছে... আড়াই হাজার টাকা মহিলাদের ভাতা, বাসে ভাড়া লাগবে না, বিদ্যুৎ ফ্রি... কোথা থেকে আসবে এসবের খরচ? আকাশ থেকে তো পড়বে না। বিজেপি, কংগ্রেস বা আম আদমি পার্টি নিজেদের পকেট থেকেও দেবে না। তার মানে, অন্য কোনও খাতের বরাদ্দ চুপিসারে ঢুকে যাবে রাজনীতিতে। তাই নয় কি?
এবারের বাজেট নরেন্দ্র মোদিকে দিল্লি ভোটে ডিভিডেন্ড দেবে বলেই মনে করছে বিজেপি। রাজধানীর ভোটারদের একটা বড় অংশের মাসিক আয় ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকার বেশি। এর নীচের চাকরিজীবীদের এমনিতেই এতদিন নতুন কাঠামোয় আয়কর দিতে হতো না। এবার ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের নাগরিকরাও এই সুবিধা পাবেন। মোদি সরকারের ইঙ্গিত এবার স্পষ্ট, যা করার করে দিয়েছি। এবার পালা মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের। এখন খরচ করুক! মোবাইল ফোন কিনুক, টিভি, ফ্রিজ, গয়না, গাড়ি, বাড়ি... মাসে ৭-৮ হাজার টাকায় এইসবের ইএমআই তো হয়েই যাবে। তাহলেই তো অর্থনীতির চাকা ঘুরবে। কিন্তু পেট্রল-ডিজেলের দামের জন্য সব্জি, মাছ এবং অন্যান্য নিত্যপণ্যের পরিবহণ খরচ বাড়ছে! সঙ্গে রয়েছে আনুষঙ্গিক আরও কত খরচ। সেই কারণেই তো মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। তার উপর জিএসটির বোঝা। একই জিনিসের রূপ বদলে জিএসটি বেড়ে যাচ্ছে। চালে জিএসটি, খাতায়, পেনে, শিশুর দুধে, বিমায়, ওষুধেও জিএসটি। লাভের গুড় তো শেষমেশ সরকারই খেয়ে যাবে। যে প্রেশারের ওষুধ এক বছর আগেও ৮৫-৯০ টাকা ছিল, সেটাই এখন ১২৫ টাকা। যে চালের দাম ৪০ টাকা কেজি ছিল, সেটা এখন ৪৮ টাকা। কিন্তু এই এক বছরে মূল্যবৃদ্ধির লাফের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আয় পাল্লা দিতে পারছে কি? যে মানুষটা ২০১৪ সালের মতো এখনও হাজার টাকা পেনশন পান, তাঁর ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হবে কীভাবে? যাঁরা বেশি টাকা আয় করেন, তাঁরা ছাড়া অন্যদের কি ভোগ্যপণ্য কেনার অধিকার নেই? সমাজে, সরকারে, অর্থনীতিতে তাঁদের কি একেবারেই কোনও ভূমিকা নেই? সরকারের এসবে কিছুই আসে যায় না। জাহান্নমে যাক সাধারণ মানুষ। শুধু একবার উঁকি মেরে দেখে নিতে হবে, ওই মানুষটির রাজ্যে কাছাকাছি কোনও সময়ে ভোট আছে কি না। করছাড় দিয়ে যদি এক লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়, তাহলে জানবেন, সরকার আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে এই টাকাটা কোথা থেকে ভরপাই হবে। প্রশ্ন হল, এই ক্ষতি কে পুষিয়ে দেবে? আমরা। আম জনতা। আমাদের করের টাকাতেই জনপ্রতিনিধিদের মাইনে বাড়বে, তাঁরা গাড়ি-বাড়ি পাবেন, তেল খরচ, সারা জীবনের জন্য ফ্রি গ্যাস সিলিন্ডার এবং পেনশন। আর সবিতা বাউরি উজ্জ্বলার কানেকশন করানোর পর ফিরে যাবেন সেই কাঠের জ্বালানিতে। গ্যাসের সিলিন্ডার কেনার টাকাটাই যে তাঁর কাছে নেই! বছর পঁচিশের অমিত বিশ্বাস একের পর এক দরজায় কড়া নাড়বেন চাকরির আশায়। সরকার কিংবা বেসরকারি... বোর্ড ঝুলবে ‘নো ভ্যাকেন্সি’র। তখন তাঁর কানে বাজবে একটা বাজেট ঘোষণা... ২ কোটি ৯০ লক্ষ চাকরির।
এখনকার দর
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৬.১৮ টাকা | ৮৭.৯২ টাকা |
| পাউন্ড | ১০৬.২৮ টাকা | ১১০.০২ টাকা |
| ইউরো | ৮৮.১৫ টাকা | ৯১.৫১ টাকা |
*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে