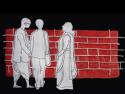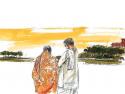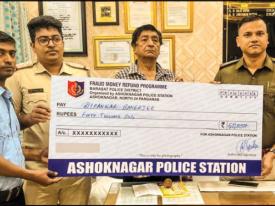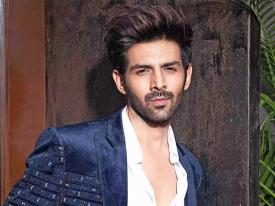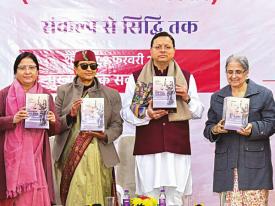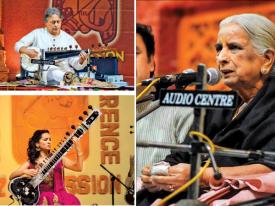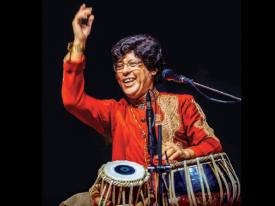কলকাতা, বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২২ মাঘ ১৪৩১
প্রকৃতি ও ভারত
মিশেছে অজন্তায়

ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্যতম দ্রষ্টব্য অজন্তা গুহা। এই গুহার ভাস্কর্য রচনার আগে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। রূপক ও বাস্তবের সংমিশ্রণে উঠে এল অজন্তা ভাস্কর্যের সেই মায়াময় সূচনা। লিখছেন দেবী প্রসাদ ত্রিপাঠী।
আজ থেকে প্রায় ২২০০ বছর আগেকার ঘটনা। মন্দিরে এসেছেন একদল শিল্পী। তাদের মধ্যে আছে পাথর কাটার লোক, চিত্রকর, স্বর্ণশিল্পীদের গোষ্ঠী, ছুতোর শিল্পী, বাস্তুকার এবং কামার শিল্পীর দল। এরা মূলত শ্রেষ্ঠীদের অধীনে কাজ করে। গোষ্ঠীপতি হন শ্রেষ্ঠীরাই। রাজা গোষ্ঠীপতিদের কখনও পয়সা অথবা অর্থের বিনিময়ে গ্রাম দান করতেন। দক্ষ শিল্পীরা সপ্তাহের শেষে মজুরি পেতেন, অন্যরাও মজুরি পেতেন কিন্তু তাঁদের মজুরির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। একই শ্রেষ্ঠী কাজের বরাত নিতেন তা নয়, একাধিক শ্রেষ্ঠী একই সঙ্গে কাজ করতেন।
আবারও সেই ২২০০ বছর আগের শিল্পীদের গ্রামে ফেরা যাক।
অজন্তা গ্রামে আজ উৎসব। পাথরের উপর লোহার শিকে বিদ্ধ করা হয়েছে একটি বুড়ো অজগর সাপকে। সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে তো খাওয়া হবেই, পাশাপাশি আবার একটি গণ্ডারকেও পোড়ানো হবে মাংস খাওয়ার জন্য। অতএব আজ মহোৎসব। সারি সারি অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাতে ঝলসানো হচ্ছে ময়ূর, বন্য শূকর প্রভৃতি জীবজন্তু। কাহ্ন এখানকার প্রধান চিত্রশিল্পী, তার সঙ্গে আছে তিন দাসী কন্যা। গোধা, ঋজা আর রম্ভা। ঋজা দাসীর কন্যা, অতীব রূপবতী। আর রম্ভা খুব সম্ভবত সন্তানসম্ভবা। কাহ্ন তার কুটির থেকে তিনজনকে নিয়ে বের হয়ে আগুনের সামনে এসে বসেছে। হাতে গাছের ছাল এবং শক্ত ক্ষুর, যেন চিত্রশিল্পীর তুলি। চারিদিক আজ আনন্দে মুখরিত। মিশর থেকে এক শিল্পী এসেছে। সে একটু আনমনা। তার দুই দাসী তার হাত মালিশ করে দিচ্ছে। একজন অম্বিকা, অপরজন নীলা।
যেখানে উৎসব হচ্ছে তার মধ্যভাগ খোলা প্রশস্ত। সেখানে ধান শুকাতে দেওয়া হয়। এখন ধান নেই তাই ওখানে বেদেনীরা নাচছে। সামনে মজুররা বসেছে। পরনে জামা নেই। আগুনের উত্তাপে তাদের শরীরে ঘাম ঝরছে। রাজা হরিসেনা হাতির পিঠে চড়ে একবার ঘুরে গিয়েছেন এবং বশিষ্ঠকে রেখে গিয়েছেন। কাহ্নকে ডেকে বলে গিয়েছেন যে এই বশিষ্ঠ শিল্পপণ্ডিত। তাঁর কথা একটু মন দিয়ে শুনতে বলে গিয়েছেন, তাতে কাজের মধ্যে রুচিবোধ আসবে। কাহ্ন চুপ করে রাজার কথা শুনেছে, কোনও কথা বলেনি। বশিষ্ঠকে যে তাঁর খুব একটা পছন্দ হয়েছে তা নয়, কিন্তু সে ভিন্ন কুটিরে থাকবে ফলে অসুবিধার কিছু নেই।
বশিষ্ঠ শিল্পশাস্ত্র রচনা করছেন, সৌন্দর্য যে কী, তা তাঁর আয়ত্তে। গোধা লোহার তরোয়াল দিয়ে গণ্ডারের তলপেট ছিন্ন করে হুক দিয়ে তার হৃদপিণ্ড টেনে বের করে নিয়ে এসেছে। শক্ত ধাতব জন্তু, কিন্তু হৃৎপিণ্ডটি পদ্ম ফুলের মতো নরম। গোধা কচুর পাতার উপরে গণ্ডারের ঝলসানো মাংস বেড়ে কাহ্ন ও বশিষ্ঠকে খাওয়ার জন্য দিয়ে গেল। কাহ্ন তাকে ক্ষণিকের জন্য বসতে বললে সে আপত্তি করল না। কাহ্ন তখন তার ছেঁড়া কাপড় দিয়ে গোধার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বশিষ্ঠকে বললে, ‘দেখো পণ্ডিত, এ যদি সোজাও তাকায় তবুও এর ঘাড় ও মাথা বেঁকে থাকে। আর দু’টি ঠোঁট দেখো নাকের মাপের অর্ধেক, আবার মুখগহ্বরটা দেখো ঠোঁটের মাপের চার ভাগ।’
ইতিমধ্যে ঋজা একখণ্ড মাংসপিণ্ড এনে তাদের সামনে রাখল। কাহ্ন তার চোখের উপর হাতের আঙুল স্পর্শ করে বললে, ‘দেখো পণ্ডিত এর চোখের পাতার উপরের অংশ চোখের বিস্তারের একের তিনভাগ আর নিম্নভাগ একের দুই ভাগ। এটাই মাপ, কিন্তু এই মাপ শারীরিক নয়। চোখের মণির প্রশস্ততা দেখানোর জন্য আমার মনে হয় তা ব্যবহার করা উচিত।’ তার কথা শুনে বশিষ্ঠ পণ্ডিত বললেন, ‘তুমি যথার্থই বলেছ। শিল্পের জন্য শরীরকে ছুঁয়ে তার অভ্যন্তর থেকে সত্য চেহারা বের করে নিতে হয়, একেই বলে শিল্পদর্শন। তুমি শিখেছ হাতে কাজ করতে করতে আর আমি ধ্যানে দেখেছি।’
গোধা আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলল, ‘তোমরা দু’জনে এইভাবে আমাদের শরীর নিয়ে শাস্ত্রবাক্য আওড়াবে আর আমরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকব?’ এমন সময় রম্ভা এগিয়ে এসে তিনজনের হাতে মাংস ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘খাও, সারাদিন পরিশ্রম করো আর আজ বিশ্রামের দিন পেয়েছ আনন্দ করো। আমি নাচব এই আগুন ঘিরে। ঋজা তুমি ঢোলক বাজাও।’
আগুনের বৃত্তকে ঘিরে নাচ শুরু হল। কাহ্ন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় সেই স্রোতকে ধরতে চাইছে কিন্তু স্রোত ধরা যাচ্ছে না। নাচের ছন্দে ধ্বনির গম্ভীর আওয়াজে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। রম্ভা নাচ করছে, কাহ্ন তাকে লক্ষ্য করছে। তার নানা নাচের ভঙ্গিমার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ভঙ্গিমা কখন সৃষ্টি হচ্ছে। রম্ভার ঠোঁটে মৃদু হাসি যেন আত্মগত বিস্ময়। ছন্দ, তাল তার শরীরে কোথাও লুকিয়ে থাকে, গতি পেয়ে আজ মুক্তি পেয়েছে এটাই আনন্দ। কাহ্ন পণ্ডিতকে বলল, ‘এর নাচ একটু স্থির করে নিয়ে যদি ভাবা যায় তবে তিনটি ভাগে শরীরকে ভাগ করে দেওয়া যায়। যেন তিনটি টুকরো একত্রে মিলেছে। চিত্রে সংযুক্ত করার সময় নানা কৌণিক তলে ওদের স্থাপিত করতে হয়।’ পণ্ডিত মুগ্ধ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে ভাবতে থাকেন, অনুভব করতে থাকেন যে শিল্পশাস্ত্র বাড়িতে বসে লেখার বিষয় নয় বা ধ্যানের বিষয় নয়। তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে কাহ্ন বলল, ‘পণ্ডিত লক্ষ্য করে দেখো রম্ভার শরীরের মধ্য সরলরেখা থেকে তার ঊর্ধ্বাংশ লম্বাটে বৃত্তের মতো বেঁকে যাচ্ছে। ঠিক আমাদের ছাদের মতো।’
পণ্ডিত বললেন, ‘প্রথমেই শারীরিক লক্ষণ অনুসারে শরীরকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। শারীরিক ঐক্য শুধুমাত্র লাবণ্য সৃষ্টি করে না, শিল্পীর দক্ষতাকেও দেখাতে পারে। শরীরের ছন্দের প্রতি অঙ্গের সংযুক্তিতে যে লাবণ্য সৃষ্টি হয় তাকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে হবে।
ভাস্কর্যশিল্পীদের প্রধান হিঙ্গিক যে নাচের টানে এসে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তা তাদের জানা ছিল না। হিঙ্গিক বললেন, ‘তুমিই সেই পণ্ডিত!’ তাকে স্পর্শ করে বললেন, ‘পণ্ডিত এই ছন্দ কোনও বাক্য দ্বারা সূচিত হতে পারে না।’ সকলেই হিঙ্গিককে দুর্মুখ বলে জানে। তার শক্তপোক্ত শরীর, একটু বেঁটে, কিন্তু মাঝে মাঝে দিলখোলা হাসি যখন হাসে, ময়ূরগুলো নেচে ওঠে।
উৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলছে, চারিদিকে মাংস পোড়ানোর গন্ধ। বেদেদের আহ্লাদের সীমা নেই। তারা এখানে থাকে শিল্পীদের সঙ্গে, পাথর টানার কাজ করে। কিন্তু তারা দাস নয়, স্বল্প পয়সার মজুর, অবসর সময় খেলা দেখায়, আবার বৈদ্যও বটে। অনেক অসুখ সেরে যায় তাদের ওষুধে। দূরে এক মাদারি দড়ি টাঙিয়ে তার উপর নাচের নানা মুদ্রা করছে। ওখানে হইচই বেশি। গাছের তলায় অনেক শান্ত পরিস্থিতি। পণ্ডিত রম্ভাকে লক্ষ্য করছেন। রম্ভা যেন প্রকৃতির অংশ। কাহ্ন বললে, ‘পণ্ডিত এখনও কি শাস্ত্রশিক্ষার কিছু বাকি আছে? তবে আজ আর শেখানোর দরকার নেই।’
আকাশের চাঁদকে দেখে আজ মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছে। রম্ভা দাড়িয়ে আছে বৃক্ষ শাখা একহাতে ধরে, তার দেহের সঙ্গে মিশে গিয়েছে সেই চন্দ্রমার আলো, আর তার সামনে পণ্ডিত প্রণামের ভঙ্গিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রম্ভার এক পায়ের উপরে ভর, সেই পা শক্ত যেন বৃক্ষের মূলশাখা, আর দ্বিতীয় পা-টি বেঁকে গাছের কান্ড স্পর্শ করে আছে। মায়াদেবীর মূর্তি কালকে কাহ্নকে রচনা করতে হবে। এই রম্ভাই সেই মায়াদেবীর রূপ। এই রূপের কাছে স্তব্ধ হয়ে গেল কাহ্ন।
গোধা ওদের জন্য সুরা এনে দিল। ভাত সেদ্ধ করে মূলত এই সুরা তৈরি করা হয় যা বেদেরা বানায়। মিশরে যে সুরা তৈরি হয়, তার কিছু অংশ শ্রেষ্ঠী হিঙ্গলছন্দ তাদের খুশি হয়ে দান করেন। সুরা গ্রহণ করে কাহ্ন বলল, ‘পণ্ডিত তুমি গ্রিসে গিয়েছিলে আমি তা জানি, তুমি মিশরে গিয়েছিলে সেটাও আমরা জানি, ওদের শিল্পধারা নিয়ে তোমার নিশ্চয়ই কিছু জানা আছে? ওদের ধারা আমার কিন্তু পছন্দ হয় না। আমরা মূর্তি রচনা করি প্রকৃতির থেকে, ওরা তৈরি করে নীলনদ আর মরুভূমির রূপ থেকে। তোমার অভিজ্ঞতা বল শুনি।’
পণ্ডিত বললেন, ‘মিশরে আমি গিয়েছিলাম। ওদের স্থাপত্যবিদ্যা আশ্চর্য হয়ে দেখার মতো। এই কাজ করতে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন সেই পরিমাণ শ্রমিক ওদের ছিল। ফলে কাজ করানোর কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু অঙ্কনশাস্ত্র ওদের কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমাদের থেকেও ২০০০ বছর পূর্বের কাজ আমি দেখেছিলাম। তুলনা করে বললে বোধহয় কাহ্ন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমি সেইভাবেই বলি।
রাজাই ওদের দেবতা বা সূর্যদেবতার প্রতিনিধি। ফলে দেওয়ালে ওরা দেওয়ালচিত্র আঁকেন রাজা যদি ফিরে আসেন এই চিন্তায়। ওরা মুখটাকে ধরে পার্শ্বদেশ থেকে, আমরা ধরি দুয়ের তিন অংশ ধরে। ফলে ওদের ক্ষেত্রে মুখটাকে চ্যাপ্টা লাগে, আমাদের ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায়। ওরা কাঁধ শরীরের তুলনায় দীর্ঘ করে রচনা করে রাজার বীরত্ব ও শক্তি বোঝানোর জন্য। শরীর কিন্তু ওরা দুয়ের তিন অংশই অঙ্কন করে। হাত দীর্ঘ যেন অন্যের রাজ্য জয় করে নিতে পারেন হাত বাড়িয়ে। রাজার কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাপ তার নীচের অংশের মাপের থেকে অনেক কম। আমরা কিন্তু উভয়-বিভাজন সমান রাখি। কোমর অনেক শীর্ণকায়। আর নারীর ক্ষেত্রে কোমর প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো নয়। বরং কৃত্রিম। ওরা শরীরকে খেজুর গাছের সমতুল্য করার চেষ্টা করে। মুখ নির্মাণের ক্ষেত্রে ওরা আয়তাকার ভূমি ব্যবহার করে। আমরা বৃত্ত বা ঋতুচক্র ব্যবহার করি। ফলে ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য অনেক। ওদের মুখে কোনও অভিব্যক্তি থাকে না, আমরা কিন্তু অভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সরলরেখাকে ওরা সুষমা সৃষ্টির জন্য ভাঙতে পারে না। তাই ওদের চিন্তাধারা আমাদের থেকে আলাদা। মিশর পরে রোমানদের দখলে চলে যায়, আমি সেই সময় গিয়েছিলাম। মিশরের শিল্পকে রোমানশিল্প বললে ভুল বলা হবে। তার সঙ্গে ভারতীয় ধারাও যুক্ত হয়েছিল। ভারতীয় ধারা বললে বহু ধারার কথা উঠতে পারে, অজন্তার ধারার কথাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওদের শিল্পে পুরো মুখটাই দৃশ্যমান। মুখটা লম্বাটে, নাক জীবন্ত, চোখে কথা আটকে গিয়েছে। কিন্তু মাথায় মিশরীয়দের মতো উঁচু করে রাখা চুলের বিস্তার। আবার গ্রিসের কথা যদি ধরো, তবে বলব, তাদের মাপ আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা নাকের দৈর্ঘ্যের সমান করে নাকের নীচ থেকে থুতনি পর্যন্ত একই মাপের করে। ফলে মুখটা লম্বাটে বলে মনে হয়। শরীর ওরা পোশাক দিয়ে আবৃত রাখে।’
কাহ্নের কথা শুনে ভাস্কর্য রচয়িতা প্রধান হিঙ্গিক ‘সাধু সাধু’ বলে চিৎকার করে উঠলেন। মাদারিরা অক্লান্তভাবে খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে। উৎসব নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মাংস ঝলসানোর পর আগুন নিভু নিভু। অম্বিকাকে দেখা গেল মাদারির দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে। সে শুধু খেলা দেখছে তা নয়, নিজেও খেলায় অংশ নিয়েছে। জন্মসূত্রে অম্বিকা মাদারি। অম্বিকার এখন নেশা হয়ে গিয়েছে। গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, সামনের পা এলানো, কিন্তু হাঁটু ও পায়ের পাতা শরীরের ভার নিয়েছে। আর একটা পা গাছে ঠেকা দিয়ে রেখেছে। নেশার ঘোরে সে গান ধরেছে। হিঙ্গিক একটা দড়ি বের করে করে অম্বিকাকে মাপতে লাগলেন। মাথা থেকে বেঁকে যাওয়া শরীর লম্বভাবে মাপলেন। মাথার চুলের শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে দড়িটা নামিয়ে দিলেন। কী আশ্চর্য, সেই দড়ি ঝুলে নেমে গিয়েছে এলানো পায়ের হাঁটুতে। আর কোমর ও অপর পা শঙ্খের রূপ ধরে বিস্তৃত হয়েছে। আবার চুল থেকে গালের পাশ দিয়ে দড়ি নামিয়ে দিয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন। সেই দড়ি পায়ের পাতা স্পর্শ করেছে। এই দড়িকে অলঙ্কার রুপে পরিয়ে দেখতে লাগলেন তা কত দূর নামানো যায়।
নারীই প্রকৃতি। তাই তার মাথার উপর বৃক্ষ ডালপালা নামিয়ে দিয়েছে। যেন প্রাণ পেয়েছে সে। হিঙ্গিক আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। অম্বিকাকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, ‘তুই বৃক্ষ, তুই ধাবমান নদী, তুই পর্বত, তুই আমার দেবী।’ তাঁকে সংযত করে পণ্ডিত বললেন, ‘হিঙ্গিক, ভাষা যিনি রচনা করেন তিনি ব্যাকরণ লেখেন না, আবার যিনি ব্যাকরণ রচনা করেন তিনি কোনও দিন কাব্য রচনা করতে পারেন না। এই ভঙ্গিমা বহুদিনকার। তার মাত্রাবোধ, ছন্দবোধ তুমি পাল্টে দিয়েছ। আমি পণ্ডিত নই আমি প্রত্যহ তোমাদের কাছই শিখব।’
হিঙ্গিক বলে উঠলেন, ‘এ কী সম্মান প্রদান না মায়া বিভ্রম?’ পণ্ডিত তাঁকে প্রণাম করলেন। হিঙ্গিক বললেন, ‘দেবীকে প্রণাম করুন। এই মূর্তিই হবে মায়া দেবীর। পণ্ডিত তাঁকে প্রণাম করে শান্তভাবে সরে গেলেন। মদালসা অম্বিকা হিন্দিককে বলল, ‘স্তুতি অনেক করা হয়েছে এবার এই চাঁদের আলোয় আমাকে একটু ঘুমাতে দাও।’
পণ্ডিত চিন্তিত। এমন সময়ে রম্ভা এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল,‘পণ্ডিত ঘরে চলো।’ পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল, রম্ভা তুমি তো এখানে কাজ করো। চিত্রলক্ষণ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?’ রম্ভা বলল, ‘কিছুটা জানি। যেমন বালিকার রূপ হবে উদিত সূর্যের মতো। কিন্তু উদিত সূর্যের বহু রূপ, তা যে ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যায়। এই বিষয়টি হয়তো পণ্ডিতদের জানা ছিল না। তাই আমরা পণ্ডিতদের মান্যতা দিলেও তাদের কথা সম্পূর্ণ শুনি না। একমাত্র তোমাকেই দেখলাম তুমি শিখতে এসেছ, জানতে এসেছ। তাই আমি তোমার কাছে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছি। রূপ ও আকারই ছন্দ, তাই তা সুন্দর। এটা মনের ব্যাপার।’ রম্ভা আবেগের বশীভূত হয়ে আবারও বলল, ‘আমরা মানুষ রূপে স্বীকৃতি পাইনি, পণ্ডিত তুমি দিলে সেই স্বীকৃতি, তুমি সত্যই মহৎ।’ পণ্ডিত বললেন, ‘আমি তোমাকে শিক্ষাগুরু হিসেবে মেনে নিয়েছি। কাজ করতে করতে আমার যে সামান্য ধারণা হয়েছে তা থেকে বলতে পারি, শিল্পে নিয়মের বলপ্রয়োগ তাকে বিকৃত করে তোলে। শিল্প মুক্ত। শিল্পীদের অধ্যাত্মবোধ যার মধ্যে রচিত হবে তার রূপ খুঁজে বেড়ানো শিল্পশাস্ত্রের কাজ। সেটা এক সময় ধারা হয়ে উঠবে।’
রম্ভা বলল, ‘তিব্বতের শিল্পশাস্ত্র যে নিয়ম মতে চলার কথা বলে, আমি যেটুকু শুনেছি, তা তোমাকে বলতে পারি।’ পণ্ডিত বললেন, ‘তুমি বলো, শুনে উপকৃত হই।’
রম্ভা বলতে শুরু করল। বালিকাদের মূর্তি মুখ হবে চাঁদের মতো গোলাকার, চোখ হবে দীর্ঘাকার, হরিণের মতো, ঠোঁট লাল রঙের, শরীরের রং হবে নীল পদ্মের মতো। সেই বালিকাকে অলঙ্কৃত করা হবে সোনার গয়না দিয়ে। এটা একটা রূপ। আবার ভিন্ন রূপেও চিত্রিত করা হয়েছে তাকে। যেখানে শরীরের রং সাদা, চোখের রং কালো, ঠোঁট লালচে। সৌন্দর্যের মাত্রাবোধ গঠিত হয়েছে পায়ের ঊর্ধ্বাংশের বলিষ্ঠতা, গলার দৃঢ়তা, সুসজ্জিত দন্ত, উচ্চ নাসিকা ইত্যাদির মাধ্যমে। মূলত এই ধারা ভারতবর্ষ থেকেই তিব্বতে গিয়েছে। চীনে বুদ্ধরূপ এই সূত্রে ফেলা হয় না। এসব আমার শোনা কথা। আমি চাই তুমি যথার্থ শিল্পশাস্ত্র রচনা করো, কিন্তু শুধুই মন থেকে নয়, শিল্পীদের কাজ দেখতে দেখতে।’
রাত যত বড়ই হোক একসময় তা শেষ হয়। পুনরায় দিন আসে। পণ্ডিত ও রম্ভাও সকালে কাজে বের হলেন। পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে। দ্রুত তাঁদের গতি। গ্রামে বৃদ্ধা আর বাচ্চারা থাকে, বাকি সবাই কাজে বেরিয়ে পড়ে। কেউ স্বাধীন শিল্পী নন, যে সমস্ত শিল্পীগোষ্ঠী আছে প্রত্যেকেই তাদের দলভুক্ত। এছাড়া দাস ও দাস কন্যাদের সংখ্যা শিল্পীদের থেকেও বেশি। তাদের শরীরের ভাব, ভঙ্গি, মুখের আদল, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি থেকেই গঠিত হয় মন্দিরের ভাস্কর্য। ইতিহাস অনুযায়ী, অজন্তার গুহাচিত্র কোনও শিল্পীর কল্পনা নয়। বরং বিভিন্ন শিল্পীদের ভাবধারার মিলন ও ভারতীয় শিল্পচেতনার মিশ্রণে তা যেন প্রকৃতির বিস্তৃতি রূপদান। সেই মূর্তির মাপজোক, বিস্তার, ভঙ্গিমা, রূপমাধুরী আজও অমর।
আজ থেকে প্রায় ২২০০ বছর আগেকার ঘটনা। মন্দিরে এসেছেন একদল শিল্পী। তাদের মধ্যে আছে পাথর কাটার লোক, চিত্রকর, স্বর্ণশিল্পীদের গোষ্ঠী, ছুতোর শিল্পী, বাস্তুকার এবং কামার শিল্পীর দল। এরা মূলত শ্রেষ্ঠীদের অধীনে কাজ করে। গোষ্ঠীপতি হন শ্রেষ্ঠীরাই। রাজা গোষ্ঠীপতিদের কখনও পয়সা অথবা অর্থের বিনিময়ে গ্রাম দান করতেন। দক্ষ শিল্পীরা সপ্তাহের শেষে মজুরি পেতেন, অন্যরাও মজুরি পেতেন কিন্তু তাঁদের মজুরির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। একই শ্রেষ্ঠী কাজের বরাত নিতেন তা নয়, একাধিক শ্রেষ্ঠী একই সঙ্গে কাজ করতেন।
আবারও সেই ২২০০ বছর আগের শিল্পীদের গ্রামে ফেরা যাক।
অজন্তা গ্রামে আজ উৎসব। পাথরের উপর লোহার শিকে বিদ্ধ করা হয়েছে একটি বুড়ো অজগর সাপকে। সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে তো খাওয়া হবেই, পাশাপাশি আবার একটি গণ্ডারকেও পোড়ানো হবে মাংস খাওয়ার জন্য। অতএব আজ মহোৎসব। সারি সারি অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাতে ঝলসানো হচ্ছে ময়ূর, বন্য শূকর প্রভৃতি জীবজন্তু। কাহ্ন এখানকার প্রধান চিত্রশিল্পী, তার সঙ্গে আছে তিন দাসী কন্যা। গোধা, ঋজা আর রম্ভা। ঋজা দাসীর কন্যা, অতীব রূপবতী। আর রম্ভা খুব সম্ভবত সন্তানসম্ভবা। কাহ্ন তার কুটির থেকে তিনজনকে নিয়ে বের হয়ে আগুনের সামনে এসে বসেছে। হাতে গাছের ছাল এবং শক্ত ক্ষুর, যেন চিত্রশিল্পীর তুলি। চারিদিক আজ আনন্দে মুখরিত। মিশর থেকে এক শিল্পী এসেছে। সে একটু আনমনা। তার দুই দাসী তার হাত মালিশ করে দিচ্ছে। একজন অম্বিকা, অপরজন নীলা।
যেখানে উৎসব হচ্ছে তার মধ্যভাগ খোলা প্রশস্ত। সেখানে ধান শুকাতে দেওয়া হয়। এখন ধান নেই তাই ওখানে বেদেনীরা নাচছে। সামনে মজুররা বসেছে। পরনে জামা নেই। আগুনের উত্তাপে তাদের শরীরে ঘাম ঝরছে। রাজা হরিসেনা হাতির পিঠে চড়ে একবার ঘুরে গিয়েছেন এবং বশিষ্ঠকে রেখে গিয়েছেন। কাহ্নকে ডেকে বলে গিয়েছেন যে এই বশিষ্ঠ শিল্পপণ্ডিত। তাঁর কথা একটু মন দিয়ে শুনতে বলে গিয়েছেন, তাতে কাজের মধ্যে রুচিবোধ আসবে। কাহ্ন চুপ করে রাজার কথা শুনেছে, কোনও কথা বলেনি। বশিষ্ঠকে যে তাঁর খুব একটা পছন্দ হয়েছে তা নয়, কিন্তু সে ভিন্ন কুটিরে থাকবে ফলে অসুবিধার কিছু নেই।
বশিষ্ঠ শিল্পশাস্ত্র রচনা করছেন, সৌন্দর্য যে কী, তা তাঁর আয়ত্তে। গোধা লোহার তরোয়াল দিয়ে গণ্ডারের তলপেট ছিন্ন করে হুক দিয়ে তার হৃদপিণ্ড টেনে বের করে নিয়ে এসেছে। শক্ত ধাতব জন্তু, কিন্তু হৃৎপিণ্ডটি পদ্ম ফুলের মতো নরম। গোধা কচুর পাতার উপরে গণ্ডারের ঝলসানো মাংস বেড়ে কাহ্ন ও বশিষ্ঠকে খাওয়ার জন্য দিয়ে গেল। কাহ্ন তাকে ক্ষণিকের জন্য বসতে বললে সে আপত্তি করল না। কাহ্ন তখন তার ছেঁড়া কাপড় দিয়ে গোধার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বশিষ্ঠকে বললে, ‘দেখো পণ্ডিত, এ যদি সোজাও তাকায় তবুও এর ঘাড় ও মাথা বেঁকে থাকে। আর দু’টি ঠোঁট দেখো নাকের মাপের অর্ধেক, আবার মুখগহ্বরটা দেখো ঠোঁটের মাপের চার ভাগ।’
ইতিমধ্যে ঋজা একখণ্ড মাংসপিণ্ড এনে তাদের সামনে রাখল। কাহ্ন তার চোখের উপর হাতের আঙুল স্পর্শ করে বললে, ‘দেখো পণ্ডিত এর চোখের পাতার উপরের অংশ চোখের বিস্তারের একের তিনভাগ আর নিম্নভাগ একের দুই ভাগ। এটাই মাপ, কিন্তু এই মাপ শারীরিক নয়। চোখের মণির প্রশস্ততা দেখানোর জন্য আমার মনে হয় তা ব্যবহার করা উচিত।’ তার কথা শুনে বশিষ্ঠ পণ্ডিত বললেন, ‘তুমি যথার্থই বলেছ। শিল্পের জন্য শরীরকে ছুঁয়ে তার অভ্যন্তর থেকে সত্য চেহারা বের করে নিতে হয়, একেই বলে শিল্পদর্শন। তুমি শিখেছ হাতে কাজ করতে করতে আর আমি ধ্যানে দেখেছি।’
গোধা আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলল, ‘তোমরা দু’জনে এইভাবে আমাদের শরীর নিয়ে শাস্ত্রবাক্য আওড়াবে আর আমরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকব?’ এমন সময় রম্ভা এগিয়ে এসে তিনজনের হাতে মাংস ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘খাও, সারাদিন পরিশ্রম করো আর আজ বিশ্রামের দিন পেয়েছ আনন্দ করো। আমি নাচব এই আগুন ঘিরে। ঋজা তুমি ঢোলক বাজাও।’
আগুনের বৃত্তকে ঘিরে নাচ শুরু হল। কাহ্ন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় সেই স্রোতকে ধরতে চাইছে কিন্তু স্রোত ধরা যাচ্ছে না। নাচের ছন্দে ধ্বনির গম্ভীর আওয়াজে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। রম্ভা নাচ করছে, কাহ্ন তাকে লক্ষ্য করছে। তার নানা নাচের ভঙ্গিমার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ভঙ্গিমা কখন সৃষ্টি হচ্ছে। রম্ভার ঠোঁটে মৃদু হাসি যেন আত্মগত বিস্ময়। ছন্দ, তাল তার শরীরে কোথাও লুকিয়ে থাকে, গতি পেয়ে আজ মুক্তি পেয়েছে এটাই আনন্দ। কাহ্ন পণ্ডিতকে বলল, ‘এর নাচ একটু স্থির করে নিয়ে যদি ভাবা যায় তবে তিনটি ভাগে শরীরকে ভাগ করে দেওয়া যায়। যেন তিনটি টুকরো একত্রে মিলেছে। চিত্রে সংযুক্ত করার সময় নানা কৌণিক তলে ওদের স্থাপিত করতে হয়।’ পণ্ডিত মুগ্ধ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে ভাবতে থাকেন, অনুভব করতে থাকেন যে শিল্পশাস্ত্র বাড়িতে বসে লেখার বিষয় নয় বা ধ্যানের বিষয় নয়। তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে কাহ্ন বলল, ‘পণ্ডিত লক্ষ্য করে দেখো রম্ভার শরীরের মধ্য সরলরেখা থেকে তার ঊর্ধ্বাংশ লম্বাটে বৃত্তের মতো বেঁকে যাচ্ছে। ঠিক আমাদের ছাদের মতো।’
পণ্ডিত বললেন, ‘প্রথমেই শারীরিক লক্ষণ অনুসারে শরীরকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। শারীরিক ঐক্য শুধুমাত্র লাবণ্য সৃষ্টি করে না, শিল্পীর দক্ষতাকেও দেখাতে পারে। শরীরের ছন্দের প্রতি অঙ্গের সংযুক্তিতে যে লাবণ্য সৃষ্টি হয় তাকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে হবে।
ভাস্কর্যশিল্পীদের প্রধান হিঙ্গিক যে নাচের টানে এসে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তা তাদের জানা ছিল না। হিঙ্গিক বললেন, ‘তুমিই সেই পণ্ডিত!’ তাকে স্পর্শ করে বললেন, ‘পণ্ডিত এই ছন্দ কোনও বাক্য দ্বারা সূচিত হতে পারে না।’ সকলেই হিঙ্গিককে দুর্মুখ বলে জানে। তার শক্তপোক্ত শরীর, একটু বেঁটে, কিন্তু মাঝে মাঝে দিলখোলা হাসি যখন হাসে, ময়ূরগুলো নেচে ওঠে।
উৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলছে, চারিদিকে মাংস পোড়ানোর গন্ধ। বেদেদের আহ্লাদের সীমা নেই। তারা এখানে থাকে শিল্পীদের সঙ্গে, পাথর টানার কাজ করে। কিন্তু তারা দাস নয়, স্বল্প পয়সার মজুর, অবসর সময় খেলা দেখায়, আবার বৈদ্যও বটে। অনেক অসুখ সেরে যায় তাদের ওষুধে। দূরে এক মাদারি দড়ি টাঙিয়ে তার উপর নাচের নানা মুদ্রা করছে। ওখানে হইচই বেশি। গাছের তলায় অনেক শান্ত পরিস্থিতি। পণ্ডিত রম্ভাকে লক্ষ্য করছেন। রম্ভা যেন প্রকৃতির অংশ। কাহ্ন বললে, ‘পণ্ডিত এখনও কি শাস্ত্রশিক্ষার কিছু বাকি আছে? তবে আজ আর শেখানোর দরকার নেই।’
আকাশের চাঁদকে দেখে আজ মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছে। রম্ভা দাড়িয়ে আছে বৃক্ষ শাখা একহাতে ধরে, তার দেহের সঙ্গে মিশে গিয়েছে সেই চন্দ্রমার আলো, আর তার সামনে পণ্ডিত প্রণামের ভঙ্গিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রম্ভার এক পায়ের উপরে ভর, সেই পা শক্ত যেন বৃক্ষের মূলশাখা, আর দ্বিতীয় পা-টি বেঁকে গাছের কান্ড স্পর্শ করে আছে। মায়াদেবীর মূর্তি কালকে কাহ্নকে রচনা করতে হবে। এই রম্ভাই সেই মায়াদেবীর রূপ। এই রূপের কাছে স্তব্ধ হয়ে গেল কাহ্ন।
গোধা ওদের জন্য সুরা এনে দিল। ভাত সেদ্ধ করে মূলত এই সুরা তৈরি করা হয় যা বেদেরা বানায়। মিশরে যে সুরা তৈরি হয়, তার কিছু অংশ শ্রেষ্ঠী হিঙ্গলছন্দ তাদের খুশি হয়ে দান করেন। সুরা গ্রহণ করে কাহ্ন বলল, ‘পণ্ডিত তুমি গ্রিসে গিয়েছিলে আমি তা জানি, তুমি মিশরে গিয়েছিলে সেটাও আমরা জানি, ওদের শিল্পধারা নিয়ে তোমার নিশ্চয়ই কিছু জানা আছে? ওদের ধারা আমার কিন্তু পছন্দ হয় না। আমরা মূর্তি রচনা করি প্রকৃতির থেকে, ওরা তৈরি করে নীলনদ আর মরুভূমির রূপ থেকে। তোমার অভিজ্ঞতা বল শুনি।’
পণ্ডিত বললেন, ‘মিশরে আমি গিয়েছিলাম। ওদের স্থাপত্যবিদ্যা আশ্চর্য হয়ে দেখার মতো। এই কাজ করতে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন সেই পরিমাণ শ্রমিক ওদের ছিল। ফলে কাজ করানোর কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু অঙ্কনশাস্ত্র ওদের কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমাদের থেকেও ২০০০ বছর পূর্বের কাজ আমি দেখেছিলাম। তুলনা করে বললে বোধহয় কাহ্ন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমি সেইভাবেই বলি।
রাজাই ওদের দেবতা বা সূর্যদেবতার প্রতিনিধি। ফলে দেওয়ালে ওরা দেওয়ালচিত্র আঁকেন রাজা যদি ফিরে আসেন এই চিন্তায়। ওরা মুখটাকে ধরে পার্শ্বদেশ থেকে, আমরা ধরি দুয়ের তিন অংশ ধরে। ফলে ওদের ক্ষেত্রে মুখটাকে চ্যাপ্টা লাগে, আমাদের ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায়। ওরা কাঁধ শরীরের তুলনায় দীর্ঘ করে রচনা করে রাজার বীরত্ব ও শক্তি বোঝানোর জন্য। শরীর কিন্তু ওরা দুয়ের তিন অংশই অঙ্কন করে। হাত দীর্ঘ যেন অন্যের রাজ্য জয় করে নিতে পারেন হাত বাড়িয়ে। রাজার কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাপ তার নীচের অংশের মাপের থেকে অনেক কম। আমরা কিন্তু উভয়-বিভাজন সমান রাখি। কোমর অনেক শীর্ণকায়। আর নারীর ক্ষেত্রে কোমর প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো নয়। বরং কৃত্রিম। ওরা শরীরকে খেজুর গাছের সমতুল্য করার চেষ্টা করে। মুখ নির্মাণের ক্ষেত্রে ওরা আয়তাকার ভূমি ব্যবহার করে। আমরা বৃত্ত বা ঋতুচক্র ব্যবহার করি। ফলে ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য অনেক। ওদের মুখে কোনও অভিব্যক্তি থাকে না, আমরা কিন্তু অভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সরলরেখাকে ওরা সুষমা সৃষ্টির জন্য ভাঙতে পারে না। তাই ওদের চিন্তাধারা আমাদের থেকে আলাদা। মিশর পরে রোমানদের দখলে চলে যায়, আমি সেই সময় গিয়েছিলাম। মিশরের শিল্পকে রোমানশিল্প বললে ভুল বলা হবে। তার সঙ্গে ভারতীয় ধারাও যুক্ত হয়েছিল। ভারতীয় ধারা বললে বহু ধারার কথা উঠতে পারে, অজন্তার ধারার কথাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওদের শিল্পে পুরো মুখটাই দৃশ্যমান। মুখটা লম্বাটে, নাক জীবন্ত, চোখে কথা আটকে গিয়েছে। কিন্তু মাথায় মিশরীয়দের মতো উঁচু করে রাখা চুলের বিস্তার। আবার গ্রিসের কথা যদি ধরো, তবে বলব, তাদের মাপ আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা নাকের দৈর্ঘ্যের সমান করে নাকের নীচ থেকে থুতনি পর্যন্ত একই মাপের করে। ফলে মুখটা লম্বাটে বলে মনে হয়। শরীর ওরা পোশাক দিয়ে আবৃত রাখে।’
কাহ্নের কথা শুনে ভাস্কর্য রচয়িতা প্রধান হিঙ্গিক ‘সাধু সাধু’ বলে চিৎকার করে উঠলেন। মাদারিরা অক্লান্তভাবে খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে। উৎসব নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মাংস ঝলসানোর পর আগুন নিভু নিভু। অম্বিকাকে দেখা গেল মাদারির দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে। সে শুধু খেলা দেখছে তা নয়, নিজেও খেলায় অংশ নিয়েছে। জন্মসূত্রে অম্বিকা মাদারি। অম্বিকার এখন নেশা হয়ে গিয়েছে। গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, সামনের পা এলানো, কিন্তু হাঁটু ও পায়ের পাতা শরীরের ভার নিয়েছে। আর একটা পা গাছে ঠেকা দিয়ে রেখেছে। নেশার ঘোরে সে গান ধরেছে। হিঙ্গিক একটা দড়ি বের করে করে অম্বিকাকে মাপতে লাগলেন। মাথা থেকে বেঁকে যাওয়া শরীর লম্বভাবে মাপলেন। মাথার চুলের শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে দড়িটা নামিয়ে দিলেন। কী আশ্চর্য, সেই দড়ি ঝুলে নেমে গিয়েছে এলানো পায়ের হাঁটুতে। আর কোমর ও অপর পা শঙ্খের রূপ ধরে বিস্তৃত হয়েছে। আবার চুল থেকে গালের পাশ দিয়ে দড়ি নামিয়ে দিয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন। সেই দড়ি পায়ের পাতা স্পর্শ করেছে। এই দড়িকে অলঙ্কার রুপে পরিয়ে দেখতে লাগলেন তা কত দূর নামানো যায়।
নারীই প্রকৃতি। তাই তার মাথার উপর বৃক্ষ ডালপালা নামিয়ে দিয়েছে। যেন প্রাণ পেয়েছে সে। হিঙ্গিক আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। অম্বিকাকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, ‘তুই বৃক্ষ, তুই ধাবমান নদী, তুই পর্বত, তুই আমার দেবী।’ তাঁকে সংযত করে পণ্ডিত বললেন, ‘হিঙ্গিক, ভাষা যিনি রচনা করেন তিনি ব্যাকরণ লেখেন না, আবার যিনি ব্যাকরণ রচনা করেন তিনি কোনও দিন কাব্য রচনা করতে পারেন না। এই ভঙ্গিমা বহুদিনকার। তার মাত্রাবোধ, ছন্দবোধ তুমি পাল্টে দিয়েছ। আমি পণ্ডিত নই আমি প্রত্যহ তোমাদের কাছই শিখব।’
হিঙ্গিক বলে উঠলেন, ‘এ কী সম্মান প্রদান না মায়া বিভ্রম?’ পণ্ডিত তাঁকে প্রণাম করলেন। হিঙ্গিক বললেন, ‘দেবীকে প্রণাম করুন। এই মূর্তিই হবে মায়া দেবীর। পণ্ডিত তাঁকে প্রণাম করে শান্তভাবে সরে গেলেন। মদালসা অম্বিকা হিন্দিককে বলল, ‘স্তুতি অনেক করা হয়েছে এবার এই চাঁদের আলোয় আমাকে একটু ঘুমাতে দাও।’
পণ্ডিত চিন্তিত। এমন সময়ে রম্ভা এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল,‘পণ্ডিত ঘরে চলো।’ পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল, রম্ভা তুমি তো এখানে কাজ করো। চিত্রলক্ষণ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?’ রম্ভা বলল, ‘কিছুটা জানি। যেমন বালিকার রূপ হবে উদিত সূর্যের মতো। কিন্তু উদিত সূর্যের বহু রূপ, তা যে ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যায়। এই বিষয়টি হয়তো পণ্ডিতদের জানা ছিল না। তাই আমরা পণ্ডিতদের মান্যতা দিলেও তাদের কথা সম্পূর্ণ শুনি না। একমাত্র তোমাকেই দেখলাম তুমি শিখতে এসেছ, জানতে এসেছ। তাই আমি তোমার কাছে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছি। রূপ ও আকারই ছন্দ, তাই তা সুন্দর। এটা মনের ব্যাপার।’ রম্ভা আবেগের বশীভূত হয়ে আবারও বলল, ‘আমরা মানুষ রূপে স্বীকৃতি পাইনি, পণ্ডিত তুমি দিলে সেই স্বীকৃতি, তুমি সত্যই মহৎ।’ পণ্ডিত বললেন, ‘আমি তোমাকে শিক্ষাগুরু হিসেবে মেনে নিয়েছি। কাজ করতে করতে আমার যে সামান্য ধারণা হয়েছে তা থেকে বলতে পারি, শিল্পে নিয়মের বলপ্রয়োগ তাকে বিকৃত করে তোলে। শিল্প মুক্ত। শিল্পীদের অধ্যাত্মবোধ যার মধ্যে রচিত হবে তার রূপ খুঁজে বেড়ানো শিল্পশাস্ত্রের কাজ। সেটা এক সময় ধারা হয়ে উঠবে।’
রম্ভা বলল, ‘তিব্বতের শিল্পশাস্ত্র যে নিয়ম মতে চলার কথা বলে, আমি যেটুকু শুনেছি, তা তোমাকে বলতে পারি।’ পণ্ডিত বললেন, ‘তুমি বলো, শুনে উপকৃত হই।’
রম্ভা বলতে শুরু করল। বালিকাদের মূর্তি মুখ হবে চাঁদের মতো গোলাকার, চোখ হবে দীর্ঘাকার, হরিণের মতো, ঠোঁট লাল রঙের, শরীরের রং হবে নীল পদ্মের মতো। সেই বালিকাকে অলঙ্কৃত করা হবে সোনার গয়না দিয়ে। এটা একটা রূপ। আবার ভিন্ন রূপেও চিত্রিত করা হয়েছে তাকে। যেখানে শরীরের রং সাদা, চোখের রং কালো, ঠোঁট লালচে। সৌন্দর্যের মাত্রাবোধ গঠিত হয়েছে পায়ের ঊর্ধ্বাংশের বলিষ্ঠতা, গলার দৃঢ়তা, সুসজ্জিত দন্ত, উচ্চ নাসিকা ইত্যাদির মাধ্যমে। মূলত এই ধারা ভারতবর্ষ থেকেই তিব্বতে গিয়েছে। চীনে বুদ্ধরূপ এই সূত্রে ফেলা হয় না। এসব আমার শোনা কথা। আমি চাই তুমি যথার্থ শিল্পশাস্ত্র রচনা করো, কিন্তু শুধুই মন থেকে নয়, শিল্পীদের কাজ দেখতে দেখতে।’
রাত যত বড়ই হোক একসময় তা শেষ হয়। পুনরায় দিন আসে। পণ্ডিত ও রম্ভাও সকালে কাজে বের হলেন। পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে। দ্রুত তাঁদের গতি। গ্রামে বৃদ্ধা আর বাচ্চারা থাকে, বাকি সবাই কাজে বেরিয়ে পড়ে। কেউ স্বাধীন শিল্পী নন, যে সমস্ত শিল্পীগোষ্ঠী আছে প্রত্যেকেই তাদের দলভুক্ত। এছাড়া দাস ও দাস কন্যাদের সংখ্যা শিল্পীদের থেকেও বেশি। তাদের শরীরের ভাব, ভঙ্গি, মুখের আদল, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি থেকেই গঠিত হয় মন্দিরের ভাস্কর্য। ইতিহাস অনুযায়ী, অজন্তার গুহাচিত্র কোনও শিল্পীর কল্পনা নয়। বরং বিভিন্ন শিল্পীদের ভাবধারার মিলন ও ভারতীয় শিল্পচেতনার মিশ্রণে তা যেন প্রকৃতির বিস্তৃতি রূপদান। সেই মূর্তির মাপজোক, বিস্তার, ভঙ্গিমা, রূপমাধুরী আজও অমর।
এখনকার দর
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৬.১৮ টাকা | ৮৭.৯২ টাকা |
| পাউন্ড | ১০৬.২৮ টাকা | ১১০.০২ টাকা |
| ইউরো | ৮৮.১৫ টাকা | ৯১.৫১ টাকা |
*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে