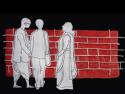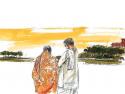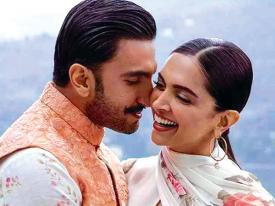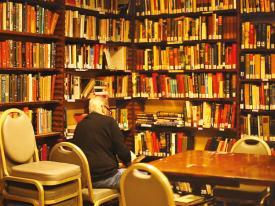কলকাতা, শুক্রবার ২২ নভেম্বর ২০২৪, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
ভারতীয় সভ্যতার
উৎস দর্শনে

ভারতীয় পুরাণ কথা আর ইতিহাসে সমৃদ্ধ স্রোতস্বিনী গঙ্গা। তার তরঙ্গে আমাদের সভ্যতার নানা কাহিনি বর্ণিত। সেই কাহিনি ও প্রাকৃতিক রূপের বর্ণনা করলেন সৌমেন জানা।
আমরা চলেছি উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর পথে। চলতে চলতে মানুষের হই-হট্টগোলে তাকিয়ে দেখি ভয়ঙ্কর জ্যামে আটকে আছে আমাদের গাড়ি। যানজট নিয়ন্ত্রণে কোনও পুলিসের দেখা মিলল না। মাথার ওপর সাদা তুলোর মতো ছেঁড়া মেঘ। চারদিকে সবুজের হাতছানি। দু’পাশে সুউচ্চ পাহাড়। মাঝখান দিয়ে নদী আপন বেগে বয়ে চলেছে। সময় কাটছিল নদীর দিকে তাকিয়েই। জ্যাম ছাড়তে দৃশ্যপট পাল্টাতে লাগল। পাহাড়ি পথের বাঁকে বাঁকে আপেল বাগান। পাইন ও দেওদারের ঘন সবুজ বন। চিকন পাতার ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়ছে মেঘছেঁড়া রোদ। যত্রতত্র পাহাড়ের গা বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝোরা।
হরশিল। এটি ভাগীরথী আর জালন্ধরী নদীর মিলনস্থল। দু’জনে মিলেমিশে এগিয়ে গিয়েছেন দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে দেখা করতে। পুরাণ অনুসারে একসময় নদীরূপিণী দুই দেবীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। তাঁদের মধ্যে কে বড়? ভাগীরথীই গঙ্গার মূল প্রবাহ। কাজেই সবার কাছে ভাগীরথী বড়। জালন্ধরী তা মানবেন কেন? শেষে নারায়ণকে বিচারক ঠিক করা হল। তাঁর তো উভয়সঙ্কট। অনেক ভেবে তিনি এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করলেন। নিজে পাথর হয়ে গেলেন। নারায়ণরূপী সেই হরি শিলার ওপর দুই দেবী ঝাঁপিয়ে পড়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে এগিয়ে চললেন। সেই হরি শিলা থেকে এই জায়গার নাম হরশিল।
এখানে এক অভিশপ্ত রাজার বাস ছিল। তিনি ফ্রেডরিক ই উইলসন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে ছিলেন তিনি। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পর তিনি পালাতে শুরু করেন। অনেকে বলেন এই সময় তিনি ডুয়েলে কোনও ইংরেজ অফিসারকে মেরে ফেলেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল গঙ্গার উৎসমুখ গঙ্গোত্রীর দিকে যাওয়ার, অর্থাৎ ইংরেজ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বাইরে বেরনো।
প্রথমে তেহরি গাড়োয়ালে আশ্রয় চান। কিন্তু গাড়োয়ালের রাজা তো ব্রিটিশদের বন্ধু ছিলেন, উইলসনকে সাহায্য করলেন না। গঙ্গার তীর বরাবর তার উৎসমুখের দিকে এগতে লাগলেন তিনি। এসে পৌঁছলেন ভাগীরথী উপত্যকার শেষ জনবসতি, হরশিলে। বুদ্ধিমান উইলসন দুনিয়াদারি বুঝতেন। কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন। উপত্যকায় গাছের অভাব ছিল না। জানা যায়, তিনি মোটা মোটা সেই গাছের গুঁড়ি ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দিতেন। সেগুলি হরিদ্বারে তাঁর লোকরা সংগ্রহ করে বিক্রি করত। ধীরে ধীরে রাজার মতো বিত্তশালী হয়ে ওঠেন তিনি। ব্রিটিশ রেলের স্লিপার তৈরি করতে কাঠের গুঁড়ি কাজে লাগত। তাছাড়া কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। উইলসন এই কাঠ সরবরাহ করতে লাগলেন। তাঁকে গাছের গুঁড়ির জন্য পয়সাও দিতে হতো না। ব্যবসা তরতরিয়ে বাড়তে লাগল। তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হলেন। হরশিলে বিবর্তন আনলেন উইলসন। এখানকার আপেলের সুনাম আছে এখনও। সেই আপেল চাষ প্রথম করেছিলেন তিনিই। এমনকী রাজমা চাষও তাঁরই কৃতিত্ব। নদীবহুল এই এলাকাগুলিতে বহু জায়গায় তিনি ব্রিজ তৈরি করেন। ভাগীরথী উপত্যকার অঘোষিত মুকুটহীন রাজায় পরিণত হলেন তিনি। জীবজন্তু শিকারও করতেন, তাদের চামড়াও নাকি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হতো। জানা যায় এই কারণে এলাকা প্রাণীশূন্য হতে থাকে। আর সেটাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। ভাগীরথী উপত্যকার দেবতা সোমেশ্বর, তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হন। দেবতার পুরোহিত তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে উইলসন ‘নির্বংশ’ হয়ে যাবেন। ১৮৮৩ সালে মুসৌরিতে উইলসন মারা যান। ততদিনে তাঁর জীবিত পুত্রের সংখ্যা তিন থেকে কমে এক। শেষ পরিচিত বংশধর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। কাঠের মিলগুলিও পরবর্তীতে আগুনে ভস্মীভূত হয়।
চলন্ত গাড়ি থেকে বাইরের দিকে তাকালাম। কোথাও সবুজের ছোঁয়া মাখা পাহাড়, কোথাও ধূসর পাহাড়। আর একটু ওপরের দিকে তাকালেই একরাশ মুগ্ধতা ও মোহময় আকর্ষণ ছড়ানো শ্বেতশুভ্র বরফে আচ্ছাদিত ঝলমলে পাহাড়! মেঘে ঢেকে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে পাহাড়ের রং বদল দেখতে দেখতে যেন সুখেও বিমর্ষ হয়ে পড়ছিলাম! এক একসময় শ্বেতশুভ্র পাহাড়ের চূড়াগুলো এক এক রং ধারণ করে চলেছে!
গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম দুপুর দুটোয়। তিন ঘণ্টার পথ ছ’ঘণ্টায়। আমাদের ডানপাশে গঙ্গা। এক অলিখিত রোমাঞ্চ। এই নদীর স্রোতে বয়ে গিয়েছে কত যুগের ইতিহাস। গঙ্গা তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মায়াবী জালের আচ্ছাদনে জড়িয়ে রেখেছে ভারতের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ। এককালে তার দুই পাড়ে গড়ে উঠেছিল কত জনবসতি, কত রাজত্ব প্রাসাদ, কত রাজপ্রাসাদ। এখনও ইতিউতি তাদের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।
বইয়ে পড়া অতীতের সঙ্গে বর্তমানের গঙ্গোত্রীর কোনও মিল নেই। আজ এ জায়গা জনবহুল। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। এই ভাগীরথী দুরন্ত, দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। আকারে ক্ষীণ। হিমশীতল তার স্পর্শ। ভাগীরথী-গঙ্গার দু’পাশে অনেক বাড়িঘর। কোনওটা ধর্মশালা। কোনওটা হোটেল। আর কতকগুলি দোকানের পসরা। তারই মাঝে কিছু সাধুর আস্তানা। নিভৃতে সাধন ভজনের নিশ্চিন্ত স্থান। গঙ্গোত্রী মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকে ভাগীরথী পার হয়ে একটা মাড়োয়ারি ধর্মশালায় ঠাঁই হল।
পাইন আর দেবদারুর ছায়ায় ঢাকা স্বর্গ ও মর্তের সন্ধিস্থল, ভাগীরথী গঙ্গার উৎসলোক এই গঙ্গোত্রী। দুপুরে খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম গঙ্গোত্রী মন্দির দেখার জন্য। মূল মন্দির পুরোটাই মার্বেল পাথরে তৈরি। ২০ ফুট উঁচু। মন্দিরের গা-লাগোয়া নাটমন্দির। তিনটি প্রবেশদ্বার। সামনে পাথরের সিঁড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গাড়োয়াল হিমালয় ছিল নেপালরাজের অধীন। তাঁর সেনাপতি অমর সিং থাপা ছিলেন এই অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর উদ্যোগেই গড়ে ওঠে গঙ্গোত্রীর মূল মন্দির। পরবর্তী সময়ে জয়পুরের রাজপরিবার মন্দিরের সংস্কার করেন। মন্দিরের জানলায় ঝরোকার মতো কারুকাজ। নাটমন্দিরে ঢুকে মা গঙ্গার বিগ্রহ দর্শন করলাম। গর্ভগৃহের মুখ পুবে, অর্থাৎ গোমুখের দিকে। মূল মন্দিরের ঠিক ডানপাশে শিবের মন্দির। আকারে মূল মন্দিরের চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট। মন্দির চত্বরের উত্তরভাগে পাহাড়ের ঢালের দিকে ইটের দেওয়াল। সে দেওয়ালের গায়ে আধুনিক শৈলীর গ্রাফিতি। মর্তে গঙ্গা অবতরণের দৃশ্য আঁকা হয়েছে তাতে। মন্দিরের পাশে আছে ভগীরথ শিলা। শিলার সঙ্গে দেবী গঙ্গার মর্তে অবতরণ সম্পর্কযুক্ত।
পুরাণ মতে, প্রাচীনকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক সূর্যবংশীয় রাজা ছিলেন। তার দুই রানি। কেশিনী এবং সুমতি। কিন্তু তাঁদের কারও সন্তান হয় না। তাই সন্তানলাভের আশায় রাজা সগর হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত পৰ্বতে ঘোরতর তপস্যায় বসলেন। ভৃগুমুনি তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হন। তাঁকে বর দেন যে, তাঁর দুই রানির গর্ভেই সন্তান হবে। সগরের রানিরা মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের কার গর্ভে কীরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। ভৃগু তাঁদের নিজেদের মনের ইচ্ছা বলতে বললেন। কেশিনী এক পুত্র ও সুমতি ষাট হাজার সন্তান প্রার্থনা করলেন। পরবর্তীকালে কেশিনী এক পুত্র প্রসব করলেন। তাঁর নাম হল অসমঞ্জ। অসমঞ্জের ১৭তম প্রজন্ম হলেন ভগবান রাম। সুমতির গর্ভে ষাট হাজার সন্তান হল। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্তী জায়গায় সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। তার আদেশে অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান যজ্ঞাশ্বের অনুধাবন করলেন। কিন্তু রাজা সগরের যজ্ঞ দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভয় পেলেন। মর্তলোকের অধিপতি হওয়ার পর সগররাজ যদি স্বর্গেরও অধিপতি হতে ইচ্ছা করেন, তখন কী হবে! ইন্দ্র ফন্দি আঁটলেন। দেবরাজ রাক্ষসরূপ ধারণ করে সেই অশ্ব অপহরণ করলেন। অশ্বমেধের ঘোড়া বেপাত্তা। রাজা সগর সে খবর শুনে তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে ঘোড়ার খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে ইন্দ্র ঘোড়াখানা চুরি করে চুপিচুপি কপিলমুনির আশ্রমে বেঁধে রেখে এলেন। ষাট হাজার রাজকুমার ত্রিলোক চষে শেষমেশ এসে পৌঁছলেন কপিলমুনির আশ্রমে। ঘোড়া বাঁধা দেখে রাগে অন্ধ হয়ে তাঁরা ভাবলেন এসব কপিলমুনিরই কারসাজি। প্রবল আক্রোশে আশ্রম লণ্ডভণ্ড করলেন তাঁরা। তপস্যা ভাঙল কপিলমুনির। তিনি রেগে রাজকুমারদের চোখের পলকে ভস্ম করে দিলেন। বেচারি বৃদ্ধ সগররাজ। প্রথমে হারালেন অশ্বমেধের ঘোড়া, তারপর হারালেন ষাট হাজার সন্তান। সন্তানদের কোনও খবর না পেয়ে রাজকুমার আর ঘোড়া খোঁজার দায়িত্ব দিলেন তাঁর পৌত্র অংশুমান। কাকাদের খুঁজতে খুঁজতে অংশুমান এসে পড়লেন সেই কপিলমুনির আশ্রমে। অংশুমানের মধুর ব্যবহারে কপিলমুনি সন্তুষ্ট হলেন। অশ্বমেধের ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন। আর বলে দিলেন তাঁর কাকাদের মুক্তির একমাত্র উপায়, গঙ্গার পবিত্র বারিধারা। কিন্তু গঙ্গা তো স্বর্গের দেবী। এই মাটির পৃথিবীতে কেমন করে তাঁর বারিধারা পাবেন অংশুমান? অগত্যা শুধু ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। অযোধ্যার রাজা হলেন অংশুমান। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র দিলীপ। এই দিলীপের পুত্র ছিলেন ভগীরথ। তিনি সংকল্প করেছিলেন গঙ্গার স্পর্শে মুক্ত করবেন তাঁর পূর্বপুরুষদের। শুরু করলেন ঘোর তপস্যা। হাজার বছরের তপস্যায় মন গলল গঙ্গার। তিনি স্বর্গ থেকে ধরাধামে নেমে আসতে রাজি হলেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে মর্তে নামার সময় গঙ্গার প্রবল বেগে ধরিত্রীতে প্রলয় ঘটবে। তাহলে তার বেগ সামলাবে কে? দেবাদিদেব ভোলানাথই একমাত্র পারেন এই কাজ করতে, যদি তিনি রাজি হন। অতএব আবার তপস্যা। দীর্ঘ তপস্যার পর তুষ্ট হলেন মহাদেব। রাজি হলেন গঙ্গার জলরাশিকে তাঁর জটায় ধারণ করতে। ধরাধামে অবতরণ করলেন গঙ্গা।
পরের দিন বেরলাম পাণ্ডবগুহার পথে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয়-নিধনের পাপস্খলনের জন্য দেবযজ্ঞ করতে পাণ্ডবরা নাকি এখানে এসেছিলেন। তাঁদের নিদর্শন হিসেবে চিরবনের ভেতরে আজও আছে পাণ্ডবগুহা। জঙ্গলে ঢাকা পথ। গাছেদের সারির মধ্যে দিয়েই সরু একটা পায়ে চলা পথ পশ্চিমে চলে গিয়েছে। একটা সাইনবোর্ডে লেখা ‘রোড টু পাণ্ডবগুহা।’ দু’পাশে বিশাল ঝাউ-পাইনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তাটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। আলো-ছায়ায় ঢাকা। কিছুক্ষণ আগেও পাহাড়ের ঢালে ছিল ফাঁকা জঙ্গল। যত এগচ্ছি ধীরে ধীরে চারদিক থেকে বড় বড় পাইনের দল ভিড় করে রাস্তাটিকে চেপে ধরেছে। কেমন যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। গাছগুলো আস্তে আস্তে আবছা হতে শুরু করেছে। কোলাহলমুক্ত নির্জন পরিবেশ। নাম না জানা এক ধরনের হলুদ ফুল রাস্তার পাশে ফুটে আছে। ছায়াগহন সকালে কুয়াশার ঘনঘটার মাঝে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা থেকে বহু দূরে এত সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজানো! কে জানে! একটা শান্ত নিস্তব্ধতা মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। পাতাগুলোয় হাত ছোঁয়াই। তির তির করে কেঁপে ওঠে। ফিসফিসিয়ে কিছু বলতে চায়। রাস্তার ধারে দেবদারুর ঝরে পড়া শুকনো বাদামি পাতাগুলোর ওপর একটা চিপসের প্যাকেট গা এলিয়ে পড়ে আছে। ধুলোমাখা। এক বৃদ্ধ বল্লরী তার শিশিরসিক্ত শরীরটাকে প্যাকেটের ওপর বিছিয়ে দিয়ে কুসুম রোদে আয়েসে মগ্ন। গায়ে কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফুল। সেগুলোর অদ্ভুত লাবণ্য। যেন কোনও অদৃশ্য দেবীর পদতলে তারা প্রকৃতির অঞ্জলি হয়ে পড়ে আছে অনাদরে। এসবের মাঝে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা খুব বিসদৃশ।
মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে নিতে কখন পৌঁছে গিয়েছি আমাদের গন্তব্যে, টের পাইনি। সামনেই চিরগাছের নীচে প্রকাণ্ড একখানা পাথর। ওপরে লাল কালিতে লেখা ওঁ। ঠিক তার নীচে একখানা পাঁচ-ছয় ফিটের মুখ। একটা কালো টিনের দরজা আধ-খোলা। ডানপাশে হিন্দিতে নীল কালি দিয়ে লেখা ‘হরি ওঁ’। এটিই পাণ্ডবগুহা। সাহস করে মাথাটা একটু নিচু করেই ঢুকে পড়লাম গুহায়। ভেতরটা ছায়াময়। স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মধ্যেই লুকিয়ে অপার রহস্য। গুহার উল্টোমুখে আরও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মুখ রয়েছে। আর বাঁদিকের দেওয়ালে একটি ছোট জানালা। এই দুই পথে বাইরে থেকে সূর্যের আলো সামান্য উঁকি মারছে গুহার ভেতর। গুহার একপাশে ধিকিধিকি করে ধুনি জ্বলছে। তার আভায় চোখে পড়ল, এক জায়গায় ফুলের মালা, ফুলের স্তূপ। নীচে ধূপ-ধুনোর ছোট ছোট পোড়া টুকরো। কিছুটা দূরে একপাশে রান্নার সামগ্রী। দেওয়াল বেশ অমসৃণ। গুহার ছাদটি কালিমাখা। ধুনির সামনে একজন জীর্ণদেহী সাধু বসে রয়েছেন। ধোঁয়াশায় তাঁর মুখ-চোখ কিছুই বিশেষভাবে বোঝা গেল না। আমাদের দেখে তিনি খুব একটা গ্রাহ্য করলেন না। ভেতরে আরও কিছু আছে তবে অন্ধকারে চেনা দায়। ঘোর অন্ধকার। কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে সব।
সেখান থেকে বেরিয়ে প্রায় ১ কিলোমিটার চলে আসার পর বাঁ হাতে একটি কুণ্ড। গৌরীকুণ্ড। ভাগীরথী ঝাঁপিয়ে পড়েছে এখানে। কী তার গর্জন! তীব্র জলোচ্ছ্বাস। কুণ্ডের পাথুরে দেওয়ালের তামাটে রং জলকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। ৫০০ মিটার যাওয়ার পরই আরেকটি কুণ্ড। সুরজকুণ্ড। কিছুটা নীচে নামার পর ছোট্ট একটা পুল। সেই পুলের ওপর থেকে দেখলাম সাদাটে পাথরের অলিগলি বেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভাগীরথী। কত হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে চলতে চলতে ভাগীরথীর জলধারা তৈরি করেছে অজস্র গলিপথ আর ছোট ছোট সুড়ঙ্গ। সেই আঁকাবাঁকা মসৃণ গলিপথ বেয়ে ভাগীরথীর জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
কুণ্ডের দিকে তাকাতে পাথরের একটি মুখ দেখতে পেলাম। স্থানীয়রা বলেন সেটি নাকি শিবের মুখ। এখানেই শিব তার জটায় ধারণ করে দেবী গঙ্গার তীব্র গতিকে ধীর করে মর্তে নামিয়ে আনেন। গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশ দিয়ে কয়েক পা এগতেই একদম ভাগীরথীর কিনারায় চলে এলাম। বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। অন্যদিকে ছোট ছোট মন্দিরের সারি। প্রধান ঘাটের ঠিক পাশেই সিদ্ধি বিনায়কের মন্দির। তার সামনে প্রশস্ত দালান। এখানেই সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি হয়। ভাগীরথীর জলে একটু পা ডোবালাম। একটু এগতে গোড়ালি থেকে হাঁটু ভিজে উঠল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই পা যেন জমে গেল। এতটাই হিমশীতল সে জল। অথচ চোখের সামনে কত পুণ্যার্থী ওই জলে চান করছে। কীসের জোরে? বোধহয় ভক্তির।
সিঁড়ির একটা ধাপে বসে পড়লাম। রোদ পড়ে এসেছে। দু’দিকের পাহাড়ের গায়ে যেন রঙের মেলা। হিমালয় জুড়ে যেন কে ছড়িয়ে দিয়েছে বসন্তের আবির। আর রঙিন এই উপত্যকার গভীর খাত বেয়ে হেঁটে চলেছে গৈরিকবসনা এক উদাসিনী। ভাগীরথী।
আমরা চলেছি উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর পথে। চলতে চলতে মানুষের হই-হট্টগোলে তাকিয়ে দেখি ভয়ঙ্কর জ্যামে আটকে আছে আমাদের গাড়ি। যানজট নিয়ন্ত্রণে কোনও পুলিসের দেখা মিলল না। মাথার ওপর সাদা তুলোর মতো ছেঁড়া মেঘ। চারদিকে সবুজের হাতছানি। দু’পাশে সুউচ্চ পাহাড়। মাঝখান দিয়ে নদী আপন বেগে বয়ে চলেছে। সময় কাটছিল নদীর দিকে তাকিয়েই। জ্যাম ছাড়তে দৃশ্যপট পাল্টাতে লাগল। পাহাড়ি পথের বাঁকে বাঁকে আপেল বাগান। পাইন ও দেওদারের ঘন সবুজ বন। চিকন পাতার ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়ছে মেঘছেঁড়া রোদ। যত্রতত্র পাহাড়ের গা বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝোরা।
হরশিল। এটি ভাগীরথী আর জালন্ধরী নদীর মিলনস্থল। দু’জনে মিলেমিশে এগিয়ে গিয়েছেন দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে দেখা করতে। পুরাণ অনুসারে একসময় নদীরূপিণী দুই দেবীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। তাঁদের মধ্যে কে বড়? ভাগীরথীই গঙ্গার মূল প্রবাহ। কাজেই সবার কাছে ভাগীরথী বড়। জালন্ধরী তা মানবেন কেন? শেষে নারায়ণকে বিচারক ঠিক করা হল। তাঁর তো উভয়সঙ্কট। অনেক ভেবে তিনি এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করলেন। নিজে পাথর হয়ে গেলেন। নারায়ণরূপী সেই হরি শিলার ওপর দুই দেবী ঝাঁপিয়ে পড়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে এগিয়ে চললেন। সেই হরি শিলা থেকে এই জায়গার নাম হরশিল।
এখানে এক অভিশপ্ত রাজার বাস ছিল। তিনি ফ্রেডরিক ই উইলসন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে ছিলেন তিনি। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পর তিনি পালাতে শুরু করেন। অনেকে বলেন এই সময় তিনি ডুয়েলে কোনও ইংরেজ অফিসারকে মেরে ফেলেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল গঙ্গার উৎসমুখ গঙ্গোত্রীর দিকে যাওয়ার, অর্থাৎ ইংরেজ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বাইরে বেরনো।
প্রথমে তেহরি গাড়োয়ালে আশ্রয় চান। কিন্তু গাড়োয়ালের রাজা তো ব্রিটিশদের বন্ধু ছিলেন, উইলসনকে সাহায্য করলেন না। গঙ্গার তীর বরাবর তার উৎসমুখের দিকে এগতে লাগলেন তিনি। এসে পৌঁছলেন ভাগীরথী উপত্যকার শেষ জনবসতি, হরশিলে। বুদ্ধিমান উইলসন দুনিয়াদারি বুঝতেন। কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন। উপত্যকায় গাছের অভাব ছিল না। জানা যায়, তিনি মোটা মোটা সেই গাছের গুঁড়ি ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দিতেন। সেগুলি হরিদ্বারে তাঁর লোকরা সংগ্রহ করে বিক্রি করত। ধীরে ধীরে রাজার মতো বিত্তশালী হয়ে ওঠেন তিনি। ব্রিটিশ রেলের স্লিপার তৈরি করতে কাঠের গুঁড়ি কাজে লাগত। তাছাড়া কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। উইলসন এই কাঠ সরবরাহ করতে লাগলেন। তাঁকে গাছের গুঁড়ির জন্য পয়সাও দিতে হতো না। ব্যবসা তরতরিয়ে বাড়তে লাগল। তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হলেন। হরশিলে বিবর্তন আনলেন উইলসন। এখানকার আপেলের সুনাম আছে এখনও। সেই আপেল চাষ প্রথম করেছিলেন তিনিই। এমনকী রাজমা চাষও তাঁরই কৃতিত্ব। নদীবহুল এই এলাকাগুলিতে বহু জায়গায় তিনি ব্রিজ তৈরি করেন। ভাগীরথী উপত্যকার অঘোষিত মুকুটহীন রাজায় পরিণত হলেন তিনি। জীবজন্তু শিকারও করতেন, তাদের চামড়াও নাকি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হতো। জানা যায় এই কারণে এলাকা প্রাণীশূন্য হতে থাকে। আর সেটাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। ভাগীরথী উপত্যকার দেবতা সোমেশ্বর, তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হন। দেবতার পুরোহিত তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে উইলসন ‘নির্বংশ’ হয়ে যাবেন। ১৮৮৩ সালে মুসৌরিতে উইলসন মারা যান। ততদিনে তাঁর জীবিত পুত্রের সংখ্যা তিন থেকে কমে এক। শেষ পরিচিত বংশধর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। কাঠের মিলগুলিও পরবর্তীতে আগুনে ভস্মীভূত হয়।
চলন্ত গাড়ি থেকে বাইরের দিকে তাকালাম। কোথাও সবুজের ছোঁয়া মাখা পাহাড়, কোথাও ধূসর পাহাড়। আর একটু ওপরের দিকে তাকালেই একরাশ মুগ্ধতা ও মোহময় আকর্ষণ ছড়ানো শ্বেতশুভ্র বরফে আচ্ছাদিত ঝলমলে পাহাড়! মেঘে ঢেকে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে পাহাড়ের রং বদল দেখতে দেখতে যেন সুখেও বিমর্ষ হয়ে পড়ছিলাম! এক একসময় শ্বেতশুভ্র পাহাড়ের চূড়াগুলো এক এক রং ধারণ করে চলেছে!
গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম দুপুর দুটোয়। তিন ঘণ্টার পথ ছ’ঘণ্টায়। আমাদের ডানপাশে গঙ্গা। এক অলিখিত রোমাঞ্চ। এই নদীর স্রোতে বয়ে গিয়েছে কত যুগের ইতিহাস। গঙ্গা তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মায়াবী জালের আচ্ছাদনে জড়িয়ে রেখেছে ভারতের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ। এককালে তার দুই পাড়ে গড়ে উঠেছিল কত জনবসতি, কত রাজত্ব প্রাসাদ, কত রাজপ্রাসাদ। এখনও ইতিউতি তাদের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।
বইয়ে পড়া অতীতের সঙ্গে বর্তমানের গঙ্গোত্রীর কোনও মিল নেই। আজ এ জায়গা জনবহুল। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। এই ভাগীরথী দুরন্ত, দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। আকারে ক্ষীণ। হিমশীতল তার স্পর্শ। ভাগীরথী-গঙ্গার দু’পাশে অনেক বাড়িঘর। কোনওটা ধর্মশালা। কোনওটা হোটেল। আর কতকগুলি দোকানের পসরা। তারই মাঝে কিছু সাধুর আস্তানা। নিভৃতে সাধন ভজনের নিশ্চিন্ত স্থান। গঙ্গোত্রী মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকে ভাগীরথী পার হয়ে একটা মাড়োয়ারি ধর্মশালায় ঠাঁই হল।
পাইন আর দেবদারুর ছায়ায় ঢাকা স্বর্গ ও মর্তের সন্ধিস্থল, ভাগীরথী গঙ্গার উৎসলোক এই গঙ্গোত্রী। দুপুরে খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম গঙ্গোত্রী মন্দির দেখার জন্য। মূল মন্দির পুরোটাই মার্বেল পাথরে তৈরি। ২০ ফুট উঁচু। মন্দিরের গা-লাগোয়া নাটমন্দির। তিনটি প্রবেশদ্বার। সামনে পাথরের সিঁড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গাড়োয়াল হিমালয় ছিল নেপালরাজের অধীন। তাঁর সেনাপতি অমর সিং থাপা ছিলেন এই অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর উদ্যোগেই গড়ে ওঠে গঙ্গোত্রীর মূল মন্দির। পরবর্তী সময়ে জয়পুরের রাজপরিবার মন্দিরের সংস্কার করেন। মন্দিরের জানলায় ঝরোকার মতো কারুকাজ। নাটমন্দিরে ঢুকে মা গঙ্গার বিগ্রহ দর্শন করলাম। গর্ভগৃহের মুখ পুবে, অর্থাৎ গোমুখের দিকে। মূল মন্দিরের ঠিক ডানপাশে শিবের মন্দির। আকারে মূল মন্দিরের চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট। মন্দির চত্বরের উত্তরভাগে পাহাড়ের ঢালের দিকে ইটের দেওয়াল। সে দেওয়ালের গায়ে আধুনিক শৈলীর গ্রাফিতি। মর্তে গঙ্গা অবতরণের দৃশ্য আঁকা হয়েছে তাতে। মন্দিরের পাশে আছে ভগীরথ শিলা। শিলার সঙ্গে দেবী গঙ্গার মর্তে অবতরণ সম্পর্কযুক্ত।
পুরাণ মতে, প্রাচীনকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক সূর্যবংশীয় রাজা ছিলেন। তার দুই রানি। কেশিনী এবং সুমতি। কিন্তু তাঁদের কারও সন্তান হয় না। তাই সন্তানলাভের আশায় রাজা সগর হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত পৰ্বতে ঘোরতর তপস্যায় বসলেন। ভৃগুমুনি তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হন। তাঁকে বর দেন যে, তাঁর দুই রানির গর্ভেই সন্তান হবে। সগরের রানিরা মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের কার গর্ভে কীরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। ভৃগু তাঁদের নিজেদের মনের ইচ্ছা বলতে বললেন। কেশিনী এক পুত্র ও সুমতি ষাট হাজার সন্তান প্রার্থনা করলেন। পরবর্তীকালে কেশিনী এক পুত্র প্রসব করলেন। তাঁর নাম হল অসমঞ্জ। অসমঞ্জের ১৭তম প্রজন্ম হলেন ভগবান রাম। সুমতির গর্ভে ষাট হাজার সন্তান হল। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্তী জায়গায় সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। তার আদেশে অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান যজ্ঞাশ্বের অনুধাবন করলেন। কিন্তু রাজা সগরের যজ্ঞ দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভয় পেলেন। মর্তলোকের অধিপতি হওয়ার পর সগররাজ যদি স্বর্গেরও অধিপতি হতে ইচ্ছা করেন, তখন কী হবে! ইন্দ্র ফন্দি আঁটলেন। দেবরাজ রাক্ষসরূপ ধারণ করে সেই অশ্ব অপহরণ করলেন। অশ্বমেধের ঘোড়া বেপাত্তা। রাজা সগর সে খবর শুনে তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে ঘোড়ার খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে ইন্দ্র ঘোড়াখানা চুরি করে চুপিচুপি কপিলমুনির আশ্রমে বেঁধে রেখে এলেন। ষাট হাজার রাজকুমার ত্রিলোক চষে শেষমেশ এসে পৌঁছলেন কপিলমুনির আশ্রমে। ঘোড়া বাঁধা দেখে রাগে অন্ধ হয়ে তাঁরা ভাবলেন এসব কপিলমুনিরই কারসাজি। প্রবল আক্রোশে আশ্রম লণ্ডভণ্ড করলেন তাঁরা। তপস্যা ভাঙল কপিলমুনির। তিনি রেগে রাজকুমারদের চোখের পলকে ভস্ম করে দিলেন। বেচারি বৃদ্ধ সগররাজ। প্রথমে হারালেন অশ্বমেধের ঘোড়া, তারপর হারালেন ষাট হাজার সন্তান। সন্তানদের কোনও খবর না পেয়ে রাজকুমার আর ঘোড়া খোঁজার দায়িত্ব দিলেন তাঁর পৌত্র অংশুমান। কাকাদের খুঁজতে খুঁজতে অংশুমান এসে পড়লেন সেই কপিলমুনির আশ্রমে। অংশুমানের মধুর ব্যবহারে কপিলমুনি সন্তুষ্ট হলেন। অশ্বমেধের ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন। আর বলে দিলেন তাঁর কাকাদের মুক্তির একমাত্র উপায়, গঙ্গার পবিত্র বারিধারা। কিন্তু গঙ্গা তো স্বর্গের দেবী। এই মাটির পৃথিবীতে কেমন করে তাঁর বারিধারা পাবেন অংশুমান? অগত্যা শুধু ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। অযোধ্যার রাজা হলেন অংশুমান। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র দিলীপ। এই দিলীপের পুত্র ছিলেন ভগীরথ। তিনি সংকল্প করেছিলেন গঙ্গার স্পর্শে মুক্ত করবেন তাঁর পূর্বপুরুষদের। শুরু করলেন ঘোর তপস্যা। হাজার বছরের তপস্যায় মন গলল গঙ্গার। তিনি স্বর্গ থেকে ধরাধামে নেমে আসতে রাজি হলেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে মর্তে নামার সময় গঙ্গার প্রবল বেগে ধরিত্রীতে প্রলয় ঘটবে। তাহলে তার বেগ সামলাবে কে? দেবাদিদেব ভোলানাথই একমাত্র পারেন এই কাজ করতে, যদি তিনি রাজি হন। অতএব আবার তপস্যা। দীর্ঘ তপস্যার পর তুষ্ট হলেন মহাদেব। রাজি হলেন গঙ্গার জলরাশিকে তাঁর জটায় ধারণ করতে। ধরাধামে অবতরণ করলেন গঙ্গা।
পরের দিন বেরলাম পাণ্ডবগুহার পথে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয়-নিধনের পাপস্খলনের জন্য দেবযজ্ঞ করতে পাণ্ডবরা নাকি এখানে এসেছিলেন। তাঁদের নিদর্শন হিসেবে চিরবনের ভেতরে আজও আছে পাণ্ডবগুহা। জঙ্গলে ঢাকা পথ। গাছেদের সারির মধ্যে দিয়েই সরু একটা পায়ে চলা পথ পশ্চিমে চলে গিয়েছে। একটা সাইনবোর্ডে লেখা ‘রোড টু পাণ্ডবগুহা।’ দু’পাশে বিশাল ঝাউ-পাইনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তাটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। আলো-ছায়ায় ঢাকা। কিছুক্ষণ আগেও পাহাড়ের ঢালে ছিল ফাঁকা জঙ্গল। যত এগচ্ছি ধীরে ধীরে চারদিক থেকে বড় বড় পাইনের দল ভিড় করে রাস্তাটিকে চেপে ধরেছে। কেমন যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। গাছগুলো আস্তে আস্তে আবছা হতে শুরু করেছে। কোলাহলমুক্ত নির্জন পরিবেশ। নাম না জানা এক ধরনের হলুদ ফুল রাস্তার পাশে ফুটে আছে। ছায়াগহন সকালে কুয়াশার ঘনঘটার মাঝে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা থেকে বহু দূরে এত সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজানো! কে জানে! একটা শান্ত নিস্তব্ধতা মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। পাতাগুলোয় হাত ছোঁয়াই। তির তির করে কেঁপে ওঠে। ফিসফিসিয়ে কিছু বলতে চায়। রাস্তার ধারে দেবদারুর ঝরে পড়া শুকনো বাদামি পাতাগুলোর ওপর একটা চিপসের প্যাকেট গা এলিয়ে পড়ে আছে। ধুলোমাখা। এক বৃদ্ধ বল্লরী তার শিশিরসিক্ত শরীরটাকে প্যাকেটের ওপর বিছিয়ে দিয়ে কুসুম রোদে আয়েসে মগ্ন। গায়ে কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফুল। সেগুলোর অদ্ভুত লাবণ্য। যেন কোনও অদৃশ্য দেবীর পদতলে তারা প্রকৃতির অঞ্জলি হয়ে পড়ে আছে অনাদরে। এসবের মাঝে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা খুব বিসদৃশ।
মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে নিতে কখন পৌঁছে গিয়েছি আমাদের গন্তব্যে, টের পাইনি। সামনেই চিরগাছের নীচে প্রকাণ্ড একখানা পাথর। ওপরে লাল কালিতে লেখা ওঁ। ঠিক তার নীচে একখানা পাঁচ-ছয় ফিটের মুখ। একটা কালো টিনের দরজা আধ-খোলা। ডানপাশে হিন্দিতে নীল কালি দিয়ে লেখা ‘হরি ওঁ’। এটিই পাণ্ডবগুহা। সাহস করে মাথাটা একটু নিচু করেই ঢুকে পড়লাম গুহায়। ভেতরটা ছায়াময়। স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মধ্যেই লুকিয়ে অপার রহস্য। গুহার উল্টোমুখে আরও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মুখ রয়েছে। আর বাঁদিকের দেওয়ালে একটি ছোট জানালা। এই দুই পথে বাইরে থেকে সূর্যের আলো সামান্য উঁকি মারছে গুহার ভেতর। গুহার একপাশে ধিকিধিকি করে ধুনি জ্বলছে। তার আভায় চোখে পড়ল, এক জায়গায় ফুলের মালা, ফুলের স্তূপ। নীচে ধূপ-ধুনোর ছোট ছোট পোড়া টুকরো। কিছুটা দূরে একপাশে রান্নার সামগ্রী। দেওয়াল বেশ অমসৃণ। গুহার ছাদটি কালিমাখা। ধুনির সামনে একজন জীর্ণদেহী সাধু বসে রয়েছেন। ধোঁয়াশায় তাঁর মুখ-চোখ কিছুই বিশেষভাবে বোঝা গেল না। আমাদের দেখে তিনি খুব একটা গ্রাহ্য করলেন না। ভেতরে আরও কিছু আছে তবে অন্ধকারে চেনা দায়। ঘোর অন্ধকার। কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে সব।
সেখান থেকে বেরিয়ে প্রায় ১ কিলোমিটার চলে আসার পর বাঁ হাতে একটি কুণ্ড। গৌরীকুণ্ড। ভাগীরথী ঝাঁপিয়ে পড়েছে এখানে। কী তার গর্জন! তীব্র জলোচ্ছ্বাস। কুণ্ডের পাথুরে দেওয়ালের তামাটে রং জলকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। ৫০০ মিটার যাওয়ার পরই আরেকটি কুণ্ড। সুরজকুণ্ড। কিছুটা নীচে নামার পর ছোট্ট একটা পুল। সেই পুলের ওপর থেকে দেখলাম সাদাটে পাথরের অলিগলি বেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভাগীরথী। কত হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে চলতে চলতে ভাগীরথীর জলধারা তৈরি করেছে অজস্র গলিপথ আর ছোট ছোট সুড়ঙ্গ। সেই আঁকাবাঁকা মসৃণ গলিপথ বেয়ে ভাগীরথীর জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
কুণ্ডের দিকে তাকাতে পাথরের একটি মুখ দেখতে পেলাম। স্থানীয়রা বলেন সেটি নাকি শিবের মুখ। এখানেই শিব তার জটায় ধারণ করে দেবী গঙ্গার তীব্র গতিকে ধীর করে মর্তে নামিয়ে আনেন। গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশ দিয়ে কয়েক পা এগতেই একদম ভাগীরথীর কিনারায় চলে এলাম। বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। অন্যদিকে ছোট ছোট মন্দিরের সারি। প্রধান ঘাটের ঠিক পাশেই সিদ্ধি বিনায়কের মন্দির। তার সামনে প্রশস্ত দালান। এখানেই সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি হয়। ভাগীরথীর জলে একটু পা ডোবালাম। একটু এগতে গোড়ালি থেকে হাঁটু ভিজে উঠল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই পা যেন জমে গেল। এতটাই হিমশীতল সে জল। অথচ চোখের সামনে কত পুণ্যার্থী ওই জলে চান করছে। কীসের জোরে? বোধহয় ভক্তির।
সিঁড়ির একটা ধাপে বসে পড়লাম। রোদ পড়ে এসেছে। দু’দিকের পাহাড়ের গায়ে যেন রঙের মেলা। হিমালয় জুড়ে যেন কে ছড়িয়ে দিয়েছে বসন্তের আবির। আর রঙিন এই উপত্যকার গভীর খাত বেয়ে হেঁটে চলেছে গৈরিকবসনা এক উদাসিনী। ভাগীরথী।
ছবি: লেখক
এখনকার দর
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৩.৫৯ টাকা | ৮৫.৩৩ টাকা |
| পাউন্ড | ১০৫.০৬ টাকা | ১০৮.৭৯ টাকা |
| ইউরো | ৮৭.৪৫ টাকা | ৯০.৮১ টাকা |
*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে