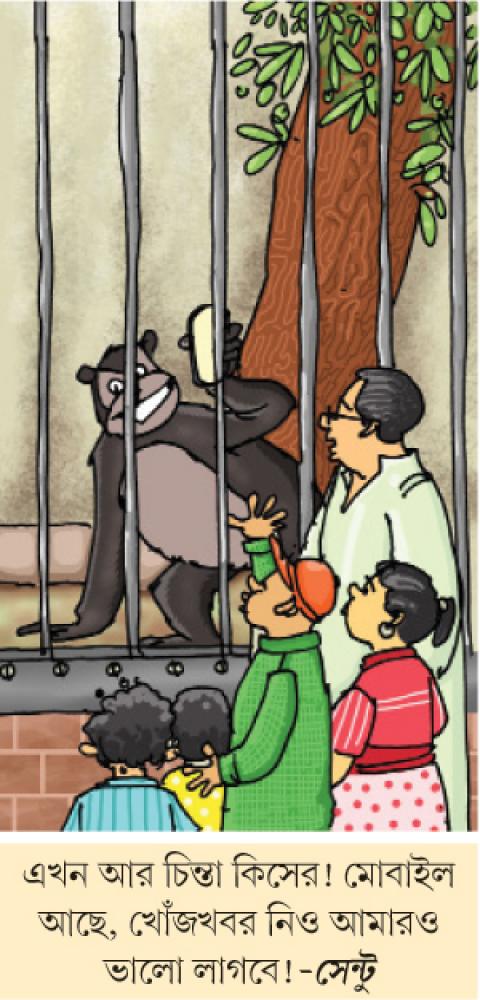কলকাতা, শনিবার ৪ জানুয়ারি ২০২৫, ২০ পৌষ ১৪৩১
দীর্ঘ জীবনের দাওয়াই
সিম্পল লিভিং হাই থিংকিং
ডাঃ সুকুমার মুখোপাধ্যায়

৮৯ বছর বয়স হল। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে রোগী দেখছি। এতদিন কেটে গেল সারা জীবনই কি স্বাস্থ্য অটুট থেকেছে? তা নয়। একবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। জোর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। সেই একবারই! বরাবর যতখানি স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা সম্ভব, করেছি। তাতে কর্মবিরতি হয়নি। আলাদা খেয়াল বলতে ভারী ব্যায়াম করিনি কোনওদিন। শুধু চেষ্টা করেছি পরিমিত জীবনযাপনের। বাকিটা এমনিই হয়ে গিয়েছে! আসলে আমি গ্রামের মানুষ। ছোটবেলায় বোলপুর স্কুলে পড়েছি। তারপর একটু বড় হয়ে কলকাতায় এসে পড়েছি বঙ্গবাসী স্কুল, হিন্দু স্কুলে। তারপর সেন্ট পল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজে। এই যে শিক্ষা গ্রহণের একটা দীর্ঘ যাত্রা অন্য কোনওদিকে খেয়াল রাখব কী! স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার কথা আলাদা করে ভাবিনি কোনওদিন। তখন দারিদ্র্য জড়িয়ে আছে সংসারে সেই অসুখ কবে সারবে তার ভাবনাই যেত না।
বাবা ইস্টার্ন রেলওয়ে ওয়ার্কস ম্যানেজার ছিলেন। তখনকার দিনে কতই বা আর বেতন ছিল! তবে আমাদের উপর বাবার শাসন ছিল যথেষ্ট। মা উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। তবে ছিলেন চরম কর্তব্যপরায়ণ।
আমরা তিন ভাই, চার বোন। আমার এক ভাই গত হয়েছে। আজকাল অতীতের দিকে তাকালে নজর চলে যায় ফসল ভরা মাঝের আলে। ধানমাঠের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি পাঠশালার দিকে। ভোলা মাস্টার অঙ্ক করাতেন। অঙ্ক না পারলে বেতের আঘাত না হলে নীলডাউন!
বাড়িতে সামান্য চায হতো। তাই গোরুর গাড়িও ছিল। তাই বলে সবসময় গোরুর গাড়ি মিলত না। তাই সুরুল গ্রাম থেকে মাঠ পেরিয়ে লাল মাটির রাস্তা ধরতাম খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাই বোনেরা। আমাদের সেই পথ থামত বোলপুর স্কুলে। ভাইয়েরা খুব সাহসী ছিল। মাঝেমধ্যেই খেলাচ্ছলে আমবাগানে চলে যেত আম চুরি করতে। আমার শৌর্যবীর্যের অভাব ছিল! আম চুরির কথা উঠলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যেতাম। একটু মুখচোরাও ছিলাম। তারপর কলকাতা গেলাম। থাকতে পারিনি বেশিদিন। শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ফিরে এক বছরের জন্য বঙ্গবাসী স্কুলে পড়াশোনা করলাম। তারপর গোটাটাই হিন্দু স্কুলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। অসম্ভব শৃঙ্খলাপরায়ণ, রাশভারী...। ১৯৫২ সালে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলাম স্কুল ফাইনাল।
সেই সময় নিজেকেই কলেজ স্থির করতে হতো। কোন কলেজে পড়লে ভালো হয়, কার কাছে খোঁজ করতে গেলে ভালো হয় কিছু জানতাম না। শুধু বাবার উত্সাহ আর মায়ের আশীর্বাদ ছিল। নিজেই ঘুরেছি কলেজে কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজেও সুযোগ পেয়েছিলাম, সেন্ট জেভিয়ার্সেও পড়ার সুযোগ ঘটেছিল। এত বোকা ছিলাম, সেন্ট জেভিয়ার্সে ইন্টারভিউ দেওয়ার পর বলেছিলাম— প্রেসিডেন্সিতেও অ্যাপ্লাই করেছি। কাল ইন্টারভিউ-এ কী হয় দেখি, দিয়ে এখানে আসব!
সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে সম্ভবত নাম কাটা পড়ল, আর প্রেসিডেন্সিতে সুযোগ পেলাম না। শেষে সেন্ট পলস কলেজে পড়লাম আইএসসি।
আজকালকার ছেলেমেয়েরা যতখানি চৌকস, সজাগ ততখানি ছিলাম না। ১৯৫৪ সালে সেন্ট পলস কলেজে আইএসসিতে প্রথম বিভাগে পাশ করলাম। আমার ইচ্ছা ছিল ইঞ্জিনিয়ার হব। শিবপুরে পরীক্ষাও দিলাম। আর ইন্টারভিউ দিলাম কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে। আমাদের বাড়িতে কোনও ডাক্তার ছিল না। মামা, মেসোমশাই, কাকা সকলেই ইঞ্জিনিয়ার। তাই শেষে ঠিক হল মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হব।
সেই ১৯৫৪ সাল থেকেই আমার ডাক্তারির যাত্রা শুরু। দেখলাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি, সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে লেখাপড়ায় তুখোড় ছেলেমেয়েরা এসেছে। জোর প্রতিযোগিতা। আমি তখন সবে ফুলপ্যান্ট পরতে শিখেছি সময় এগতে থাকল। দেখলাম ২ বছর পড়াশোনা করে ফার্স্ট হয়ে গিয়েছি! বহু লোকের নেক নজরে পড়ে গেলাম। আরও তিনবছর পরে দিলাম ফাইনাল এমবিবিএস। তাতেও প্রথম। শুনলাম ইউনিভার্সিটিতেও প্রথম হয়েছি! তবে পড়াশোনাটা হতো না। হল কারণ শেষ তিন বছর প্রতি মাসে মাসে ২৫ টাকা করে স্কলারশিপ পেয়েছি। আর কলেজের মাইনে মকুব হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় অনেকগুলো স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। না হলে কীভাবে পড়াশোনা করা হতো জানি না। মাকে কয়লাও ভাঙতে হয়েছে একসময়, কাচতে হয়েছে কাপড়!
এত সমস্যার মধ্যেও পাড়ায় মাঝেমধ্যে ফুটবল খেলতাম। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কোনও কোনও সময় যেতাম গড়ের মাঠ। কিন্তু কখনও পড়াশোনায় ফাঁকি দিতাম না। তার প্রধান কারণ ছিল বাবা-মা। ওরা সবসময় আমার লেখাপড়ার দিকে রাখতেন কড়া নজর। আর একজন ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। তিনি আমার মামা। বড় মাপের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আর যখনই বাড়ি আসতেন, অন্যান্যদের উদাহরণ টেনে বলতেন— দেখ কেমনভাবে সাফল্য পেয়েছে! কীভাবে পড়াশোনা করলে লাভ হবে!
শিক্ষকদের সান্নিধ্য
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হাউজস্টাফ শিপ করছিলাম। সেখানেই পেলাম ডাঃ শৈলেন সেনের মতো শিক্ষক। তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।
তাঁর কাছে শিখেছি দায়িত্ব নেওয়া, মানুষের সঙ্গে কথা বলার ধরন ইত্যাদি। তার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জি। তাঁর কাছ থেকে শিখেছি বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতা। পাশ করার পরে মনে জাগল এমডি পাশ করার ইচ্ছা। তখনকার দিনে এমডি পাশ করতে হলে অনেকখানি অর্থ লাগে। ডাঃ শৈলেন সেন বাড়তি কাজের ব্যবস্থা করে সেই অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিলেন। সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলাম ১৯৬২ সালে। পাশও করলাম। আমার তখন ইচ্ছা হল বিদেশে পড়তে যাব। অনেক টাকা লাগে। কী করে পাব। তখনকার দিনে দেওয়া হতো মাত্র ৩ পাউন্ড। সরকারি তরফে ৩ বছরের জন্য ছুটি মঞ্জুর হল। এডিনবরা আর লন্ডনে করলাম এমআরসিপি। বিদেশে থাকাকালীনই বাবা মারা গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে মেডিক্যাল কলেজে জয়েন করতেই বলা হল সোজা বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে চলে যেতে।
১৯৭০ সাল। একটা ব্যাগে রোজকার ব্যবহার্য স্বল্প কিছু সরঞ্জাম নিয়ে তীব্র গরমে ঢুকলাম বাঁকুড়া। অথচ তখন আমার হাতে ইংল্যান্ড, আমেরিকার চাকরি। মা বলল, এতগুলো ভাইবোনকে কে দেখবে? দেশ ছেড়ে যাওয়া যাবে না। মায়ের কথা অবহেলা করব কীভাবে!
গরম ছাড়াও বাঁকুড়ার আরও একটা বিশেষত্ব ছিল রাতে লোডশেডিং। তার মধ্যেই শুরু হল কাজ। অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকবে হয় তো! সেই যে বাঁকুড়া ঢুকলাম। পরবর্তী ৬ বছর কেটেছিল বাঁকুড়ায়। তখন রোগী দেখছি, ছাত্র পড়াচ্ছি ছয় মাসে একবার হয়তো কলকাতা যাচ্ছি। তার মধ্যেও পরিবারের দায়িত্ব পালন করছি ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। একদিন বউবাজারের বাড়িতে ফিরতে মা বলল এবার বিয়েটা সারতে হবে। না হলে নাকি অনেক বাধা আছে। মায়ের বিশ্বাস, কী আর বলি। সম্মতি দিলাম।
রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। তাঁরা বাড়ি দেখতে এলেন! দেখেই বললেন এখানে কী করে থাকবেন! আমি রেলের একটা গোটা কামরা বুক করে সবাইকে নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে বিয়ে দেব। জামা আদান প্রদান হল। অথচ কী আশ্চর্য নানা কারণে ওরা বিয়েটা শুধু পিছিয়ে যেতে লাগল। আসলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের বারং বার নানা কারণে ঝামেলা বাঁধত। তাতেই বিয়ের তারিখ নিয়ে বেশ কয়েকবার এমন হওয়ার পর মা বাধ্য হয়ে মা সম্বন্ধটা ভাঙতে বাধ্য হলেন।
বউবাজারের শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক অত্যন্ত সত্ শিক্ষকের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হল। সাতদিনের নোটিসে আমি বাঁকুড়া থেকে এসে বিয়ে করলাম। তখন নকশাল আন্দোলন। গাড়ি ছিল না। ট্যাক্সি ভাড়া করে বিয়ে করতে গেলাম। সেই গাড়ি পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল পুলিস।
শ্বশুরমশাই ছিলেন ট্রিপল এম এ। আইন পাশও করেছিলেন। শুধু অসত্ হতে পারবেন না বলে ল প্র্যাকটিস করেননি। বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করতেন। শাশুড়ি ছিলেন এম এ পাশ। মধ্যবিত্ত অথচ শিক্ষিত ওই পরিবারে আমার বিয়ে হয়ে গেল।
কয়েকদিন পরে বাঁকুড়া ঢুকলাম সস্ত্রীক। একটা বাড়িতে থাকতাম। স্বাচ্ছন্দ্যের বালাই নেই। বিশ্রামের আরামদায়ক জায়গা নেই! মাত্র হাজার দু’য়েক টাকা বেতন পাই! সেই অর্থ থেকেই সব কিছু চলে। টাকা বাঁচিয়ে ষাট টাকায় একটা খাট কেনা হল!
ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস বাড়তে থাকল। বাড়ছিল হাসপাতালের চাপও! অসুস্থ হওয়ারও যেন সময় নেই। ৬ বছর কেটে গেল। ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, সবই হচ্ছে শুধু শিক্ষাগত উত্কর্ষের জায়গায় বড় বেশি ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে! বিষয়টা ক্রমাগত সুচের মতো মস্তিষ্কে বিঁধছিল।
সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন অজিত পাঁজা। তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করলাম। জানালাম গত ছয় বছরে বাড়তি ছুটি নিইনি, কাজ করেছি, রোগী দেখেছি। শুধু শিক্ষাগত ক্ষেত্রের জায়গাটা পূরণ হচ্ছে না। এবার যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়।
সাতদিনের মধ্যে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক হিসেবে বদলি হয়ে গেলাম। সেটা ১৯৭৬ সাল। তখন কলকাতায় প্র্যাকটিস নেই। সপ্তাহান্তে বাঁকুড়ায় প্র্যাকটিস করতে যেতাম। যা রোজগার হতো তাই দিয়ে সংসার চলত। তাই দিয়েই ভাই, বোনেদের বিয়ে হল। আসলে আমাদের সংসারে, পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে সুন্দর বন্ধন। কই, কোনও ভেদাভেদ দেখিনি। মনে শান্তি ছিল। অত কাজের চাপ ছিল। চাপ কমাতে কোনওদিন মদ খেতাম না, সিগারেট খেতাম না, পার্টি করতাম না। কোনও রেস্তোরাঁয় যেতাম না। মাঝেমধ্যে ফুটবল খেলতাম আর খেলা দেখতে খুব ভালোবাসতাম।
প্রথম গাড়ি কিনেছিলাম ১৯৭৭ সালে। অ্যাম্বাসেডর গাড়ি। ৩০ হাজার টাকায়। একজন সত্ ড্রাইভার পেলাম। ১০ টাকা ফি নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু হল ধর্মতলায়। পরে সেটা হল ১৬, তারপর ৩২, তারপর...।
না উল্কার গতিবেগে উন্নতি হয়নি। রাজনীতিতে কোনও দাদা, দিদিও ছিল না যে তাঁদের ধরে একটা কিছু করে নেব...তারপরেও কাজ করতে সমস্যা হয়নি। সারাজীবন কাজের প্রতি সত্ থেকেছি।
১৯৯৩ সালে পুরস্কার পেলাম আইসিএমআর-এর তরফে। তারপর ডব্লিউএইচও ফেলোশিপ পেয়ে গেলাম অস্ট্রেলিয়া। তখন এইডস নিয়ে সারা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ফিরে এসে মেডিক্যাল কলেজে শুরু হল এইডস ইউনিট। এমন অসংখ্য প্রাপ্তিতেই ভরে আছে পরবর্তী জীবন।
ভারতে চিকিত্সকদের নানা অ্যাসোসিয়েশন আছে। অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ানস অব ইন্ডিয়া, অ্যাসোসিয়েশন অব হাইপারটেনশন অব ইন্ডিয়া এমন বিখ্যাত পাঁচটি জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। অর্থাত্ জাতীয় স্তরে পরিচিতি বাড়ছিল। সুযোগ হয়েছিল মাদার টেরেসার চিকিত্সা করার! সরকারি তরফে এসেছে একাধিক পুরস্কার। নামকরা অভিনেতা, অভিনেত্রীদের চিকিত্সা করার সুযোগও ঘটেছে একাধিকবার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পেয়েছি ডক্টরেট। টেকনো ইন্ডিয়া দিল ডি লিট! ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, চীন, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ঘোরা হয়েছে। মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব থেকে পেয়েছি সম্মান। কত রাজনীতিবিদের চিকিত্সাও করতে হয়েছে।
জীবন মানে
আমার কাছে জীবনের অর্থ নিরলস কাজ, ছাত্র পড়ানো, পরিবার। পাঁচটা গাড়ি, চারটে বাড়ি করব ভাবিনি কখনও এরপরেও আমার সব ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে শেষে বাড়ি করেছি! বাড়ি করার পরে মা চলে গেলেন। আমার এখনও ভাইবোনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এই তো জীবন!
এখন সবাই যখন প্রশ্ন করে আমার দীর্ঘজীবনের কারণ কী! তবে আবার একটা জীবন পেলে আরও অনেক কাজ করব। আসলে সবই ঈশ্বরের কৃপা! ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ দেখেছি, দ্বারকা, বেনারস, রামেশ্বর, কেদারনাথ ঘুরেছি! আবার রামকৃষ্ণ মিশনের চারজন প্রেসিডেন্টের চিকিত্সা করার কথা বলার বিরল সৌভাগ্যও হয়েছে। শেষে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমত্ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির কাছে দীক্ষিত হয়েছি। রঙ্গনাথানন্দজি বলেছিলেন, সব কিছু কর, তবে নিজের অন্দরে চোখ মেলে দেখ। অর্থাত্ অন্দরে এমন কিছু একটা আছে যা আমাদের ভালো কাজ করতে উত্সাহ দেয়।
আমার তো আর কোনও নেশা নেই, কাজ করাই নেশা।
খাবার মানে নিয়ন্ত্রণ
খাবার দাবার নিয়ে সেভাবে কোনও আলাদা লোভ নেই। ছোট থেকেই পরিমিত খাই। আগে নিয়মিত আমিষ খেতাম। দীর্ঘদিন হল সপ্তাহে দু’দিন, বৃহস্পতি-শনি নিরামিষ খাই। না হলে বাকি দিনগুলো মাছ, ভাত, ডাল, তরকারিতেই সন্তুষ্ট। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ির বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খাওয়াচ্ছি তাও নয়। ফাস্টফুডও খাই না। ভাজাভুজির প্রতি কোনওদিনই সেভাবে আকর্ষণ ছিল না। বাড়িতে ফিশ ফ্রাই হলে খাই। বেগুন ভাজা খাই। কারণ আমার খাবার খাওয়ার সময় কোথায়? আগেও এই চিকিত্সা পেশায় থাকার কারণে দীর্ঘসময় না খেয়েই রোগী দেখতে হতো। বাঁকুড়া জেলায় রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত রোগী দেখতে হতো। খিদে পেলেও নিজেকে বোঝাতে হতো, পাক না খিদে, আর একটু পরেই খাব। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাটাও শেখা দরকার।
মোটামুটি তিনবেলা খাবার খাই। প্রাতঃরাশে কোনওদিন খাই চিঁড়ে-দই। কোনওদিন টোস্ট, ওমলেট। কোনও কোনওদিন কর্নফ্লেক্স। আর ফল খেতে ভালোবাসি। তাই পাঁচ রকম ফল খাই ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের মাঝে।
একটু দেরি হয় দুপুরের খাবার খেতে। আসলে আহ্নিক করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে যায়। দুপুরে খাই মাছ, ভাত, ডাল, তরকারি। শেষপাতে দই মাস্ট। ওঃ হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে চিকেন খাই। শাক খেতেও পছন্দ করি। পালং, পুঁই শাক খেতে ভালো লাগে। সজনেও ডাঁটাও খুব পছন্দের। অবশ্য লাঞ্চে পোস্ত আর কলাইয়ের ডাল হলে আর কিছু লাগে না। কখনও কখনও গরম ভাতে একটু ঘি খেতে ভালোবাসি!
লাঞ্চ আর ডিনারের মাঝখানে চা আর বিস্কুট খাই। কখনও সখনও নিরামিষ পকোড়াও খাই। রাত্রিবেলা ডিনার করতে বেশ দেরি হয়ে যায়। মানে মাঝরাতও হয়ে যায় কখনওসখনও। পড়াশোনা করতে হয় তো এখনও। জার্নাল পড়ি। সেসব কাজ করতে করতে রাত তিনটে চারটে বেজে যায়। তখন একটু ভাত বা রুটি, তরকারি, সব্জি। রাতে নিরামিষ খাই।
মিষ্টি : রসগোল্লা খেতে ভালো লাগে। আম খেতে খুব ভালো লাগে। আমার ডায়াবেটিস নেই। তাই খেলে সমস্যাও নেই।
খাদ্যস্মৃতি : আগে বাবা রবিবার হলেই জিলিপি আনত। জিলিপি খুব ভালো লাগত। আর খেতাম মরশুমে ইলিশ মাছ।
অনিয়ম : নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেলে বা বাইরে বেড়াতে গেলে একটু অনিয়ম হয় বটে। একটু পোলাও, মশলাদার খাওয়া হয়। তবে তাও খাই পরিমিত মাত্রায়।
বদভ্যাস : আমি কলকাতার একাধিক প্রেস্টিজিয়াস ক্লাবের মেম্বার। অথচ কোনওদিন সেখানে ড্রিংকস করতে যাইনি। ধূমপানও করি না। একবার আমার একসময়ের বন্ধু ডাঃ জয়ন্ত সেন (সেও আমার সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকে এফআরসিএস করেছিল) আর কয়েকজন মিলে শখ করে বেশ কয়েকটা দামি সিগারেট কিনে খেয়েছিলাম। সেই প্রথম। আমার খুব একটা ভালো লাগেনি সিগারেট খেতে। সেই শেষ।
অবসরের শখ
স্বামী রঙ্গনাথনজির বই পড়ি। ভালোবাসি মেডিক্যাল জার্নাল পড়তে। আহ্নিক করি একটু বেশি সময় নিয়ে। এই তো জীবন। এই জীবনই ভালো লাগে।
বাবা ইস্টার্ন রেলওয়ে ওয়ার্কস ম্যানেজার ছিলেন। তখনকার দিনে কতই বা আর বেতন ছিল! তবে আমাদের উপর বাবার শাসন ছিল যথেষ্ট। মা উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। তবে ছিলেন চরম কর্তব্যপরায়ণ।
আমরা তিন ভাই, চার বোন। আমার এক ভাই গত হয়েছে। আজকাল অতীতের দিকে তাকালে নজর চলে যায় ফসল ভরা মাঝের আলে। ধানমাঠের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি পাঠশালার দিকে। ভোলা মাস্টার অঙ্ক করাতেন। অঙ্ক না পারলে বেতের আঘাত না হলে নীলডাউন!
বাড়িতে সামান্য চায হতো। তাই গোরুর গাড়িও ছিল। তাই বলে সবসময় গোরুর গাড়ি মিলত না। তাই সুরুল গ্রাম থেকে মাঠ পেরিয়ে লাল মাটির রাস্তা ধরতাম খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাই বোনেরা। আমাদের সেই পথ থামত বোলপুর স্কুলে। ভাইয়েরা খুব সাহসী ছিল। মাঝেমধ্যেই খেলাচ্ছলে আমবাগানে চলে যেত আম চুরি করতে। আমার শৌর্যবীর্যের অভাব ছিল! আম চুরির কথা উঠলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যেতাম। একটু মুখচোরাও ছিলাম। তারপর কলকাতা গেলাম। থাকতে পারিনি বেশিদিন। শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ফিরে এক বছরের জন্য বঙ্গবাসী স্কুলে পড়াশোনা করলাম। তারপর গোটাটাই হিন্দু স্কুলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। অসম্ভব শৃঙ্খলাপরায়ণ, রাশভারী...। ১৯৫২ সালে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলাম স্কুল ফাইনাল।
সেই সময় নিজেকেই কলেজ স্থির করতে হতো। কোন কলেজে পড়লে ভালো হয়, কার কাছে খোঁজ করতে গেলে ভালো হয় কিছু জানতাম না। শুধু বাবার উত্সাহ আর মায়ের আশীর্বাদ ছিল। নিজেই ঘুরেছি কলেজে কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজেও সুযোগ পেয়েছিলাম, সেন্ট জেভিয়ার্সেও পড়ার সুযোগ ঘটেছিল। এত বোকা ছিলাম, সেন্ট জেভিয়ার্সে ইন্টারভিউ দেওয়ার পর বলেছিলাম— প্রেসিডেন্সিতেও অ্যাপ্লাই করেছি। কাল ইন্টারভিউ-এ কী হয় দেখি, দিয়ে এখানে আসব!
সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে সম্ভবত নাম কাটা পড়ল, আর প্রেসিডেন্সিতে সুযোগ পেলাম না। শেষে সেন্ট পলস কলেজে পড়লাম আইএসসি।
আজকালকার ছেলেমেয়েরা যতখানি চৌকস, সজাগ ততখানি ছিলাম না। ১৯৫৪ সালে সেন্ট পলস কলেজে আইএসসিতে প্রথম বিভাগে পাশ করলাম। আমার ইচ্ছা ছিল ইঞ্জিনিয়ার হব। শিবপুরে পরীক্ষাও দিলাম। আর ইন্টারভিউ দিলাম কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে। আমাদের বাড়িতে কোনও ডাক্তার ছিল না। মামা, মেসোমশাই, কাকা সকলেই ইঞ্জিনিয়ার। তাই শেষে ঠিক হল মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হব।
সেই ১৯৫৪ সাল থেকেই আমার ডাক্তারির যাত্রা শুরু। দেখলাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি, সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে লেখাপড়ায় তুখোড় ছেলেমেয়েরা এসেছে। জোর প্রতিযোগিতা। আমি তখন সবে ফুলপ্যান্ট পরতে শিখেছি সময় এগতে থাকল। দেখলাম ২ বছর পড়াশোনা করে ফার্স্ট হয়ে গিয়েছি! বহু লোকের নেক নজরে পড়ে গেলাম। আরও তিনবছর পরে দিলাম ফাইনাল এমবিবিএস। তাতেও প্রথম। শুনলাম ইউনিভার্সিটিতেও প্রথম হয়েছি! তবে পড়াশোনাটা হতো না। হল কারণ শেষ তিন বছর প্রতি মাসে মাসে ২৫ টাকা করে স্কলারশিপ পেয়েছি। আর কলেজের মাইনে মকুব হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় অনেকগুলো স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। না হলে কীভাবে পড়াশোনা করা হতো জানি না। মাকে কয়লাও ভাঙতে হয়েছে একসময়, কাচতে হয়েছে কাপড়!
এত সমস্যার মধ্যেও পাড়ায় মাঝেমধ্যে ফুটবল খেলতাম। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কোনও কোনও সময় যেতাম গড়ের মাঠ। কিন্তু কখনও পড়াশোনায় ফাঁকি দিতাম না। তার প্রধান কারণ ছিল বাবা-মা। ওরা সবসময় আমার লেখাপড়ার দিকে রাখতেন কড়া নজর। আর একজন ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। তিনি আমার মামা। বড় মাপের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আর যখনই বাড়ি আসতেন, অন্যান্যদের উদাহরণ টেনে বলতেন— দেখ কেমনভাবে সাফল্য পেয়েছে! কীভাবে পড়াশোনা করলে লাভ হবে!
শিক্ষকদের সান্নিধ্য
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হাউজস্টাফ শিপ করছিলাম। সেখানেই পেলাম ডাঃ শৈলেন সেনের মতো শিক্ষক। তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।
তাঁর কাছে শিখেছি দায়িত্ব নেওয়া, মানুষের সঙ্গে কথা বলার ধরন ইত্যাদি। তার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জি। তাঁর কাছ থেকে শিখেছি বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতা। পাশ করার পরে মনে জাগল এমডি পাশ করার ইচ্ছা। তখনকার দিনে এমডি পাশ করতে হলে অনেকখানি অর্থ লাগে। ডাঃ শৈলেন সেন বাড়তি কাজের ব্যবস্থা করে সেই অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিলেন। সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলাম ১৯৬২ সালে। পাশও করলাম। আমার তখন ইচ্ছা হল বিদেশে পড়তে যাব। অনেক টাকা লাগে। কী করে পাব। তখনকার দিনে দেওয়া হতো মাত্র ৩ পাউন্ড। সরকারি তরফে ৩ বছরের জন্য ছুটি মঞ্জুর হল। এডিনবরা আর লন্ডনে করলাম এমআরসিপি। বিদেশে থাকাকালীনই বাবা মারা গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে মেডিক্যাল কলেজে জয়েন করতেই বলা হল সোজা বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে চলে যেতে।
১৯৭০ সাল। একটা ব্যাগে রোজকার ব্যবহার্য স্বল্প কিছু সরঞ্জাম নিয়ে তীব্র গরমে ঢুকলাম বাঁকুড়া। অথচ তখন আমার হাতে ইংল্যান্ড, আমেরিকার চাকরি। মা বলল, এতগুলো ভাইবোনকে কে দেখবে? দেশ ছেড়ে যাওয়া যাবে না। মায়ের কথা অবহেলা করব কীভাবে!
গরম ছাড়াও বাঁকুড়ার আরও একটা বিশেষত্ব ছিল রাতে লোডশেডিং। তার মধ্যেই শুরু হল কাজ। অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকবে হয় তো! সেই যে বাঁকুড়া ঢুকলাম। পরবর্তী ৬ বছর কেটেছিল বাঁকুড়ায়। তখন রোগী দেখছি, ছাত্র পড়াচ্ছি ছয় মাসে একবার হয়তো কলকাতা যাচ্ছি। তার মধ্যেও পরিবারের দায়িত্ব পালন করছি ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। একদিন বউবাজারের বাড়িতে ফিরতে মা বলল এবার বিয়েটা সারতে হবে। না হলে নাকি অনেক বাধা আছে। মায়ের বিশ্বাস, কী আর বলি। সম্মতি দিলাম।
রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। তাঁরা বাড়ি দেখতে এলেন! দেখেই বললেন এখানে কী করে থাকবেন! আমি রেলের একটা গোটা কামরা বুক করে সবাইকে নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে বিয়ে দেব। জামা আদান প্রদান হল। অথচ কী আশ্চর্য নানা কারণে ওরা বিয়েটা শুধু পিছিয়ে যেতে লাগল। আসলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের বারং বার নানা কারণে ঝামেলা বাঁধত। তাতেই বিয়ের তারিখ নিয়ে বেশ কয়েকবার এমন হওয়ার পর মা বাধ্য হয়ে মা সম্বন্ধটা ভাঙতে বাধ্য হলেন।
বউবাজারের শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক অত্যন্ত সত্ শিক্ষকের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হল। সাতদিনের নোটিসে আমি বাঁকুড়া থেকে এসে বিয়ে করলাম। তখন নকশাল আন্দোলন। গাড়ি ছিল না। ট্যাক্সি ভাড়া করে বিয়ে করতে গেলাম। সেই গাড়ি পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল পুলিস।
শ্বশুরমশাই ছিলেন ট্রিপল এম এ। আইন পাশও করেছিলেন। শুধু অসত্ হতে পারবেন না বলে ল প্র্যাকটিস করেননি। বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করতেন। শাশুড়ি ছিলেন এম এ পাশ। মধ্যবিত্ত অথচ শিক্ষিত ওই পরিবারে আমার বিয়ে হয়ে গেল।
কয়েকদিন পরে বাঁকুড়া ঢুকলাম সস্ত্রীক। একটা বাড়িতে থাকতাম। স্বাচ্ছন্দ্যের বালাই নেই। বিশ্রামের আরামদায়ক জায়গা নেই! মাত্র হাজার দু’য়েক টাকা বেতন পাই! সেই অর্থ থেকেই সব কিছু চলে। টাকা বাঁচিয়ে ষাট টাকায় একটা খাট কেনা হল!
ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস বাড়তে থাকল। বাড়ছিল হাসপাতালের চাপও! অসুস্থ হওয়ারও যেন সময় নেই। ৬ বছর কেটে গেল। ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, সবই হচ্ছে শুধু শিক্ষাগত উত্কর্ষের জায়গায় বড় বেশি ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে! বিষয়টা ক্রমাগত সুচের মতো মস্তিষ্কে বিঁধছিল।
সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন অজিত পাঁজা। তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করলাম। জানালাম গত ছয় বছরে বাড়তি ছুটি নিইনি, কাজ করেছি, রোগী দেখেছি। শুধু শিক্ষাগত ক্ষেত্রের জায়গাটা পূরণ হচ্ছে না। এবার যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়।
সাতদিনের মধ্যে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক হিসেবে বদলি হয়ে গেলাম। সেটা ১৯৭৬ সাল। তখন কলকাতায় প্র্যাকটিস নেই। সপ্তাহান্তে বাঁকুড়ায় প্র্যাকটিস করতে যেতাম। যা রোজগার হতো তাই দিয়ে সংসার চলত। তাই দিয়েই ভাই, বোনেদের বিয়ে হল। আসলে আমাদের সংসারে, পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে সুন্দর বন্ধন। কই, কোনও ভেদাভেদ দেখিনি। মনে শান্তি ছিল। অত কাজের চাপ ছিল। চাপ কমাতে কোনওদিন মদ খেতাম না, সিগারেট খেতাম না, পার্টি করতাম না। কোনও রেস্তোরাঁয় যেতাম না। মাঝেমধ্যে ফুটবল খেলতাম আর খেলা দেখতে খুব ভালোবাসতাম।
প্রথম গাড়ি কিনেছিলাম ১৯৭৭ সালে। অ্যাম্বাসেডর গাড়ি। ৩০ হাজার টাকায়। একজন সত্ ড্রাইভার পেলাম। ১০ টাকা ফি নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু হল ধর্মতলায়। পরে সেটা হল ১৬, তারপর ৩২, তারপর...।
না উল্কার গতিবেগে উন্নতি হয়নি। রাজনীতিতে কোনও দাদা, দিদিও ছিল না যে তাঁদের ধরে একটা কিছু করে নেব...তারপরেও কাজ করতে সমস্যা হয়নি। সারাজীবন কাজের প্রতি সত্ থেকেছি।
১৯৯৩ সালে পুরস্কার পেলাম আইসিএমআর-এর তরফে। তারপর ডব্লিউএইচও ফেলোশিপ পেয়ে গেলাম অস্ট্রেলিয়া। তখন এইডস নিয়ে সারা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ফিরে এসে মেডিক্যাল কলেজে শুরু হল এইডস ইউনিট। এমন অসংখ্য প্রাপ্তিতেই ভরে আছে পরবর্তী জীবন।
ভারতে চিকিত্সকদের নানা অ্যাসোসিয়েশন আছে। অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ানস অব ইন্ডিয়া, অ্যাসোসিয়েশন অব হাইপারটেনশন অব ইন্ডিয়া এমন বিখ্যাত পাঁচটি জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। অর্থাত্ জাতীয় স্তরে পরিচিতি বাড়ছিল। সুযোগ হয়েছিল মাদার টেরেসার চিকিত্সা করার! সরকারি তরফে এসেছে একাধিক পুরস্কার। নামকরা অভিনেতা, অভিনেত্রীদের চিকিত্সা করার সুযোগও ঘটেছে একাধিকবার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পেয়েছি ডক্টরেট। টেকনো ইন্ডিয়া দিল ডি লিট! ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, চীন, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ঘোরা হয়েছে। মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব থেকে পেয়েছি সম্মান। কত রাজনীতিবিদের চিকিত্সাও করতে হয়েছে।
জীবন মানে
আমার কাছে জীবনের অর্থ নিরলস কাজ, ছাত্র পড়ানো, পরিবার। পাঁচটা গাড়ি, চারটে বাড়ি করব ভাবিনি কখনও এরপরেও আমার সব ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে শেষে বাড়ি করেছি! বাড়ি করার পরে মা চলে গেলেন। আমার এখনও ভাইবোনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এই তো জীবন!
এখন সবাই যখন প্রশ্ন করে আমার দীর্ঘজীবনের কারণ কী! তবে আবার একটা জীবন পেলে আরও অনেক কাজ করব। আসলে সবই ঈশ্বরের কৃপা! ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ দেখেছি, দ্বারকা, বেনারস, রামেশ্বর, কেদারনাথ ঘুরেছি! আবার রামকৃষ্ণ মিশনের চারজন প্রেসিডেন্টের চিকিত্সা করার কথা বলার বিরল সৌভাগ্যও হয়েছে। শেষে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমত্ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির কাছে দীক্ষিত হয়েছি। রঙ্গনাথানন্দজি বলেছিলেন, সব কিছু কর, তবে নিজের অন্দরে চোখ মেলে দেখ। অর্থাত্ অন্দরে এমন কিছু একটা আছে যা আমাদের ভালো কাজ করতে উত্সাহ দেয়।
আমার তো আর কোনও নেশা নেই, কাজ করাই নেশা।
খাবার মানে নিয়ন্ত্রণ
খাবার দাবার নিয়ে সেভাবে কোনও আলাদা লোভ নেই। ছোট থেকেই পরিমিত খাই। আগে নিয়মিত আমিষ খেতাম। দীর্ঘদিন হল সপ্তাহে দু’দিন, বৃহস্পতি-শনি নিরামিষ খাই। না হলে বাকি দিনগুলো মাছ, ভাত, ডাল, তরকারিতেই সন্তুষ্ট। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ির বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খাওয়াচ্ছি তাও নয়। ফাস্টফুডও খাই না। ভাজাভুজির প্রতি কোনওদিনই সেভাবে আকর্ষণ ছিল না। বাড়িতে ফিশ ফ্রাই হলে খাই। বেগুন ভাজা খাই। কারণ আমার খাবার খাওয়ার সময় কোথায়? আগেও এই চিকিত্সা পেশায় থাকার কারণে দীর্ঘসময় না খেয়েই রোগী দেখতে হতো। বাঁকুড়া জেলায় রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত রোগী দেখতে হতো। খিদে পেলেও নিজেকে বোঝাতে হতো, পাক না খিদে, আর একটু পরেই খাব। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাটাও শেখা দরকার।
মোটামুটি তিনবেলা খাবার খাই। প্রাতঃরাশে কোনওদিন খাই চিঁড়ে-দই। কোনওদিন টোস্ট, ওমলেট। কোনও কোনওদিন কর্নফ্লেক্স। আর ফল খেতে ভালোবাসি। তাই পাঁচ রকম ফল খাই ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের মাঝে।
একটু দেরি হয় দুপুরের খাবার খেতে। আসলে আহ্নিক করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে যায়। দুপুরে খাই মাছ, ভাত, ডাল, তরকারি। শেষপাতে দই মাস্ট। ওঃ হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে চিকেন খাই। শাক খেতেও পছন্দ করি। পালং, পুঁই শাক খেতে ভালো লাগে। সজনেও ডাঁটাও খুব পছন্দের। অবশ্য লাঞ্চে পোস্ত আর কলাইয়ের ডাল হলে আর কিছু লাগে না। কখনও কখনও গরম ভাতে একটু ঘি খেতে ভালোবাসি!
লাঞ্চ আর ডিনারের মাঝখানে চা আর বিস্কুট খাই। কখনও সখনও নিরামিষ পকোড়াও খাই। রাত্রিবেলা ডিনার করতে বেশ দেরি হয়ে যায়। মানে মাঝরাতও হয়ে যায় কখনওসখনও। পড়াশোনা করতে হয় তো এখনও। জার্নাল পড়ি। সেসব কাজ করতে করতে রাত তিনটে চারটে বেজে যায়। তখন একটু ভাত বা রুটি, তরকারি, সব্জি। রাতে নিরামিষ খাই।
মিষ্টি : রসগোল্লা খেতে ভালো লাগে। আম খেতে খুব ভালো লাগে। আমার ডায়াবেটিস নেই। তাই খেলে সমস্যাও নেই।
খাদ্যস্মৃতি : আগে বাবা রবিবার হলেই জিলিপি আনত। জিলিপি খুব ভালো লাগত। আর খেতাম মরশুমে ইলিশ মাছ।
অনিয়ম : নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেলে বা বাইরে বেড়াতে গেলে একটু অনিয়ম হয় বটে। একটু পোলাও, মশলাদার খাওয়া হয়। তবে তাও খাই পরিমিত মাত্রায়।
বদভ্যাস : আমি কলকাতার একাধিক প্রেস্টিজিয়াস ক্লাবের মেম্বার। অথচ কোনওদিন সেখানে ড্রিংকস করতে যাইনি। ধূমপানও করি না। একবার আমার একসময়ের বন্ধু ডাঃ জয়ন্ত সেন (সেও আমার সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকে এফআরসিএস করেছিল) আর কয়েকজন মিলে শখ করে বেশ কয়েকটা দামি সিগারেট কিনে খেয়েছিলাম। সেই প্রথম। আমার খুব একটা ভালো লাগেনি সিগারেট খেতে। সেই শেষ।
অবসরের শখ
স্বামী রঙ্গনাথনজির বই পড়ি। ভালোবাসি মেডিক্যাল জার্নাল পড়তে। আহ্নিক করি একটু বেশি সময় নিয়ে। এই তো জীবন। এই জীবনই ভালো লাগে।
অনুলিখন: সুপ্রিয় নায়েক
এখনকার দর
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৪.৯৬ টাকা | ৮৬.৭০ টাকা |
| পাউন্ড | ১০৪.৫৩ টাকা | ১০৮.২৪ টাকা |
| ইউরো | ৮৬.৫১ টাকা | ৮৯.৮৫ টাকা |
*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে