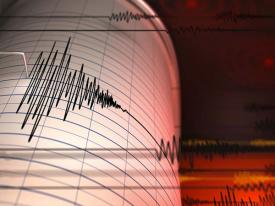কলকাতা, শনিবার ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, ৬ পৌষ ১৪৩১
কৈলাসের জ্ঞানগঞ্জে যোগীরা কীভাবে পৌঁছন?

কৈলাসের আশপাশে আছে জ্ঞানগঞ্জ। সেখানে সিদ্ধযোগীরাই কেবল যেতে পারেন। জ্ঞানগঞ্জ ঠিক কোথায়? সেই কৌতূহলোদ্দীপক কথা লিখেছেন সোমব্রত সরকার।
দেশ, কাল ও নিমিত্তে আটকে গেছে গোটা পৃথিবীর সমস্ত জিনিস। যা কিছু এখানে আছে, সবেরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা রয়েছে, যা তৃতীয় মাত্রা... থ্রি ডাইমেনশন নির্দেশ করে। মানুষ যখন স্থানহীনতা... শূন্যতা প্রভাবিত কোনও একটি এলাকার মধ্যে ঢুকে যায়, সে রহস্যময় এক নতুন বাতাবরণে প্রবেশ করে। তার মনের, প্রাণের শক্তি সেখানে আশাতীতভাবে বেড়ে যায়। কালের প্রভাব সেখানে এতই নগণ্য যে শরীরের ওপর তা একেবারে পড়ে না। বায়ু-শূন্যতা আর ভূ-শূন্যতায় সম্পৃক্ত জায়গাগুলোকে বলা হচ্ছে চতুর্থ আয়াম... ফোর্থ ডাইমেনশন। এখানে পৌঁছে গেলে তার সত্তা অদৃশ্য, লুপ্ত হয়ে যায়। অস্তিত্ব যেমন ছিল তেমনই থাকে। যদি কোনও মানুষ পঁচিশ বছর বয়সে চতুর্থ আয়াম প্রভাবিত ক্ষেত্রে চলে যায়, তাহলে তার শরীর বহু বছর ধরে ওই পঁচিশ বছর বয়সের যুবকের মতো হয়ে থাকবে, বয়সের কোনও ছাপ পড়বে না। চতুর্থ আয়াম প্রভাবিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত যোগীরা থাকেন, পাঁচশো-ছশো বছর বেঁচে থাকা তাঁদের পক্ষে কোনও সমস্যাই নয়। তাঁদের শরীর একরকম থেকে যায়, যদিও বয়স বাড়তে থাকে কালের নিয়মে। কালের প্রভাব শরীরে গিয়ে পড়ে না। চতুর্থ আয়াম থেকে যোগীরা যখন থ্রি ডাইমেনশনে বাঁধা এ সংসারে প্রবেশ করেন, শরীরের ওপর প্রভাব পড়তে থাকে, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। একটা সময় পর যোগীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।
যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী চতুর্থ আয়ামে অবস্থানরত এমনই এক যোগীপুরুষের কথা তাঁর শিষ্যবৃত্তে জানিয়েছেন, যিনি চক্রাকার আলোকপুঞ্জের মতো ঘুরে ঘুরে আকাশপথ দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পৃথিবীর যে কোনও স্থানে অবতরণ করতে পারেন। পৃথিবী বিখ্যাত যোগী পরমহংস যোগানন্দ তাঁর আত্মজীবনী ‘Autobiography of a Yogi’ বইটিতে চতুর্থ আয়ামে অবস্থানরত মহাবতার বাবাজির অস্তিত্বের বিষয় সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। যোগানন্দজির সংস্কৃতের শিক্ষক স্বামী কেবলানন্দ কিছুদিন বাবাজি মহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে কাটিয়েছিলেন। তিনি পরমহংস যোগানন্দকে জানিয়েছেন, ‘মহাগুরু হিমালয়ে তাঁর দলবল নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ইচ্ছা করলে তবেই কেউ তাঁকে দেখতে বা চিনতে পারে, তা না হলে নয়। তিনি ঈষৎ পরিবর্তিত বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে তাঁর নানা শিষ্যদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন। তাঁর পঁচিশ বছরের যুবক চেহারার মুখে কোনও সময় হালকা দাড়ি-গোঁফ থাকত, কখনও একেবারে পরিষ্কার ঝকঝকে মুখমণ্ডল। তাঁর অক্ষয়দেহের কোনও প্রকার আহারের প্রয়োজন হতো না। শিষ্যদেরকে দেখা দেওয়ার সময় লৌকিকতা হিসেবে তিনি তাঁদের হাতে ফল, পায়েস, ঘি, ভাত ধরিয়ে দিয়ে ফের অদৃশ্য হয়ে যেতেন।’
রণবাজপুরের যোগী রামগোপাল মজুমদার যোগানন্দজিকে জানিয়েছেন, ‘কখনও কখনও আমি নির্জন গুহা ছেড়ে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গিয়ে থাকতাম। একদিন গভীর রাতে গুরুদেবের ঘরে ধ্যানে বসেছি, তিনি আমাকে অদ্ভুত আদেশ দিলেন, রামগোপাল, এক্ষুনি তুমি দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে যাও।’
ঘাটে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে আছি। উজ্জ্বল নক্ষত্র আর চন্দ্রালোকে রাত হাসছে। হঠাৎ পায়ের কাছেই একটা প্রকাণ্ড পাথর উপরে উঠতে লাগল, খুলে গেল গুহা। সেখান থেকে একজন অপরূপ সুন্দরী যোগীনী বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, আমি মাতাজি, বাবাজি মহারাজের বোন। আমি তাঁকে আর লাহিড়ী মহাশয়কেও আজ রাত্রে আমার এই গুহায় আসতে বলেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবার জন্যে।
মাতাজির বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে দুটি জ্যোতি নেমে এল। দুটিই রূপ নিল মানুষের মূর্তিতে। একটা মূর্তি গুরুদেবের আর একটা অল্পবয়স্ক, উজ্জ্বল চেহারার ও সুদীর্ঘ চুলধারী তরুণের।
গুরুদেব, মাতাজি ও আমি বাবাজিকে প্রণাম করার পর তিনি বললেন, দেহ ছেড়ে দেওয়ার কথাটি।
‘বললেন, পরব্রহ্মসাগরে আত্মার তরঙ্গ দৃশ্যই হোক আর অদৃশ্যই হোক... প্রভেদ কিছু নেই।’
মাতাজি বললেন, ‘যদি কোনও পার্থক্য না থাকে গুরুদেব, তবে দয়া করে আপনি আর দেহত্যাগ করবেন না।’
মহাবতার বাবাজি বললেন, ‘তবে তাই হোক। আমি কখনও আমার এ জড়দেহ আর পরিত্যাগ করব না। এই দেহ পৃথিবীতে, অন্তত জনকতকের কাছে সর্বদাই দৃশ্য হয়ে থাকবে।’
১৮৯৫ সালে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন সাতষট্টি বছর বয়সে। ১৯৫২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ অ্যাঞ্জেলসে দেহ রাখেন পরমহংস যোগানন্দজি। তিনি বাবাজি মহারাজের যে সূক্ষ্ম শরীর দর্শন করেছিলেন তার একটা স্কেচ করিয়ে রাখেন। এটিই মহাবতার বাবাজি মহারাজের একমাত্র ছবি।
পুরাণপুঁথির ভেতর সাংগ্রিলা ঘাটির উল্লেখ পাই আমরা। ভারতীয় ঋষিরা বলছেন, ‘স্বর্গীয় বাতাবরণে ডুবে থাকা এই ঘাটিটি জ্যোতির আভায় পূর্ণ। এখানে গুপ্তভাবে অনেক যোগাশ্রম, সিদ্ধাশ্রম, তান্ত্রিক মঠ আছে। সেইসব মঠ ও আশ্রমে আছেন কালজয়ী সাধক আর যোগী-যোগীনীরা। এঁরা সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করেন, উপযুক্ত শিষ্যদের দর্শনও দেন।’
সাংগ্রীলার কোনও সিদ্ধাশ্রমে আজও বাস করেন মহাবতার বাবাজি। অনেকে বলেন উন্নত সাধকদের সাধনে সাহায্য করার জন্য তিনি আমাদের থ্রি ডাইমেনশনের পৃথিবীতে নেমে আসেন চতুর্থ আয়াম থেকেই।
হাড়িয়াখণ্ড কথার মানে পবিত্র জায়গা। নেপাল ও তিব্বতের মাঝে খুব প্রাচীন এক জায়গা হল হাড়িয়াখণ্ড। মানস সরোবর থেকে বেরিয়ে কৈলাস গঙ্গা, গৌতম গঙ্গা ও গোলা নামে তিনটি ক্ষীণধারার নদী পার হয়ে কয়েক ঘণ্টা হেঁটে গেলে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি গুহা রয়েছে। ওখানে এক যোগীপুরুষের বাস ছিল। হাড়িয়াখণ্ডের যোগী লোকমুখে হৈড়াখান বাবা বলেই পরিচিত ছিলেন। পরিষ্কার সাদা কাপড় পড়তেন তিনি। সৌম্যমূর্তি ও সুন্দর চেহারা তাঁর। দেখলে মনে হতো বাবার বয়স তিরিশের বেশি নয়। কিন্তু ওই অঞ্চলের পুরনো মানুষেরা বলতেন, ‘আমাদের ঠাকুরদাদারা পর্যন্ত বাবাকে দেখেছেন। তাঁরা কোন কালে চলে গিয়েছেন! আমাদের সময় হয়ে এল। শরীরে জরা ধরে গেছে। বাবার চেহারায় এখনও নবযৌবন রয়েছে।’
বলা হয় হৈড়াখান বাবাও ছিলেন চতুর্থ আয়ামের মানুষ। কৈলাস পর্বতে হৈড়াখান বাবার অনেক লীলাকাহিনি প্রচলিত আছে। বারো-তেরো বছর বয়সে হঠাৎ করে তাঁকে এ অঞ্চলে দেখা গেল। তিনি তখন জ্যোতির্ময় বালক। বালকের সঙ্গে ঘোরে হিংস্র দুটি কুকুর কালী আর লালি। এই বালকই কিশোর থেকে যুবক হলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি যখন দেহ রাখলেন, তাঁর চেহারায় ছড়িয়ে ছিল ত্রিশ বছরের যুবকের যৌবন।
কলকাতার বাসিন্দা শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাইয়ের শিষ্য দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য ১৯৭৯ সালে যখন গিয়েছেন হৈড়াখান বাবার সঙ্গে দেখা করতে, হাড়িয়াখণ্ডে আশ্রম গড়ে উঠেছে। ১০৮টি সিঁড়ি বেয়ে বাবার গুহায় পৌঁছতে হয়। ‘সহজ ক্রিয়াযোগ ও যোগ ঐশ্বর্য’ গ্রন্থে দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য লিখছেন, ‘ভক্তদের চোখে বাবা দেবতাস্বরূপ। কায়াকল্প ধরে সৃষ্টির আদি হতে তিনি আছেন। হৈড়াখান বাবা যুগযুগান্তরের কথা বলতে পারেন। মাঝে মাঝে তিনি সমবেত ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলেন, উপস্থিত এখানে জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত কেউ আছ কি না। অনেক বিদেশি ভক্তকে দেখে তিনি তাঁদের নামধাম ইত্যাদি বলে বলেন, তোমরা আমার পূর্বজন্মের পরিচিত।’
একবিংশ শতকের অন্যতম মহান সাধক স্বামী রামার জন্ম হিমালয়ের কোলে। খুব ছোটবেলা থেকে তিনি হিমালয়ে বসবাসকারী যোগী... বাঙ্গালি বাবার সাহচর্য লাভ করেন। গুরুর নির্দেশে তিনি সুদূর পাঞ্জাব হিমালয় থেকে কুমায়ুন এবং গাড়োয়াল হিমালয়, আবার নেপাল থেকে অসম এবং সিকিম থেকে ভুটান এবং তিব্বত অঞ্চলে সুবিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালার দুর্গম খাঁজে খাঁজে যোগীদের কুঠিয়ায় কাটান। যুবকালে তিনি অনেক সময় কৈলাস পর্বতের পদতলে বসে মানস সরোবরের জল পান করতেন। কেদারনাথ এবং গঙ্গোত্রীতে প্রায় তিনি প্রকৃতি-মায়ের কোলে জন্মানো শাক-সব্জি-মূল রান্না করে খেতেন আর থাকতেন হিমালয়ের গুহায়-গুহায় যোগীদের সান্নিধ্যে।
স্বামী রামা গুরুদেবের কাছে শুনেছিলেন যে, হৈড়াখান বাবা এবং হিমালয়ের অন্য কয়েকজন যোগী অনেক বছর তাঁর সঙ্গে শিক্ষা নিয়েছিলেন। কুমায়ুন হিমালয়ে হৈড়াখান বাবা বেশ বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তাঁকে সকলে হিমালয়ের শাশ্বত বাবাজি বলেই মান্য করত। হৈড়াখান বাবা মহাগুরুদেবের কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন। স্বামী রামা গুরুদেবের কথামতো দুর্গম এবং ক্লান্তিকর যাত্রা করে হৈড়াখান বাবার গুহায় পৌঁছেছিলেন।
‘Living with the Himalayan Masters’ গ্রন্থে স্বামী রামা লিখছেন তিব্বতের এক গুম্ফায় তিনি মহাগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, ‘আমার মহাগুরু ছোটকাল থেকে হিমালয়ের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরাও সাধু ছিলেন। তিনি অবয়বানুযায়ী অতি বৃদ্ধ কিন্তু স্বাস্থ্যবান দেখতে ছিলেন। খুব ভোরে এবং সন্ধ্যাবেলা মাত্র দু’বার তিনি আসন ছেড়ে উঠতেন। তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুট নয় বা দশ ইঞ্চি, খুবই শীর্ণকায়, অথচ প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর ঝোপের মতো ভ্রু-যুগল, সদা অত্যুজ্জ্বল মুখমণ্ডল থেকে কী গভীর এক প্রশান্তি বিচ্ছুরিত হতো! সদা হাস্যমুখে অধিকাংশ সময়ে চমরীগাইয়ের দুধ সেবন করে এবং কখনও বা যবের সুরুয়া খেয়ে সানন্দে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। কোনও সময়ে কয়েকজন লামা এসে তাঁর কাছে কিছুদিন অধ্যয়ন করে যেতেন। পাহাড়ের সাত হাজার ফুট উচ্চতায় একটি প্রাকৃতিক গুহায় তিনি বাস করতেন। স্যাঁতস্যাতে ভাব কাটাতে এবং জল ও দুধ গরম করতে কখনও-সখনও গুহার ভিতরে তিনি আগুন জ্বালতেন। তাঁর ছাত্রেরা গুহার মুখে একটি বারান্দা মতো তৈরি করে দিয়েছিল। এখানে বসেই তিনি আমাকে পরকায়া প্রবেশ শিখিয়েছিলেন। গুহার মধ্যে বসা অবস্থাতে মহাগুরুর শরীর আবছা হতে শুরু করল। রক্তমাংসের দেহটি হয়ে গেল এক টুকরো মেঘ। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। অদৃশ্য তিনি। কিছু পর ধীরে ধীরে তিনি নিজের শরীরের অবয়ব ধারণ করে আমাদের সামনে দৃশ্যমান হলেন।’
চতুর্থ আয়ামে অবস্থানরত সময়ে চোখের সামনে দেখা কায়াকল্প সাধুর কাহিনি রাম ঠাকুর তাঁর শিষ্য রোহিণীকুমার মজুমদার ও কাশীতে অবস্থানকালে জ্ঞানগঞ্জের সাধক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্য প্রখ্যাত পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মশাইকে বিস্তারিত বলে গিয়েছেন। হিমালয়ের শিখর অভিমুখে চলেছেন গুরু অনঙ্গদেবের সঙ্গে রাম ঠাকুর। পর্বতের শেষ চূড়ায় বশিষ্ঠাশ্রমে গুরুর সঙ্গে দুটো দিন থাকার পর যুবক রাম চলেছেন পূর্বদিকের দুর্গম সিদ্ধপীঠে। বরফ ঢাকা পথের চারদিকে চারটি স্ফটিক স্তম্ভ। মাঝখানে তুষারশুভ্র শিবলিঙ্গ। জটাজূটধারী ভৈরবী মা ধ্যানস্থা হয়ে রয়েছেন। তিনি অনঙ্গদেবের কথাতে তপঃসিদ্ধ দিব্যদেহ থেকে জ্যোতি বের করতে করতে তাঁদেরকে নিয়ে চললেন প্রাচীন গুহায়। গুহার সামনে ধুনি জ্বলছে। সেখানে বসে অতি বৃদ্ধ মহাত্মা সাধনা করে চলেছেন। গুরুদেব তাঁকে বললেন, ‘রাম, মহাত্মন দেবকল্প মহাসাধক। বহু শত বছর ধরে এভাবেই বসে আছেন। এটা যোগীদের রাজ্য। যোগেশ্বর আশ্রম। আজ তিনি শরীর বদল করবেন। বহু পুণ্যবলে তোমার অলৌকিক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ মিলেছে।’
রাম ঠাকুর দেখলেন যোগাসনে উপবিষ্ট মহাপুরুষের নিথর দেহ স্পন্দিত হয়ে উঠল। মুখ থেকে মন্ত্র বের হতে লাগল। ধুনির আগুন দপ করে উঁচুতে উঠে পড়ল। বিশালকায় সাপ সেখানে চলে এল। মহাত্মন সাপটাকে ধরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুনির আগুনে ছেড়ে দিতে ভস্মমাখা মাংসপিণ্ড বের হল। মহাপুরুষ পিণ্ড খেয়ে নেওয়া মাত্রই শরীর ফুলে বিকট আওয়াজে ফেটে তরুণ তাপসমূর্তি বেরিয়ে এল। গুরুদেব বললেন, ‘রাম একে বলে কায়াবদল। যোগীরা সাধনা করতে-করতে জীর্ণ শরীর ফেলে নতুন শরীর নেন।’
রাম ঠাকুর দেখলেন শরীর বদল করা মহাপুরুষ তাঁর সামনে দিয়ে বৃদ্ধ যোগীর পরিত্যক্ত আসন, চিমটা ও কমণ্ডলু নিয়ে ধীরে ধীরে অরণ্যে ঢুকে যাচ্ছেন। গুহার ভেতর পাঁচ জন মহাপুরুষ বসে আছেন। দুটো আসন ফাঁকা রয়েছে। অনঙ্গদেব বললেন, ‘এঁরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাজ হলে ফিরে আসবেন।’
যোগীদের শরীরগুলো পাথরের মতন হয়ে গেছে। জটা কাঁধের নীচ দিয়ে নামতে নামতে বিরাট আকার নিয়েছে। চোখগুলো চামড়ার আবরণে ঢেকে গেছে। মুখটা খালি বড়সড় হয়ে জেগে আছে। রাম ঠাকুর রোহিণীবাবু এবং কবিরাজ মশাইকে পৃথক পৃথক ভাবে বলেছিলেন, ‘এঁরা কেউ কায়া পরিবর্তন করে বেঁচে নেই। মুখমণ্ডলে জীবনের চিহ্ন আছে। একাসনে যুগের পর যুগ বসে আছেন। গুরুদেব নির্দেশ দিলেন এঁদের সেবাযত্ন করার। এঁরা প্রসন্ন হলে যোগসিদ্ধির সর্ব অভীষ্ঠ পূর্ণ হয়ে যাবে। ফলমূল তুলে এনে ধ্যানী মহাত্মাদের সামনে আমি খালি বসে থাকতাম। আহারহীন মহাত্মারা কৃপা করে এগুলোর কিছু কিছু গ্রহণ করতেন। এখানে তেরোটি গুপ্ত আশ্রম আছে। হিমালয়ের এ হল অপ্রাকৃত ভূমি। সাধারণের আসা-যাওয়া এখানে নেই।’
কাশীতে থাকতেন গুপ্তযোগী কালীপদ গুহরায়। তিনি রাম ঠাকুরের গুরুভাই। ১৯৫০ সালে কলকাতাতে শ্রীঅরবিন্দের আশি বছরের জন্মোৎসব পালন করবেন বলে বেশ আগে থেকে তোড়জোড় শুরু করেছিলেন ওঁর শিষ্যরা। কালীপদ গুহরায় শুনে বললেন, ‘বৃথা। শ্রীঅরবিন্দ ততদিন ইহলোকে থাকবেন না।’
অরবিন্দের এক শিষ্য তর্ক তুলতে যোগীরাজ শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন তিরোধানের তারিখ লিখে কাগজটি মুড়ে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ‘রেখে দিন আপনার কাছে, এখন খুলবেন না, আপনার গুরুদেব গতায়ু হলে পর মিলিয়ে নেবেন।’
অরবিন্দের শিষ্য কাগজটি নিতে অসম্মত হলে কালীপদ গুহরায় সেটা তাঁর বন্ধু অমলেন্দু দাশকে ডেকে তাঁর জিম্মায় দেন।
বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দিলীপকুমার রায় লিখছেন, ‘১৯৫০ সালে ৫ ডিসেম্বরে শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক তিরোধানের পরে অমলেন্দু কাগজটি খুলে দেখেন তারিখটি লেখা আছে... ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫০।’
১৯৬৬ সালে চৌষট্টি বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন কালীপদ গুহরায়। তিনি কায়াসিদ্ধ ছিলেন। কায়াব্যুহ রচনা করতে পারতেন। এক শরীর ছেড়ে আরেক শরীরে অনায়াসে চলে যেতে পারতেন। একবার একখানি যাত্রীভর্তি বাস তাঁর শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। তিনি ব্যূহ রচনা করে বেঁচে যান।
কালীপদ গুহরায় মাঝে মাঝে ভক্ত বিভুপদ কীর্তিকে যাজ্ঞবল্ক আশ্রমের কথা শোনাতেন। এ কোনও লৌকিক স্থান নয়। জ্ঞানগঞ্জের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। স্থূলদেহে সেখানে কখনও প্রবেশ করা যায় না। যোগেশ্বররা একমাত্র পৌঁছতে পারেন।
সাংগ্রীলা ঘাঁটির তিনটি সাধনাকেন্দ্রর কথা অনেক যোগীবরই উল্লেখ করে গেছেন। প্রথম কেন্দ্র জ্ঞানগঞ্জ, দ্বিতীয়টি সিদ্ধবিজ্ঞান আশ্রম, আর তৃতীয় স্থলটি হল যোগসিদ্ধাশ্রম। প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা আচার্য ও নির্দেশক রয়েছেন। এঁরা সকলেই কালজয়ী সাধক... ভৌতিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরকে আলাদা করতে জানেন, আত্ম শরীরে সাধনা করেন আর সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ করেন, যে কারণে মুহূর্তে মাইল-মাইল রাস্তা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারেন তাঁরা। প্রয়োজন পড়লে থার্ড ডাইমেনশনে নিজেদের ভৌতিক শরীর দিয়েও প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলতে পারেন।
অরুণাচল প্রদেশের সীমানা থেকে তিব্বতের উত্তর-পূর্বের পশ্চিমাংশে অবস্থিত অঞ্চলটিই সাংগ্রিলা। পুরো এলাকাটি ভূ- শূন্য এবং বায়ু- শূন্য। ফোর্থ ডাইমেনশন দ্বারা প্রভাবিত। দেশ, কাল এবং নিমিত্তের ঊর্ধ্বে এই জায়গাটি মহাযোগীদের তপস্যার প্রভাবে সৃষ্ট। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়ামের সংযোগস্থল বলে জায়গাটিকে খালি চোখে আমরা দেখতে পাই না। কৃষ্ণসুড়ঙ্গের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে সাংগ্রিলা সংযুক্ত। ভূমি সংস্থানের মাধ্যমে যোগীরা হাজার হাজার বছর অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে এখানে বেঁচে থাকেন। থার্ড ডাইমেনশনের বাসিন্দা বলে আমাদের সেখানে যাওয়ার কোনও শারীরিক ক্ষমতা নেই। অক্সিজেনের অভাব বোধ হবে এগলেই।
এগারোটি সিদ্ধমঠ নিয়ে সাংগ্রিলা ঘাটি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে অলৌকিক ও রহস্যময় মঠটিরই নাম জ্ঞানগঞ্জ। ভারতের উত্তর দিকের শেষপ্রান্ত গাড়োয়াল হিমালয় এবং তিব্বতের মধ্যবর্তী এক তুষারক্ষেত্রের মধ্যে সিদ্ধাশ্রম জ্ঞানগঞ্জ অবস্থিত। যেখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের প্রবেশ করার এক্তিয়ারই নেই। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মাদের নজরে যদি পড়েন থার্ড ডাইমেনশনের কোনও সাধক, যোগী, তাঁকে তাঁরা পৃথিবী থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন অনায়াসে।
উত্তুঙ্গ হিমালয়ে অবস্থিত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব কথিত জ্ঞানগঞ্জ, মহাত্মা রাম ঠাকুরের বর্ণিত কৌশিকী আশ্রম, যোগীবর কালীপদ গুহরায়ের বলা যাজ্ঞবল্ক আশ্রম, আর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাইয়ের কথকতার দ্রোণগিরি... সাংগ্রিলারই অন্তর্ভুক্ত এগারোটি গুপ্ত মঠের প্রকাশ্য চারটি। নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও এখানকার কার্যপ্রণালী ও আদবকায়দা যে মূলত এক সেটি রাম ঠাকুরের বক্তব্যেই স্পষ্ট।
রাম ঠাকুর বললেন, ‘কৌশিকী পর্বতের উপর আশ্রম। শিলাময় জায়গা। কোনও বরফ নেই। শিলা ভেদ করে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্ম নিয়েছে।’
গোপীনাথ কবিরাজ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায় এই আশ্রম?’
ঠাকুর বললেন, ‘মানস সরোবর পেরিয়ে অনেক দূরের পথ।’
কবিরাজ মশাই বললেন, ‘বহু তীর্থযাত্রী সেখানে যান, কেউ আশ্রম দেখতে পান না কেন?’
রাম ঠাকুর বললেন, ‘দিব্য আশ্রম সহজে দেখা যায় না। মনের আসক্তি দূর হলে কায়াসাধনে সিদ্ধ গুরুদেব নিয়ে যেতে পারেন কোনও নির্বাচিত শিষ্যকে। দেহের সমস্ত পাশ, এমনকী বস্ত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করে কৌশিকী আশ্রম পৌঁছতে হয়।’
জ্ঞানগঞ্জ বলে তিব্বতে কোনও জায়গা নেই। ওটি ভারতীয় যোগীদের দেওয়া নামসংকেত, যার চূড়ান্ত অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানগঞ্জ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করার জায়গা। তিব্বতে বর্ডার টাউন আছে, যার নাম গীয়ানৎসে... বাংলা মানে করলে জ্ঞানগঞ্জ দাঁড়ায়।
বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন, ‘দুশো-তিনশো হতে হাজার বছরের লোকও জ্ঞানগঞ্জে বর্তমান আছেন। সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে অনেকেই আহার করেন না... তবে যাঁরা ততটা উৎকর্ষ লাভ করেননি তাঁরা সামান্য কিছু গ্রহণ করেন মাত্র।’
বিন্ধ্যাচল থেকে ষোলো মাইল দূরের এক আশ্রমের কথা বিশুদ্ধানন্দজি শিষ্য গোপীনাথ মশাইকে বলেছেন। অনেক সাধু মহাত্মা সেখানে থাকেন। পাহাড়ে গুহার ভেতর শ্যামা ভৈরবী মাতার বাস। চারধারে খাড়া পাহাড়। হাতে ছুঁয়ে ফেলা দূরত্ব নিয়ে নীল মেঘেদের চলাচল। ঝর্ণা বয়ে চলেছে। সেসব পেরিয়ে আরেক আশ্রম। পাহাড়ি উপত্যকার একেবারে মাঝামাঝি জায়গা এটি। বড়সড় জায়গা জুড়ে আশ্রমভূমি। চারদিক পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলের পর জলে ভরা পরিখা। পরিখার ওপর দিয়ে ধাতুর সেতু। সেটি পেরিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়।
আশ্রমের ভেতর নানান শিক্ষাকেন্দ্র। বিজ্ঞানের একটি পৃথক বিভাগ আছে। যার আচার্য শ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরমহংস। গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন, ‘বিজ্ঞানের কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন এটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় জড়-বিজ্ঞান। বিশিষ্ট জ্ঞান- বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। তথাকথিত জড় ও চেতন। দুটোই বিজ্ঞানের বিষয়। সূর্য এর কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান আশ্রয় বলে জ্ঞানগঞ্জে একে সূর্যবিজ্ঞান বলা হচ্ছে। জাগতিক ও ব্যবহারিক যাবতীয় ব্যাপার সূর্যাধীন। স্বরূপোলব্ধি করতে হলে সৌরতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।’
জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমের মুখ্য আচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ পরমহংস। তিনি প্রাচীন আশ্রমটির তত্ত্বাবধায়ক। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন, ‘জায়গাটা বেশ পুরনো। এখানে ইন্দ্রভবন ছিল। জ্ঞানানন্দ স্বামী এটি সংস্কার করিয়ে নেন। আশ্রমে আছে যুবক ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী কুমারী মেয়েরা। আর আছে সূর্যবিজ্ঞান শেখার ছাত্ররা।’
বিশুদ্ধানন্দ ওঁর গুরু নিমানন্দ স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জে রইলেন আট-দশ দিন। তারপর গুরুদেব তাঁকে শ্রীশ্রীমৎ মহাতপার কাছে নিয়ে গেলেন। বারোশো বছর বয়স মহাতপার। মহাশক্তিশালী যোগীপুরুষ। জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমে তিনি থাকেন না।
দুর্গম এক পাহাড়ি গুহার ভেতর শ্যামা ভৈরবী একা থাকেন। তাঁর বয়সও হাজার পেরনো।
মহাতপা থাকেন আলাদা এক গুহায়। সেখানে ওঁর আরাধ্য রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আছে। এখানে কোনও ঘরবাড়ি নেই। তিনি গুহার ভেতর সর্বক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকেন।
মহাতপার গুরুমা খ্যাপা মাই থাকেন কিছু দূরের মনোহর তীর্থে। পাহাড় ঘেরা দুর্ভেদ্য এলাকা সব। হেঁটে চলা যাবে না। মহাতপা চলে যান তাঁরই সমসাময়িক বয়সের মা- গুরুকে দেখতে আকাশপথ ব্যবহার করে। বরফে ঢাকা এলাকার ভেতর আরও কয়েকটি মঠ আছে। সবগুলো রাজরাজেশ্বরী গুহাভূমির নির্দেশমতো চলে।
মহাতপা ঋষি জ্ঞানগঞ্জ সহ সমস্ত যোগশিক্ষার নানান গুপ্ত মঠের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। তাঁর প্রধান শিষ্য ভৃগুরাম স্বামী। তিনিও আকাশচারী।
বিশুদ্ধানন্দজির গুরুদেব নিমানন্দ সহ সকল যোগী পরস্পর পরস্পরের গুরুভাই। সকলের গুরুদেব মহর্ষি মহাতপা।
ভৃগুরাম যোগ শেখান। সূর্যবিজ্ঞানের শিক্ষা দেন শ্যামানন্দ পরমহংস। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাক্রম চলে। বিশুদ্ধানন্দের মহাতপার কাছে দীক্ষা হওয়ার পর শিক্ষা চলতে থাকে জ্ঞানগঞ্জের যোগীঋষিদের কাছে।
কাশীর আশ্রমে বিশুদ্ধানন্দজিকে এক শিষ্য প্রশ্ন করেন, ‘জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মারা আপনার সঙ্গে কোন ভাষাতে কথা বলতেন?’
স্বামীজি উত্তর দেন, ‘বাংলাতেই তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতেন।’
শিষ্যটি প্রশ্ন করেন, ‘তাঁরা সকলেই কি বাংলা ভাষা জানতেন?’
বিশুদ্ধানন্দ বললেন, ‘না জানলেই বা কী! ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে সব ভাষাতেই কথা বলা যায়। মূল যে ভাষা তা যোগীদের আয়ত্তে। যোগীরা দেবভূমিতে আরোহণ করে বক্তার অভিপ্রায় বুঝতে পারেন। অজ্ঞাত ভাষা বলার সময় শ্রোতার স্তরে নীচে নেমে আসেন ওঁরা। জ্ঞানগঞ্জের সাধুরা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা হিব্রুতে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রোতার মাতৃভাষায় তাঁদের হিব্রুভাষাগুলো স্বরনিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হয়ে শ্রোতাদের কানে গিয়ে পৌঁছাত।’
গোপীনাথ কবিরাজ বসে আছেন গুরুদেবের সম্মুখে। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বললেন, ‘পশ্চিম থেকে চিঠি এসেছে। চিঠিতে তোমাদের কথা-টথা আছে।’
পশ্চিম হল জ্ঞানগঞ্জের সংকেত। অনধিকারীরা সামনে থাকলে কাশীর আশ্রমে এমন সংকেতে কথা চলত। ১৯২৬ সাল... জ্ঞানগঞ্জের আচার্য উমানন্দ স্বামীর চিঠি এল। গোপীনাথ দেখলেন চিঠির গায়ে জ্ঞানগঞ্জের মোহর। নাগরি লিপিতে লেখা, ‘পঞ্জাব আশ্রম।’ ভাবলেন, না-থাকা জায়গার নামে আসা খামের ওপর পোস্টাপিসের মোহর পড়ে কী করে!
একদিন দেখলেন লেন্স নিয়ে বসেছেন বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব। বড় বড় ওষুধের শিশিগুলো শূন্যমার্গে ভেসে ভেসে আসছে। গুরুদেব ভৈরবী মায়েদের কাপড় কিনেছেন। সেসব শূন্যমার্গে চলেছে জ্ঞানগঞ্জে। লেন্সে ফোকাস করে তিনি সাধারণ পাথরকে হীরক করে দিলেন। ময়দার লেচিগুলোকে চমচমের আকার দিয়ে পাতায় মুড়ে রোদে ধরে লেন্সে ফোকাস করে তৈরি করলেন চমচম। একটুকরো নীল কাগজে গুরুদেব একটু তুলো রেখে কাগজ ও তুলোর মধ্যে ভিক্টু মাতার হাতের মাপের গোলাকৃতি তামার সূক্ষ্ম তার স্থাপন করলেন। একটি লেন্সের সাহায্যে একটু দূর থেকে তুলোর উপর অল্প রোদ ফেলা হল। এক- দু’মিনিট পর সোনার হাঙ্গরমুখো রুলি তৈরি হল। স্যাকরার দোকানে নিয়ে গেলে দোকানি বলল, ‘খাঁটি সোনা।’
কাশীর হনুমান ঘাটের কাছে দিলীপগঞ্জের দোতলা বাড়িতে বসে গোপীনাথ কবিরাজ পড়ে চলেছেন জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মাদের লেখা চিঠিপত্রগুলো। চিঠিও আসতে দেখলেন তিনি আশ্রমের ঘরে শূন্যমার্গে ভেসে-ভেসেই। অনেক যত্নে গুরুদেবের কাছে আসা চিঠিগুলো তিনি রেখে দিতেন নিজের জিম্মায়। গুরুদেব বললেন, ‘কেন ব্যস্ত হও?’
চব্বিশ বছর পর বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব অনুমতি দিলেন জ্ঞানগঞ্জের চিঠি প্রকাশ করতে। গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশ পাচ্ছে কল্যাণ পত্রিকা। গোপীনাথজি জ্ঞানগঞ্জের বিবৃতি দিলেন। ভৌগোলিক সীমার বাইরে থাকা এ স্থানের প্রকাশ ঘটল ভারতীয় অধ্যাত্মমণ্ডলে।
ভারতের উচ্চকোটির মহাত্মারা জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সাধক রামদাস কাঠিয়াবাবা কৈলাস- মানস সরোবরে তীর্থ পরিদর্শন কালে জ্ঞানগঞ্জে গিয়েছিলেন। রাম ঠাকুর ও কালীপদ গুহরায়ের গুরুদেব অনঙ্গদেবই ছিলেন জ্ঞানগঞ্জের ভৃগুরাম স্বামী। জ্ঞানগঞ্জের কাছে গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট যোগী গম্ভীরনাথজির যোগাসন ছিল। গম্ভীরনাথজিরই শিষ্য হলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শিবকল্প যোগী স্বামী প্রণবানন্দ।
জেমস হিল্টন একজন ইংরেজ লেখক। তাঁর লেখা কল্পলৌকিক উপন্যাস ‘Lost Horizon’ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এই বইতে হিল্টন ভারতের এমন কিছু রহস্যময় ঘাটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে মানুষ শত শত বছর ধরে বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছেন যোগ সাধনার মাধ্যমে। তাঁদের কারও শরীরেই বয়সের ছাপ পড়েনি। যোগ সাধনার মাধ্যমে পাঁচশো-ছশো বছর ধরে শরীরে থাকা সাংগ্রিলার সাধুদের কথা হিল্টন গোচরে আনার পর তাঁর বইয়ে দেওয়া ভারত-তিব্বত-ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে দেশ-বিদেশের অনুসন্ধানকারী দল সাংগ্রিলা ঘাঁটির খোঁজে আসতে থাকে। কিন্তু কোনও দলই সফল হয়নি সাধুদের ডেরা খোঁজার ক্ষেত্রে। অনেক অভিযাত্রী অনুসন্ধান করতে-করতেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন, যাঁদের কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।
ষোলো বছরের ঘর-পালানো একটি ছেলে তিব্বত যায় সাধুদের দলের সঙ্গে, গ্যাংটক থেকে লাসা, ব্রহ্মপুত্র, কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে ঘুরে সে ফেরে লিপু লেক নৈনিতাল হয়ে। ১৯৫৬ সালের তিব্বত যাত্রাতে পুণ্য সঙ্গমস্থল নানগুং নদী যেখানে মিলেছে পুণ্যস্রোত ব্রহ্মপুত্রতে, তার অনতিদূরে রহস্যময় তান্ত্রিক পীঠস্থান ইউংদ্রুলিং, সেখানে তখন কালচারাল রেভোল্যুশনের নামে চীন প্রলয়ের ধ্বংসলীলা চালায়নি, সেখানে এক গুহার ভেতর ঘর-পালানো ছেলেটি দেখা পায় এক তান্ত্রিক যোগীপুরুষের। তাঁর পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে ছেলেটি কৈলাসখণ্ডে মানস সরোবরের ধারে তান্ত্রিক যোগীর কাছে পেল একদিন দীক্ষা। ঘর পালানো ছেলেটি পরবর্তী সময়ে পরিণত হল ভূ-পর্যটকে।
২০০৭ সালে ভূ-পর্যটক বিমল দে ফের গেলেন ঐতিহ্যময় তিব্বত তীর্থে তান্ত্রিকগুরুর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে তিব্বতিদের জীবনযাত্রার বিরাট পরিবর্তন। তান্ত্রিকগুরু কৈলাসবাবাকে খুঁজতে খুঁজতে বিমল দে পৌঁছে গেলেন তিব্বতের রহস্যময় নারী-মঠ ওসেরলিং গুম্ফায়, সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন সন্ন্যাসিনী আছেন। ধুনির সামনে বসে আছেন মহাযোগীনী ভৈরবী মা। প্রচুর বয়স তাঁর, কিন্তু অতি সুন্দরী যুবতীর মুখ মায়ের। মাথার জটাকে গুছিয়ে কোলের ওপর রেখে লাল রঙের চাদরে ঢাকা শরীরে সিদ্ধাসনে বসে রয়েছেন ভৈরবী মা।
বিমল দে বসে রয়েছেন অপরূপ মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে। তাঁর মুখ থেকে কোনও কথা বের হচ্ছে না। ভৈরবী যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে এখানে টেনে এনেছেন।
এক সন্ন্যাসিনী এসে মায়ের হাতে একটি পাত্র ধরাতে ভৈরবী মা সেটি বিমলবাবুর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, ‘পি - লে বেটা।’
‘আশ্চর্য! তিনি হিন্দি বলেন!’ লম্বা কাচের গ্লাস হাতে ধরে বিমল দে ভাবছেন।
সেবিকা সন্ন্যাসিনী বললেন, ‘মা জানেন আপনি কবে তিব্বতে এসেছেন, কেন এসেছেন।’
পরিষ্কার হিন্দিতে ভৈরবী মা বললেন, ‘আমি অধিকাংশ সময় হিন্দুস্থানে থাকি, ওখানে আমার অনেক ছেলেমেয়ে আছে, তারা ডাকে, যেতেই হয়। মহাগুরু বুদ্ধাবতার গুরু রিমপোচ্চে নির্বিঘ্নে সাধনার জন্য হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে মোট ষোলোটি গুপ্ত গুহা-গ্রাম তৈরি করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে হিমালয় ডিঙিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে নেমেছে, সেখানে এখনও অনেক মৌনী গুহা আছে, বুঝলে বাবা? তুমি এখান থেকে কৈলাসে যাও, প্রথমে চুরাশি সিদ্ধ শ্মশান। শ্মশানে গিয়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসবে। তারপর শিবস্থান। ওখানে সূক্ষ্ম শরীরে অনেক যোগী যোগীনীরা আছেন, তাঁরাই তোমাকে পরিষ্কার করে বলে দেবেন তোমার দীক্ষাগুরু কৈলাসবাবা এখন কোথায় আছেন।’
বিমল দে লিখছেন, ‘এক আশ্চর্য পাওয়া জ্ঞানগঞ্জ রি-পুক মঠের ভৈরবী মাতাজি... এক রহস্যময়ী মা... অপরূপা নারী। তাঁর নির্দেশ পেয়ে গেলাম কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর খণ্ডে। সে যাত্রায় কৈলাস পরিক্রমার উদ্দেশে নয়, উদ্দেশ্য ছিল চুরাশি মহাসিদ্ধ যোগী শ্মশানে রাত কাটানো, মাতাজির দ্বিতীয় আদেশ ছিল... শিবস্থল থেকে পাপক্ষয় পাথরগুহা অতিক্রম করা... মাতাজিই আমাকে পার করিয়েছিলেন সেই ভয়াবহ সুড়ঙ্গ পথ, তাঁর কৃপায় অসাধ্য সাধন হয়েছে। ভৈরবী মাতা জ্ঞানগঞ্জের এক অলৌকিক নারী। লামা, সাধু, জ্ঞানী ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে রাস্তার ভিখারি পর্যন্ত সবাই তাঁর নাম শুনেছে। স্থানীয় লোকেরা বিপদে পড়লে তাঁকেই ডাকে, অথচ খুব কম লোকেই তাঁর দর্শন পেয়েছে।’
১৯৫৬ সালে তিব্বতের লাংবোনা গুহার যোগীপুরুষ, দীক্ষাগুরু কৈলাসবাবাকে শেষে ভূ-পর্যটক বিমল দে খুঁজে পেলেন অমরকণ্টকের বরফানি ধামে।
বরফানি বাবা বসে আছেন। এখানে সকলের কাছে তিনি দাদাজি। বয়স দুশো পেরিয়ে গেছে।
বিমল দে বললেন, ‘কৈলাসখণ্ডে লাংবোনা গোম্ফায়, গুহার সঙ্গেই ছিল আপনার ঘর, যেদিন দেখলাম সেদিন থেকে আপনি আমার কৈলাসবাবা।’ বলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন বাবার শ্রীচরণে।
বরফানি দাদাজি বললেন, ‘ওখান থেকে তুমি পারখা হয়ে চলে গেলে কৈলাস পরিক্রমায়। তারপর আবার তুমি এলে মানস সরোবরের ধারে চিউ গোম্ফাতে।’
দাদাজি সোজা হয়ে চেয়ারে বসে কথাগুলো বলছেন। উপস্থিত ভক্তেরা কৌতূহলী হয়ে শুনছেন কৈলাসবাবার কথা।
বিমল দে লিখছেন, ‘দীর্ঘ তিপান্ন বছর আগেকার সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ তাঁর মুখে শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এই দীর্ঘ তিপান্ন বছর ধরে তিনি তো হাজার হাজার ভক্তের কথা শুনেছেন, তিনি তো সাক্ষাৎ ইতিহাস। আমার মতো এক ছোট্ট মানুষের সামান্য ঘটনা তিনি কী করে মনে রেখেছেন? বুঝলাম, আমি তাঁকে ধরে রেখেছি আর তিনিও আমাকে ছাড়েননি। তিনি লালসুতো দিয়ে আমার হাতে আড়াই পাকের বন্ধন পরিয়ে দিয়ে ফের গুরু-শিষ্য সম্পর্কে বাঁধলেন।’
কৈলাসবাবা উপস্থিত ভক্তদের বললেন, ‘জানো বাবা, কৈলাসে অনেকেই আমাকে কৈলাসবাবা ডাকত... এই বাবাকে আমার গুহাতেই কয়েকদিন রেখেছিলাম। ওকে সব শিখিয়ে তারপর পাঠিয়েছিলাম পরিক্রমায়। ও আমার কৈলাসখণ্ডের শিষ্য। আমি কৈলাসে ছিলাম আরও ছ-সাত বছর, তারপর চীনারা আর থাকতে দিল না। আমি চলে এলাম, আমার অনেক পরিচিত যোগীরাও চলে আসে।’
কৈলাস পর্বতের উচ্চতা ৬ হাজার ৬৩৮ মিটার। এভারেস্টের থেকে ২ হাজার ২০০ মিটার কম হলেও এখনও পর্যন্ত পর্বতারোহীরা এর চূড়াতে উঠতে পারেননি। কৈলাসে যখন কোনও পর্বতারোহী ওঠার চেষ্টা করেন, কিছুটা উঁচুতে যাওয়ার পরই প্রকৃতি বিরূপ হতে শুরু করে। ওঠে ঝড়, তেড়ে আসে পাথরের টুকরো, পা পিছলা?
দেশ, কাল ও নিমিত্তে আটকে গেছে গোটা পৃথিবীর সমস্ত জিনিস। যা কিছু এখানে আছে, সবেরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা রয়েছে, যা তৃতীয় মাত্রা... থ্রি ডাইমেনশন নির্দেশ করে। মানুষ যখন স্থানহীনতা... শূন্যতা প্রভাবিত কোনও একটি এলাকার মধ্যে ঢুকে যায়, সে রহস্যময় এক নতুন বাতাবরণে প্রবেশ করে। তার মনের, প্রাণের শক্তি সেখানে আশাতীতভাবে বেড়ে যায়। কালের প্রভাব সেখানে এতই নগণ্য যে শরীরের ওপর তা একেবারে পড়ে না। বায়ু-শূন্যতা আর ভূ-শূন্যতায় সম্পৃক্ত জায়গাগুলোকে বলা হচ্ছে চতুর্থ আয়াম... ফোর্থ ডাইমেনশন। এখানে পৌঁছে গেলে তার সত্তা অদৃশ্য, লুপ্ত হয়ে যায়। অস্তিত্ব যেমন ছিল তেমনই থাকে। যদি কোনও মানুষ পঁচিশ বছর বয়সে চতুর্থ আয়াম প্রভাবিত ক্ষেত্রে চলে যায়, তাহলে তার শরীর বহু বছর ধরে ওই পঁচিশ বছর বয়সের যুবকের মতো হয়ে থাকবে, বয়সের কোনও ছাপ পড়বে না। চতুর্থ আয়াম প্রভাবিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত যোগীরা থাকেন, পাঁচশো-ছশো বছর বেঁচে থাকা তাঁদের পক্ষে কোনও সমস্যাই নয়। তাঁদের শরীর একরকম থেকে যায়, যদিও বয়স বাড়তে থাকে কালের নিয়মে। কালের প্রভাব শরীরে গিয়ে পড়ে না। চতুর্থ আয়াম থেকে যোগীরা যখন থ্রি ডাইমেনশনে বাঁধা এ সংসারে প্রবেশ করেন, শরীরের ওপর প্রভাব পড়তে থাকে, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। একটা সময় পর যোগীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।
যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী চতুর্থ আয়ামে অবস্থানরত এমনই এক যোগীপুরুষের কথা তাঁর শিষ্যবৃত্তে জানিয়েছেন, যিনি চক্রাকার আলোকপুঞ্জের মতো ঘুরে ঘুরে আকাশপথ দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পৃথিবীর যে কোনও স্থানে অবতরণ করতে পারেন। পৃথিবী বিখ্যাত যোগী পরমহংস যোগানন্দ তাঁর আত্মজীবনী ‘Autobiography of a Yogi’ বইটিতে চতুর্থ আয়ামে অবস্থানরত মহাবতার বাবাজির অস্তিত্বের বিষয় সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। যোগানন্দজির সংস্কৃতের শিক্ষক স্বামী কেবলানন্দ কিছুদিন বাবাজি মহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে কাটিয়েছিলেন। তিনি পরমহংস যোগানন্দকে জানিয়েছেন, ‘মহাগুরু হিমালয়ে তাঁর দলবল নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ইচ্ছা করলে তবেই কেউ তাঁকে দেখতে বা চিনতে পারে, তা না হলে নয়। তিনি ঈষৎ পরিবর্তিত বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে তাঁর নানা শিষ্যদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন। তাঁর পঁচিশ বছরের যুবক চেহারার মুখে কোনও সময় হালকা দাড়ি-গোঁফ থাকত, কখনও একেবারে পরিষ্কার ঝকঝকে মুখমণ্ডল। তাঁর অক্ষয়দেহের কোনও প্রকার আহারের প্রয়োজন হতো না। শিষ্যদেরকে দেখা দেওয়ার সময় লৌকিকতা হিসেবে তিনি তাঁদের হাতে ফল, পায়েস, ঘি, ভাত ধরিয়ে দিয়ে ফের অদৃশ্য হয়ে যেতেন।’
রণবাজপুরের যোগী রামগোপাল মজুমদার যোগানন্দজিকে জানিয়েছেন, ‘কখনও কখনও আমি নির্জন গুহা ছেড়ে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গিয়ে থাকতাম। একদিন গভীর রাতে গুরুদেবের ঘরে ধ্যানে বসেছি, তিনি আমাকে অদ্ভুত আদেশ দিলেন, রামগোপাল, এক্ষুনি তুমি দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে যাও।’
ঘাটে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে আছি। উজ্জ্বল নক্ষত্র আর চন্দ্রালোকে রাত হাসছে। হঠাৎ পায়ের কাছেই একটা প্রকাণ্ড পাথর উপরে উঠতে লাগল, খুলে গেল গুহা। সেখান থেকে একজন অপরূপ সুন্দরী যোগীনী বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, আমি মাতাজি, বাবাজি মহারাজের বোন। আমি তাঁকে আর লাহিড়ী মহাশয়কেও আজ রাত্রে আমার এই গুহায় আসতে বলেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবার জন্যে।
মাতাজির বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে দুটি জ্যোতি নেমে এল। দুটিই রূপ নিল মানুষের মূর্তিতে। একটা মূর্তি গুরুদেবের আর একটা অল্পবয়স্ক, উজ্জ্বল চেহারার ও সুদীর্ঘ চুলধারী তরুণের।
গুরুদেব, মাতাজি ও আমি বাবাজিকে প্রণাম করার পর তিনি বললেন, দেহ ছেড়ে দেওয়ার কথাটি।
‘বললেন, পরব্রহ্মসাগরে আত্মার তরঙ্গ দৃশ্যই হোক আর অদৃশ্যই হোক... প্রভেদ কিছু নেই।’
মাতাজি বললেন, ‘যদি কোনও পার্থক্য না থাকে গুরুদেব, তবে দয়া করে আপনি আর দেহত্যাগ করবেন না।’
মহাবতার বাবাজি বললেন, ‘তবে তাই হোক। আমি কখনও আমার এ জড়দেহ আর পরিত্যাগ করব না। এই দেহ পৃথিবীতে, অন্তত জনকতকের কাছে সর্বদাই দৃশ্য হয়ে থাকবে।’
১৮৯৫ সালে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন সাতষট্টি বছর বয়সে। ১৯৫২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ অ্যাঞ্জেলসে দেহ রাখেন পরমহংস যোগানন্দজি। তিনি বাবাজি মহারাজের যে সূক্ষ্ম শরীর দর্শন করেছিলেন তার একটা স্কেচ করিয়ে রাখেন। এটিই মহাবতার বাবাজি মহারাজের একমাত্র ছবি।
পুরাণপুঁথির ভেতর সাংগ্রিলা ঘাটির উল্লেখ পাই আমরা। ভারতীয় ঋষিরা বলছেন, ‘স্বর্গীয় বাতাবরণে ডুবে থাকা এই ঘাটিটি জ্যোতির আভায় পূর্ণ। এখানে গুপ্তভাবে অনেক যোগাশ্রম, সিদ্ধাশ্রম, তান্ত্রিক মঠ আছে। সেইসব মঠ ও আশ্রমে আছেন কালজয়ী সাধক আর যোগী-যোগীনীরা। এঁরা সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করেন, উপযুক্ত শিষ্যদের দর্শনও দেন।’
সাংগ্রীলার কোনও সিদ্ধাশ্রমে আজও বাস করেন মহাবতার বাবাজি। অনেকে বলেন উন্নত সাধকদের সাধনে সাহায্য করার জন্য তিনি আমাদের থ্রি ডাইমেনশনের পৃথিবীতে নেমে আসেন চতুর্থ আয়াম থেকেই।
হাড়িয়াখণ্ড কথার মানে পবিত্র জায়গা। নেপাল ও তিব্বতের মাঝে খুব প্রাচীন এক জায়গা হল হাড়িয়াখণ্ড। মানস সরোবর থেকে বেরিয়ে কৈলাস গঙ্গা, গৌতম গঙ্গা ও গোলা নামে তিনটি ক্ষীণধারার নদী পার হয়ে কয়েক ঘণ্টা হেঁটে গেলে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি গুহা রয়েছে। ওখানে এক যোগীপুরুষের বাস ছিল। হাড়িয়াখণ্ডের যোগী লোকমুখে হৈড়াখান বাবা বলেই পরিচিত ছিলেন। পরিষ্কার সাদা কাপড় পড়তেন তিনি। সৌম্যমূর্তি ও সুন্দর চেহারা তাঁর। দেখলে মনে হতো বাবার বয়স তিরিশের বেশি নয়। কিন্তু ওই অঞ্চলের পুরনো মানুষেরা বলতেন, ‘আমাদের ঠাকুরদাদারা পর্যন্ত বাবাকে দেখেছেন। তাঁরা কোন কালে চলে গিয়েছেন! আমাদের সময় হয়ে এল। শরীরে জরা ধরে গেছে। বাবার চেহারায় এখনও নবযৌবন রয়েছে।’
বলা হয় হৈড়াখান বাবাও ছিলেন চতুর্থ আয়ামের মানুষ। কৈলাস পর্বতে হৈড়াখান বাবার অনেক লীলাকাহিনি প্রচলিত আছে। বারো-তেরো বছর বয়সে হঠাৎ করে তাঁকে এ অঞ্চলে দেখা গেল। তিনি তখন জ্যোতির্ময় বালক। বালকের সঙ্গে ঘোরে হিংস্র দুটি কুকুর কালী আর লালি। এই বালকই কিশোর থেকে যুবক হলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি যখন দেহ রাখলেন, তাঁর চেহারায় ছড়িয়ে ছিল ত্রিশ বছরের যুবকের যৌবন।
কলকাতার বাসিন্দা শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাইয়ের শিষ্য দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য ১৯৭৯ সালে যখন গিয়েছেন হৈড়াখান বাবার সঙ্গে দেখা করতে, হাড়িয়াখণ্ডে আশ্রম গড়ে উঠেছে। ১০৮টি সিঁড়ি বেয়ে বাবার গুহায় পৌঁছতে হয়। ‘সহজ ক্রিয়াযোগ ও যোগ ঐশ্বর্য’ গ্রন্থে দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য লিখছেন, ‘ভক্তদের চোখে বাবা দেবতাস্বরূপ। কায়াকল্প ধরে সৃষ্টির আদি হতে তিনি আছেন। হৈড়াখান বাবা যুগযুগান্তরের কথা বলতে পারেন। মাঝে মাঝে তিনি সমবেত ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলেন, উপস্থিত এখানে জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত কেউ আছ কি না। অনেক বিদেশি ভক্তকে দেখে তিনি তাঁদের নামধাম ইত্যাদি বলে বলেন, তোমরা আমার পূর্বজন্মের পরিচিত।’
একবিংশ শতকের অন্যতম মহান সাধক স্বামী রামার জন্ম হিমালয়ের কোলে। খুব ছোটবেলা থেকে তিনি হিমালয়ে বসবাসকারী যোগী... বাঙ্গালি বাবার সাহচর্য লাভ করেন। গুরুর নির্দেশে তিনি সুদূর পাঞ্জাব হিমালয় থেকে কুমায়ুন এবং গাড়োয়াল হিমালয়, আবার নেপাল থেকে অসম এবং সিকিম থেকে ভুটান এবং তিব্বত অঞ্চলে সুবিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালার দুর্গম খাঁজে খাঁজে যোগীদের কুঠিয়ায় কাটান। যুবকালে তিনি অনেক সময় কৈলাস পর্বতের পদতলে বসে মানস সরোবরের জল পান করতেন। কেদারনাথ এবং গঙ্গোত্রীতে প্রায় তিনি প্রকৃতি-মায়ের কোলে জন্মানো শাক-সব্জি-মূল রান্না করে খেতেন আর থাকতেন হিমালয়ের গুহায়-গুহায় যোগীদের সান্নিধ্যে।
স্বামী রামা গুরুদেবের কাছে শুনেছিলেন যে, হৈড়াখান বাবা এবং হিমালয়ের অন্য কয়েকজন যোগী অনেক বছর তাঁর সঙ্গে শিক্ষা নিয়েছিলেন। কুমায়ুন হিমালয়ে হৈড়াখান বাবা বেশ বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তাঁকে সকলে হিমালয়ের শাশ্বত বাবাজি বলেই মান্য করত। হৈড়াখান বাবা মহাগুরুদেবের কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন। স্বামী রামা গুরুদেবের কথামতো দুর্গম এবং ক্লান্তিকর যাত্রা করে হৈড়াখান বাবার গুহায় পৌঁছেছিলেন।
‘Living with the Himalayan Masters’ গ্রন্থে স্বামী রামা লিখছেন তিব্বতের এক গুম্ফায় তিনি মহাগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, ‘আমার মহাগুরু ছোটকাল থেকে হিমালয়ের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরাও সাধু ছিলেন। তিনি অবয়বানুযায়ী অতি বৃদ্ধ কিন্তু স্বাস্থ্যবান দেখতে ছিলেন। খুব ভোরে এবং সন্ধ্যাবেলা মাত্র দু’বার তিনি আসন ছেড়ে উঠতেন। তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুট নয় বা দশ ইঞ্চি, খুবই শীর্ণকায়, অথচ প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর ঝোপের মতো ভ্রু-যুগল, সদা অত্যুজ্জ্বল মুখমণ্ডল থেকে কী গভীর এক প্রশান্তি বিচ্ছুরিত হতো! সদা হাস্যমুখে অধিকাংশ সময়ে চমরীগাইয়ের দুধ সেবন করে এবং কখনও বা যবের সুরুয়া খেয়ে সানন্দে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। কোনও সময়ে কয়েকজন লামা এসে তাঁর কাছে কিছুদিন অধ্যয়ন করে যেতেন। পাহাড়ের সাত হাজার ফুট উচ্চতায় একটি প্রাকৃতিক গুহায় তিনি বাস করতেন। স্যাঁতস্যাতে ভাব কাটাতে এবং জল ও দুধ গরম করতে কখনও-সখনও গুহার ভিতরে তিনি আগুন জ্বালতেন। তাঁর ছাত্রেরা গুহার মুখে একটি বারান্দা মতো তৈরি করে দিয়েছিল। এখানে বসেই তিনি আমাকে পরকায়া প্রবেশ শিখিয়েছিলেন। গুহার মধ্যে বসা অবস্থাতে মহাগুরুর শরীর আবছা হতে শুরু করল। রক্তমাংসের দেহটি হয়ে গেল এক টুকরো মেঘ। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। অদৃশ্য তিনি। কিছু পর ধীরে ধীরে তিনি নিজের শরীরের অবয়ব ধারণ করে আমাদের সামনে দৃশ্যমান হলেন।’
চতুর্থ আয়ামে অবস্থানরত সময়ে চোখের সামনে দেখা কায়াকল্প সাধুর কাহিনি রাম ঠাকুর তাঁর শিষ্য রোহিণীকুমার মজুমদার ও কাশীতে অবস্থানকালে জ্ঞানগঞ্জের সাধক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্য প্রখ্যাত পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মশাইকে বিস্তারিত বলে গিয়েছেন। হিমালয়ের শিখর অভিমুখে চলেছেন গুরু অনঙ্গদেবের সঙ্গে রাম ঠাকুর। পর্বতের শেষ চূড়ায় বশিষ্ঠাশ্রমে গুরুর সঙ্গে দুটো দিন থাকার পর যুবক রাম চলেছেন পূর্বদিকের দুর্গম সিদ্ধপীঠে। বরফ ঢাকা পথের চারদিকে চারটি স্ফটিক স্তম্ভ। মাঝখানে তুষারশুভ্র শিবলিঙ্গ। জটাজূটধারী ভৈরবী মা ধ্যানস্থা হয়ে রয়েছেন। তিনি অনঙ্গদেবের কথাতে তপঃসিদ্ধ দিব্যদেহ থেকে জ্যোতি বের করতে করতে তাঁদেরকে নিয়ে চললেন প্রাচীন গুহায়। গুহার সামনে ধুনি জ্বলছে। সেখানে বসে অতি বৃদ্ধ মহাত্মা সাধনা করে চলেছেন। গুরুদেব তাঁকে বললেন, ‘রাম, মহাত্মন দেবকল্প মহাসাধক। বহু শত বছর ধরে এভাবেই বসে আছেন। এটা যোগীদের রাজ্য। যোগেশ্বর আশ্রম। আজ তিনি শরীর বদল করবেন। বহু পুণ্যবলে তোমার অলৌকিক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ মিলেছে।’
রাম ঠাকুর দেখলেন যোগাসনে উপবিষ্ট মহাপুরুষের নিথর দেহ স্পন্দিত হয়ে উঠল। মুখ থেকে মন্ত্র বের হতে লাগল। ধুনির আগুন দপ করে উঁচুতে উঠে পড়ল। বিশালকায় সাপ সেখানে চলে এল। মহাত্মন সাপটাকে ধরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুনির আগুনে ছেড়ে দিতে ভস্মমাখা মাংসপিণ্ড বের হল। মহাপুরুষ পিণ্ড খেয়ে নেওয়া মাত্রই শরীর ফুলে বিকট আওয়াজে ফেটে তরুণ তাপসমূর্তি বেরিয়ে এল। গুরুদেব বললেন, ‘রাম একে বলে কায়াবদল। যোগীরা সাধনা করতে-করতে জীর্ণ শরীর ফেলে নতুন শরীর নেন।’
রাম ঠাকুর দেখলেন শরীর বদল করা মহাপুরুষ তাঁর সামনে দিয়ে বৃদ্ধ যোগীর পরিত্যক্ত আসন, চিমটা ও কমণ্ডলু নিয়ে ধীরে ধীরে অরণ্যে ঢুকে যাচ্ছেন। গুহার ভেতর পাঁচ জন মহাপুরুষ বসে আছেন। দুটো আসন ফাঁকা রয়েছে। অনঙ্গদেব বললেন, ‘এঁরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাজ হলে ফিরে আসবেন।’
যোগীদের শরীরগুলো পাথরের মতন হয়ে গেছে। জটা কাঁধের নীচ দিয়ে নামতে নামতে বিরাট আকার নিয়েছে। চোখগুলো চামড়ার আবরণে ঢেকে গেছে। মুখটা খালি বড়সড় হয়ে জেগে আছে। রাম ঠাকুর রোহিণীবাবু এবং কবিরাজ মশাইকে পৃথক পৃথক ভাবে বলেছিলেন, ‘এঁরা কেউ কায়া পরিবর্তন করে বেঁচে নেই। মুখমণ্ডলে জীবনের চিহ্ন আছে। একাসনে যুগের পর যুগ বসে আছেন। গুরুদেব নির্দেশ দিলেন এঁদের সেবাযত্ন করার। এঁরা প্রসন্ন হলে যোগসিদ্ধির সর্ব অভীষ্ঠ পূর্ণ হয়ে যাবে। ফলমূল তুলে এনে ধ্যানী মহাত্মাদের সামনে আমি খালি বসে থাকতাম। আহারহীন মহাত্মারা কৃপা করে এগুলোর কিছু কিছু গ্রহণ করতেন। এখানে তেরোটি গুপ্ত আশ্রম আছে। হিমালয়ের এ হল অপ্রাকৃত ভূমি। সাধারণের আসা-যাওয়া এখানে নেই।’
কাশীতে থাকতেন গুপ্তযোগী কালীপদ গুহরায়। তিনি রাম ঠাকুরের গুরুভাই। ১৯৫০ সালে কলকাতাতে শ্রীঅরবিন্দের আশি বছরের জন্মোৎসব পালন করবেন বলে বেশ আগে থেকে তোড়জোড় শুরু করেছিলেন ওঁর শিষ্যরা। কালীপদ গুহরায় শুনে বললেন, ‘বৃথা। শ্রীঅরবিন্দ ততদিন ইহলোকে থাকবেন না।’
অরবিন্দের এক শিষ্য তর্ক তুলতে যোগীরাজ শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন তিরোধানের তারিখ লিখে কাগজটি মুড়ে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ‘রেখে দিন আপনার কাছে, এখন খুলবেন না, আপনার গুরুদেব গতায়ু হলে পর মিলিয়ে নেবেন।’
অরবিন্দের শিষ্য কাগজটি নিতে অসম্মত হলে কালীপদ গুহরায় সেটা তাঁর বন্ধু অমলেন্দু দাশকে ডেকে তাঁর জিম্মায় দেন।
বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দিলীপকুমার রায় লিখছেন, ‘১৯৫০ সালে ৫ ডিসেম্বরে শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক তিরোধানের পরে অমলেন্দু কাগজটি খুলে দেখেন তারিখটি লেখা আছে... ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫০।’
১৯৬৬ সালে চৌষট্টি বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন কালীপদ গুহরায়। তিনি কায়াসিদ্ধ ছিলেন। কায়াব্যুহ রচনা করতে পারতেন। এক শরীর ছেড়ে আরেক শরীরে অনায়াসে চলে যেতে পারতেন। একবার একখানি যাত্রীভর্তি বাস তাঁর শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। তিনি ব্যূহ রচনা করে বেঁচে যান।
কালীপদ গুহরায় মাঝে মাঝে ভক্ত বিভুপদ কীর্তিকে যাজ্ঞবল্ক আশ্রমের কথা শোনাতেন। এ কোনও লৌকিক স্থান নয়। জ্ঞানগঞ্জের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। স্থূলদেহে সেখানে কখনও প্রবেশ করা যায় না। যোগেশ্বররা একমাত্র পৌঁছতে পারেন।
সাংগ্রীলা ঘাঁটির তিনটি সাধনাকেন্দ্রর কথা অনেক যোগীবরই উল্লেখ করে গেছেন। প্রথম কেন্দ্র জ্ঞানগঞ্জ, দ্বিতীয়টি সিদ্ধবিজ্ঞান আশ্রম, আর তৃতীয় স্থলটি হল যোগসিদ্ধাশ্রম। প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা আচার্য ও নির্দেশক রয়েছেন। এঁরা সকলেই কালজয়ী সাধক... ভৌতিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরকে আলাদা করতে জানেন, আত্ম শরীরে সাধনা করেন আর সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ করেন, যে কারণে মুহূর্তে মাইল-মাইল রাস্তা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারেন তাঁরা। প্রয়োজন পড়লে থার্ড ডাইমেনশনে নিজেদের ভৌতিক শরীর দিয়েও প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলতে পারেন।
অরুণাচল প্রদেশের সীমানা থেকে তিব্বতের উত্তর-পূর্বের পশ্চিমাংশে অবস্থিত অঞ্চলটিই সাংগ্রিলা। পুরো এলাকাটি ভূ- শূন্য এবং বায়ু- শূন্য। ফোর্থ ডাইমেনশন দ্বারা প্রভাবিত। দেশ, কাল এবং নিমিত্তের ঊর্ধ্বে এই জায়গাটি মহাযোগীদের তপস্যার প্রভাবে সৃষ্ট। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়ামের সংযোগস্থল বলে জায়গাটিকে খালি চোখে আমরা দেখতে পাই না। কৃষ্ণসুড়ঙ্গের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে সাংগ্রিলা সংযুক্ত। ভূমি সংস্থানের মাধ্যমে যোগীরা হাজার হাজার বছর অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে এখানে বেঁচে থাকেন। থার্ড ডাইমেনশনের বাসিন্দা বলে আমাদের সেখানে যাওয়ার কোনও শারীরিক ক্ষমতা নেই। অক্সিজেনের অভাব বোধ হবে এগলেই।
এগারোটি সিদ্ধমঠ নিয়ে সাংগ্রিলা ঘাটি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে অলৌকিক ও রহস্যময় মঠটিরই নাম জ্ঞানগঞ্জ। ভারতের উত্তর দিকের শেষপ্রান্ত গাড়োয়াল হিমালয় এবং তিব্বতের মধ্যবর্তী এক তুষারক্ষেত্রের মধ্যে সিদ্ধাশ্রম জ্ঞানগঞ্জ অবস্থিত। যেখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের প্রবেশ করার এক্তিয়ারই নেই। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মাদের নজরে যদি পড়েন থার্ড ডাইমেনশনের কোনও সাধক, যোগী, তাঁকে তাঁরা পৃথিবী থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন অনায়াসে।
উত্তুঙ্গ হিমালয়ে অবস্থিত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব কথিত জ্ঞানগঞ্জ, মহাত্মা রাম ঠাকুরের বর্ণিত কৌশিকী আশ্রম, যোগীবর কালীপদ গুহরায়ের বলা যাজ্ঞবল্ক আশ্রম, আর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাইয়ের কথকতার দ্রোণগিরি... সাংগ্রিলারই অন্তর্ভুক্ত এগারোটি গুপ্ত মঠের প্রকাশ্য চারটি। নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও এখানকার কার্যপ্রণালী ও আদবকায়দা যে মূলত এক সেটি রাম ঠাকুরের বক্তব্যেই স্পষ্ট।
রাম ঠাকুর বললেন, ‘কৌশিকী পর্বতের উপর আশ্রম। শিলাময় জায়গা। কোনও বরফ নেই। শিলা ভেদ করে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্ম নিয়েছে।’
গোপীনাথ কবিরাজ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায় এই আশ্রম?’
ঠাকুর বললেন, ‘মানস সরোবর পেরিয়ে অনেক দূরের পথ।’
কবিরাজ মশাই বললেন, ‘বহু তীর্থযাত্রী সেখানে যান, কেউ আশ্রম দেখতে পান না কেন?’
রাম ঠাকুর বললেন, ‘দিব্য আশ্রম সহজে দেখা যায় না। মনের আসক্তি দূর হলে কায়াসাধনে সিদ্ধ গুরুদেব নিয়ে যেতে পারেন কোনও নির্বাচিত শিষ্যকে। দেহের সমস্ত পাশ, এমনকী বস্ত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করে কৌশিকী আশ্রম পৌঁছতে হয়।’
জ্ঞানগঞ্জ বলে তিব্বতে কোনও জায়গা নেই। ওটি ভারতীয় যোগীদের দেওয়া নামসংকেত, যার চূড়ান্ত অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানগঞ্জ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করার জায়গা। তিব্বতে বর্ডার টাউন আছে, যার নাম গীয়ানৎসে... বাংলা মানে করলে জ্ঞানগঞ্জ দাঁড়ায়।
বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন, ‘দুশো-তিনশো হতে হাজার বছরের লোকও জ্ঞানগঞ্জে বর্তমান আছেন। সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে অনেকেই আহার করেন না... তবে যাঁরা ততটা উৎকর্ষ লাভ করেননি তাঁরা সামান্য কিছু গ্রহণ করেন মাত্র।’
বিন্ধ্যাচল থেকে ষোলো মাইল দূরের এক আশ্রমের কথা বিশুদ্ধানন্দজি শিষ্য গোপীনাথ মশাইকে বলেছেন। অনেক সাধু মহাত্মা সেখানে থাকেন। পাহাড়ে গুহার ভেতর শ্যামা ভৈরবী মাতার বাস। চারধারে খাড়া পাহাড়। হাতে ছুঁয়ে ফেলা দূরত্ব নিয়ে নীল মেঘেদের চলাচল। ঝর্ণা বয়ে চলেছে। সেসব পেরিয়ে আরেক আশ্রম। পাহাড়ি উপত্যকার একেবারে মাঝামাঝি জায়গা এটি। বড়সড় জায়গা জুড়ে আশ্রমভূমি। চারদিক পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলের পর জলে ভরা পরিখা। পরিখার ওপর দিয়ে ধাতুর সেতু। সেটি পেরিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়।
আশ্রমের ভেতর নানান শিক্ষাকেন্দ্র। বিজ্ঞানের একটি পৃথক বিভাগ আছে। যার আচার্য শ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরমহংস। গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন, ‘বিজ্ঞানের কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন এটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় জড়-বিজ্ঞান। বিশিষ্ট জ্ঞান- বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। তথাকথিত জড় ও চেতন। দুটোই বিজ্ঞানের বিষয়। সূর্য এর কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান আশ্রয় বলে জ্ঞানগঞ্জে একে সূর্যবিজ্ঞান বলা হচ্ছে। জাগতিক ও ব্যবহারিক যাবতীয় ব্যাপার সূর্যাধীন। স্বরূপোলব্ধি করতে হলে সৌরতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।’
জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমের মুখ্য আচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ পরমহংস। তিনি প্রাচীন আশ্রমটির তত্ত্বাবধায়ক। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন, ‘জায়গাটা বেশ পুরনো। এখানে ইন্দ্রভবন ছিল। জ্ঞানানন্দ স্বামী এটি সংস্কার করিয়ে নেন। আশ্রমে আছে যুবক ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী কুমারী মেয়েরা। আর আছে সূর্যবিজ্ঞান শেখার ছাত্ররা।’
বিশুদ্ধানন্দ ওঁর গুরু নিমানন্দ স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জে রইলেন আট-দশ দিন। তারপর গুরুদেব তাঁকে শ্রীশ্রীমৎ মহাতপার কাছে নিয়ে গেলেন। বারোশো বছর বয়স মহাতপার। মহাশক্তিশালী যোগীপুরুষ। জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমে তিনি থাকেন না।
দুর্গম এক পাহাড়ি গুহার ভেতর শ্যামা ভৈরবী একা থাকেন। তাঁর বয়সও হাজার পেরনো।
মহাতপা থাকেন আলাদা এক গুহায়। সেখানে ওঁর আরাধ্য রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আছে। এখানে কোনও ঘরবাড়ি নেই। তিনি গুহার ভেতর সর্বক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকেন।
মহাতপার গুরুমা খ্যাপা মাই থাকেন কিছু দূরের মনোহর তীর্থে। পাহাড় ঘেরা দুর্ভেদ্য এলাকা সব। হেঁটে চলা যাবে না। মহাতপা চলে যান তাঁরই সমসাময়িক বয়সের মা- গুরুকে দেখতে আকাশপথ ব্যবহার করে। বরফে ঢাকা এলাকার ভেতর আরও কয়েকটি মঠ আছে। সবগুলো রাজরাজেশ্বরী গুহাভূমির নির্দেশমতো চলে।
মহাতপা ঋষি জ্ঞানগঞ্জ সহ সমস্ত যোগশিক্ষার নানান গুপ্ত মঠের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। তাঁর প্রধান শিষ্য ভৃগুরাম স্বামী। তিনিও আকাশচারী।
বিশুদ্ধানন্দজির গুরুদেব নিমানন্দ সহ সকল যোগী পরস্পর পরস্পরের গুরুভাই। সকলের গুরুদেব মহর্ষি মহাতপা।
ভৃগুরাম যোগ শেখান। সূর্যবিজ্ঞানের শিক্ষা দেন শ্যামানন্দ পরমহংস। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাক্রম চলে। বিশুদ্ধানন্দের মহাতপার কাছে দীক্ষা হওয়ার পর শিক্ষা চলতে থাকে জ্ঞানগঞ্জের যোগীঋষিদের কাছে।
কাশীর আশ্রমে বিশুদ্ধানন্দজিকে এক শিষ্য প্রশ্ন করেন, ‘জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মারা আপনার সঙ্গে কোন ভাষাতে কথা বলতেন?’
স্বামীজি উত্তর দেন, ‘বাংলাতেই তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতেন।’
শিষ্যটি প্রশ্ন করেন, ‘তাঁরা সকলেই কি বাংলা ভাষা জানতেন?’
বিশুদ্ধানন্দ বললেন, ‘না জানলেই বা কী! ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে সব ভাষাতেই কথা বলা যায়। মূল যে ভাষা তা যোগীদের আয়ত্তে। যোগীরা দেবভূমিতে আরোহণ করে বক্তার অভিপ্রায় বুঝতে পারেন। অজ্ঞাত ভাষা বলার সময় শ্রোতার স্তরে নীচে নেমে আসেন ওঁরা। জ্ঞানগঞ্জের সাধুরা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা হিব্রুতে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রোতার মাতৃভাষায় তাঁদের হিব্রুভাষাগুলো স্বরনিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হয়ে শ্রোতাদের কানে গিয়ে পৌঁছাত।’
গোপীনাথ কবিরাজ বসে আছেন গুরুদেবের সম্মুখে। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বললেন, ‘পশ্চিম থেকে চিঠি এসেছে। চিঠিতে তোমাদের কথা-টথা আছে।’
পশ্চিম হল জ্ঞানগঞ্জের সংকেত। অনধিকারীরা সামনে থাকলে কাশীর আশ্রমে এমন সংকেতে কথা চলত। ১৯২৬ সাল... জ্ঞানগঞ্জের আচার্য উমানন্দ স্বামীর চিঠি এল। গোপীনাথ দেখলেন চিঠির গায়ে জ্ঞানগঞ্জের মোহর। নাগরি লিপিতে লেখা, ‘পঞ্জাব আশ্রম।’ ভাবলেন, না-থাকা জায়গার নামে আসা খামের ওপর পোস্টাপিসের মোহর পড়ে কী করে!
একদিন দেখলেন লেন্স নিয়ে বসেছেন বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব। বড় বড় ওষুধের শিশিগুলো শূন্যমার্গে ভেসে ভেসে আসছে। গুরুদেব ভৈরবী মায়েদের কাপড় কিনেছেন। সেসব শূন্যমার্গে চলেছে জ্ঞানগঞ্জে। লেন্সে ফোকাস করে তিনি সাধারণ পাথরকে হীরক করে দিলেন। ময়দার লেচিগুলোকে চমচমের আকার দিয়ে পাতায় মুড়ে রোদে ধরে লেন্সে ফোকাস করে তৈরি করলেন চমচম। একটুকরো নীল কাগজে গুরুদেব একটু তুলো রেখে কাগজ ও তুলোর মধ্যে ভিক্টু মাতার হাতের মাপের গোলাকৃতি তামার সূক্ষ্ম তার স্থাপন করলেন। একটি লেন্সের সাহায্যে একটু দূর থেকে তুলোর উপর অল্প রোদ ফেলা হল। এক- দু’মিনিট পর সোনার হাঙ্গরমুখো রুলি তৈরি হল। স্যাকরার দোকানে নিয়ে গেলে দোকানি বলল, ‘খাঁটি সোনা।’
কাশীর হনুমান ঘাটের কাছে দিলীপগঞ্জের দোতলা বাড়িতে বসে গোপীনাথ কবিরাজ পড়ে চলেছেন জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মাদের লেখা চিঠিপত্রগুলো। চিঠিও আসতে দেখলেন তিনি আশ্রমের ঘরে শূন্যমার্গে ভেসে-ভেসেই। অনেক যত্নে গুরুদেবের কাছে আসা চিঠিগুলো তিনি রেখে দিতেন নিজের জিম্মায়। গুরুদেব বললেন, ‘কেন ব্যস্ত হও?’
চব্বিশ বছর পর বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব অনুমতি দিলেন জ্ঞানগঞ্জের চিঠি প্রকাশ করতে। গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশ পাচ্ছে কল্যাণ পত্রিকা। গোপীনাথজি জ্ঞানগঞ্জের বিবৃতি দিলেন। ভৌগোলিক সীমার বাইরে থাকা এ স্থানের প্রকাশ ঘটল ভারতীয় অধ্যাত্মমণ্ডলে।
ভারতের উচ্চকোটির মহাত্মারা জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সাধক রামদাস কাঠিয়াবাবা কৈলাস- মানস সরোবরে তীর্থ পরিদর্শন কালে জ্ঞানগঞ্জে গিয়েছিলেন। রাম ঠাকুর ও কালীপদ গুহরায়ের গুরুদেব অনঙ্গদেবই ছিলেন জ্ঞানগঞ্জের ভৃগুরাম স্বামী। জ্ঞানগঞ্জের কাছে গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট যোগী গম্ভীরনাথজির যোগাসন ছিল। গম্ভীরনাথজিরই শিষ্য হলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শিবকল্প যোগী স্বামী প্রণবানন্দ।
জেমস হিল্টন একজন ইংরেজ লেখক। তাঁর লেখা কল্পলৌকিক উপন্যাস ‘Lost Horizon’ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এই বইতে হিল্টন ভারতের এমন কিছু রহস্যময় ঘাটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে মানুষ শত শত বছর ধরে বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছেন যোগ সাধনার মাধ্যমে। তাঁদের কারও শরীরেই বয়সের ছাপ পড়েনি। যোগ সাধনার মাধ্যমে পাঁচশো-ছশো বছর ধরে শরীরে থাকা সাংগ্রিলার সাধুদের কথা হিল্টন গোচরে আনার পর তাঁর বইয়ে দেওয়া ভারত-তিব্বত-ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে দেশ-বিদেশের অনুসন্ধানকারী দল সাংগ্রিলা ঘাঁটির খোঁজে আসতে থাকে। কিন্তু কোনও দলই সফল হয়নি সাধুদের ডেরা খোঁজার ক্ষেত্রে। অনেক অভিযাত্রী অনুসন্ধান করতে-করতেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন, যাঁদের কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।
ষোলো বছরের ঘর-পালানো একটি ছেলে তিব্বত যায় সাধুদের দলের সঙ্গে, গ্যাংটক থেকে লাসা, ব্রহ্মপুত্র, কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে ঘুরে সে ফেরে লিপু লেক নৈনিতাল হয়ে। ১৯৫৬ সালের তিব্বত যাত্রাতে পুণ্য সঙ্গমস্থল নানগুং নদী যেখানে মিলেছে পুণ্যস্রোত ব্রহ্মপুত্রতে, তার অনতিদূরে রহস্যময় তান্ত্রিক পীঠস্থান ইউংদ্রুলিং, সেখানে তখন কালচারাল রেভোল্যুশনের নামে চীন প্রলয়ের ধ্বংসলীলা চালায়নি, সেখানে এক গুহার ভেতর ঘর-পালানো ছেলেটি দেখা পায় এক তান্ত্রিক যোগীপুরুষের। তাঁর পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে ছেলেটি কৈলাসখণ্ডে মানস সরোবরের ধারে তান্ত্রিক যোগীর কাছে পেল একদিন দীক্ষা। ঘর পালানো ছেলেটি পরবর্তী সময়ে পরিণত হল ভূ-পর্যটকে।
২০০৭ সালে ভূ-পর্যটক বিমল দে ফের গেলেন ঐতিহ্যময় তিব্বত তীর্থে তান্ত্রিকগুরুর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে তিব্বতিদের জীবনযাত্রার বিরাট পরিবর্তন। তান্ত্রিকগুরু কৈলাসবাবাকে খুঁজতে খুঁজতে বিমল দে পৌঁছে গেলেন তিব্বতের রহস্যময় নারী-মঠ ওসেরলিং গুম্ফায়, সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন সন্ন্যাসিনী আছেন। ধুনির সামনে বসে আছেন মহাযোগীনী ভৈরবী মা। প্রচুর বয়স তাঁর, কিন্তু অতি সুন্দরী যুবতীর মুখ মায়ের। মাথার জটাকে গুছিয়ে কোলের ওপর রেখে লাল রঙের চাদরে ঢাকা শরীরে সিদ্ধাসনে বসে রয়েছেন ভৈরবী মা।
বিমল দে বসে রয়েছেন অপরূপ মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে। তাঁর মুখ থেকে কোনও কথা বের হচ্ছে না। ভৈরবী যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে এখানে টেনে এনেছেন।
এক সন্ন্যাসিনী এসে মায়ের হাতে একটি পাত্র ধরাতে ভৈরবী মা সেটি বিমলবাবুর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, ‘পি - লে বেটা।’
‘আশ্চর্য! তিনি হিন্দি বলেন!’ লম্বা কাচের গ্লাস হাতে ধরে বিমল দে ভাবছেন।
সেবিকা সন্ন্যাসিনী বললেন, ‘মা জানেন আপনি কবে তিব্বতে এসেছেন, কেন এসেছেন।’
পরিষ্কার হিন্দিতে ভৈরবী মা বললেন, ‘আমি অধিকাংশ সময় হিন্দুস্থানে থাকি, ওখানে আমার অনেক ছেলেমেয়ে আছে, তারা ডাকে, যেতেই হয়। মহাগুরু বুদ্ধাবতার গুরু রিমপোচ্চে নির্বিঘ্নে সাধনার জন্য হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে মোট ষোলোটি গুপ্ত গুহা-গ্রাম তৈরি করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে হিমালয় ডিঙিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে নেমেছে, সেখানে এখনও অনেক মৌনী গুহা আছে, বুঝলে বাবা? তুমি এখান থেকে কৈলাসে যাও, প্রথমে চুরাশি সিদ্ধ শ্মশান। শ্মশানে গিয়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসবে। তারপর শিবস্থান। ওখানে সূক্ষ্ম শরীরে অনেক যোগী যোগীনীরা আছেন, তাঁরাই তোমাকে পরিষ্কার করে বলে দেবেন তোমার দীক্ষাগুরু কৈলাসবাবা এখন কোথায় আছেন।’
বিমল দে লিখছেন, ‘এক আশ্চর্য পাওয়া জ্ঞানগঞ্জ রি-পুক মঠের ভৈরবী মাতাজি... এক রহস্যময়ী মা... অপরূপা নারী। তাঁর নির্দেশ পেয়ে গেলাম কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর খণ্ডে। সে যাত্রায় কৈলাস পরিক্রমার উদ্দেশে নয়, উদ্দেশ্য ছিল চুরাশি মহাসিদ্ধ যোগী শ্মশানে রাত কাটানো, মাতাজির দ্বিতীয় আদেশ ছিল... শিবস্থল থেকে পাপক্ষয় পাথরগুহা অতিক্রম করা... মাতাজিই আমাকে পার করিয়েছিলেন সেই ভয়াবহ সুড়ঙ্গ পথ, তাঁর কৃপায় অসাধ্য সাধন হয়েছে। ভৈরবী মাতা জ্ঞানগঞ্জের এক অলৌকিক নারী। লামা, সাধু, জ্ঞানী ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে রাস্তার ভিখারি পর্যন্ত সবাই তাঁর নাম শুনেছে। স্থানীয় লোকেরা বিপদে পড়লে তাঁকেই ডাকে, অথচ খুব কম লোকেই তাঁর দর্শন পেয়েছে।’
১৯৫৬ সালে তিব্বতের লাংবোনা গুহার যোগীপুরুষ, দীক্ষাগুরু কৈলাসবাবাকে শেষে ভূ-পর্যটক বিমল দে খুঁজে পেলেন অমরকণ্টকের বরফানি ধামে।
বরফানি বাবা বসে আছেন। এখানে সকলের কাছে তিনি দাদাজি। বয়স দুশো পেরিয়ে গেছে।
বিমল দে বললেন, ‘কৈলাসখণ্ডে লাংবোনা গোম্ফায়, গুহার সঙ্গেই ছিল আপনার ঘর, যেদিন দেখলাম সেদিন থেকে আপনি আমার কৈলাসবাবা।’ বলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন বাবার শ্রীচরণে।
বরফানি দাদাজি বললেন, ‘ওখান থেকে তুমি পারখা হয়ে চলে গেলে কৈলাস পরিক্রমায়। তারপর আবার তুমি এলে মানস সরোবরের ধারে চিউ গোম্ফাতে।’
দাদাজি সোজা হয়ে চেয়ারে বসে কথাগুলো বলছেন। উপস্থিত ভক্তেরা কৌতূহলী হয়ে শুনছেন কৈলাসবাবার কথা।
বিমল দে লিখছেন, ‘দীর্ঘ তিপান্ন বছর আগেকার সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ তাঁর মুখে শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এই দীর্ঘ তিপান্ন বছর ধরে তিনি তো হাজার হাজার ভক্তের কথা শুনেছেন, তিনি তো সাক্ষাৎ ইতিহাস। আমার মতো এক ছোট্ট মানুষের সামান্য ঘটনা তিনি কী করে মনে রেখেছেন? বুঝলাম, আমি তাঁকে ধরে রেখেছি আর তিনিও আমাকে ছাড়েননি। তিনি লালসুতো দিয়ে আমার হাতে আড়াই পাকের বন্ধন পরিয়ে দিয়ে ফের গুরু-শিষ্য সম্পর্কে বাঁধলেন।’
কৈলাসবাবা উপস্থিত ভক্তদের বললেন, ‘জানো বাবা, কৈলাসে অনেকেই আমাকে কৈলাসবাবা ডাকত... এই বাবাকে আমার গুহাতেই কয়েকদিন রেখেছিলাম। ওকে সব শিখিয়ে তারপর পাঠিয়েছিলাম পরিক্রমায়। ও আমার কৈলাসখণ্ডের শিষ্য। আমি কৈলাসে ছিলাম আরও ছ-সাত বছর, তারপর চীনারা আর থাকতে দিল না। আমি চলে এলাম, আমার অনেক পরিচিত যোগীরাও চলে আসে।’
কৈলাস পর্বতের উচ্চতা ৬ হাজার ৬৩৮ মিটার। এভারেস্টের থেকে ২ হাজার ২০০ মিটার কম হলেও এখনও পর্যন্ত পর্বতারোহীরা এর চূড়াতে উঠতে পারেননি। কৈলাসে যখন কোনও পর্বতারোহী ওঠার চেষ্টা করেন, কিছুটা উঁচুতে যাওয়ার পরই প্রকৃতি বিরূপ হতে শুরু করে। ওঠে ঝড়, তেড়ে আসে পাথরের টুকরো, পা পিছলা?
এখনকার দর
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৪.১৩ টাকা | ৮৫.৮৭ টাকা |
| পাউন্ড | ১০৪.২৭ টাকা | ১০৭.৯৮ টাকা |
| ইউরো | ৮৬.৪২ টাকা | ৮৯.৭৮ টাকা |
*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে