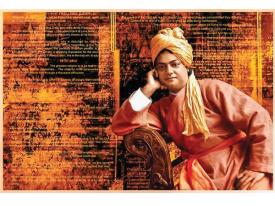কলকাতা, বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, ১ মাঘ ১৪৩১
বর্ষা এল, মাছ ধরতে চল
অমিতাভ পুরকায়স্থ

শ্যামপুকুরের কৃষ্ণকুমার মিত্রের গাছগাছালি ঘেরা পুকুর সহ নিরিবিলি এক বাগানবাড়ি ছিল দমদমে। বাগানের মালিকের নিমন্ত্রণেই সেখানে একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সহ কয়েকজন শিল্পী সাহিত্যিক বন্ধু। পূর্ণচন্দ্র ছাড়া বাকিদের মাছ ধরার নেশা ছিল। তাঁরা চটপট জায়গা বেছে ছিপ ফেলে বসে গেলেন। হেমেন্দ্রকুমারের বঁড়শিতে প্রথম শিকার পড়ল। অনেক খেলিয়ে তিনি ইয়াব্বড় এক কাতলা পাড়ে তুললেন। তার মধ্যে বাগানের ম্যানেজারবাবু আর গোমস্তা গিয়ে লোকজন ডেকে এনেছেন। তারা ফিতে, দাঁড়িপাল্লা, খাতা, পেন্সিল নিয়ে হাজির। হেমেন্দ্রকুমার ছিপ ছেড়ে দিতেই ম্যানেজারবাবুর লোকরা মাছের লম্বা আর বেড় মাপতে লেগে গেল। লম্বা চার ফুট, বেড় ছত্রিশ ইঞ্চি। ওজন সাড়ে বারো সের। সব কিছু খাতায় লেখা হল। মাছের নাকে একটা পেতলের নথ পরানো ছিল। তাতে খুদে একটা পেতলের টিকিট। গোমস্তা খাতায় নোট করালেন— ৭৩ নং। তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাছটাকে ঠেলে ঝুপ করে আবার জলে ফেলে দেওয়া হল। মাছুড়েদের চক্ষুস্থির!
অন্যদিকে ম্যানেজারবাবু মুখে মুখে হিসেব করলেন— সাড়ে বারোক্কে ছয় আনা হল গিয়ে ছয় বারোং বাহাত্তর আর তিন। মনিব্যাগ খুলে চার টাকা এগারো আনা এগিয়ে দিলেন। সঙ্গে অমায়িক পরামর্শ— ‘বাড়ি যাবার পথে ভালো দেখে একটা কিনে নিয়ে যাবেন, কেমন?’
বাড়িয়ে ধরা টাকার দিকে অতিথিদের ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি থেকে পোড় খাওয়া ম্যানেজার আন্দাজ করলেন, কোথাও যেন ভুল হচ্ছে। তাই বোঝাতে দেরি করলেন না। ‘আরে ছি! ছি! কর্তাবাবু বোধহয় বলতে ভুলে গেছেন যে, আমাদের এখানকার নিয়ম, মাছ ধরা হবে, কিন্তু মারা হবে না। আনন্দটা তো ধরাতেই, মারাতে তো আর নয়। আমরা এই খাতায় মাছদের নম্বর দেখে, ওদের বাড়ের একটা হিসাব পাই।’
লীলা মজুমদারের ‘খেরোর খাতা’ বইতে এমন অহিংস মাছ ধরার গল্প শুনে ‘মৎস্য মারিব খাইব সুখে’ প্রবাদের সত্যতা নিয়ে কারও মনে সংশয়ের উদ্রেক হওয়া ঠিক নয়। কারণ ছিপে খেলিয়ে মাছ ধরে সেই শিকার বাড়ি নিয়ে এসে সৎকার, মানে ভাজা বা ঝোল রান্নার জন্য হস্তান্তর করার তৃপ্তির আর কোনও জুড়ি নেই বাঙালি মাছ শিকারির কাছে।
গত শতকের প্রথম দিকের সময়কাল থেকে যতীন্দ্রমোহন দত্ত সেই রকমই এক গল্প শুনিয়েছেন তাঁর যম দত্তের ডায়েরিতে। তবে শেষে সামান্য টুইস্ট যোগ করেন। বিটি রোড ধরে বারাকপুর যাওয়ার পথেই সুখচর গির্জা মোড়ের লাগোয়া এলাকাটা একসময় আলো করে থাকত পাইকপাড়ার সিংহদের রাজবাড়ি। বাড়ি না বলে একটা ছোটখাট শহর বলাই ভালো। সাড়ে তিনশো ঘর নিয়ে তৈরি কমপ্লেক্সের মধ্যে এক বিশাল পুকুর ছিল। সেই পুকুরে প্রতি বছর গুনতি করে নদীর পোনা ছাড়া হতো। রাজারা পরম বৈষ্ণব হওয়ায় নিজেরা মাছ মারতেন না। তবে এলাকার লোকজনকে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হতো। শুধু অনুমতি নয়, বিকেলে মেছোদের রীতিমতো জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। মাছের বাড়-বৃদ্ধির হিসেব করার উদ্দেশ্যে সেখানেও রাজবাড়ির কর্মচারীরা ধরা পড়া মাছ ওজন করে নোট রাখতেন। এখানে অবশ্য মাছ বাড়ি যাওয়ার অনুমতি ছিল। সন্ধের সময় মৎস্য শিকারিরা বাড়ি যাওয়ার সময় ঘটত আসল মজা। যে যত সের মাছ ধরেছে, তাকে তত পোয়া রাজবাড়ির ঘানির খাঁটি সর্ষের তেল দেওয়া হতো মাছ ভাজার জন্য। রাজারা মনে করতেন যে, রাজবাড়ির পুকুরের মাছ ভাজতে সাধারণ তেলের ব্যবহার একদমই উচিত নয়!
শৌখিন মৎস্য শিকারিদের বঁড়শির বাক্স ছিল এক দেখার মতো জিনিস। ছোট ছোট টিনের খোপে থাকত নানা রকমের বঁড়শি। তিন-চারটি ডালায় ভাগ করা প্রতিটি খোপে টিকিট মারা থাকত— ‘রুই মাছের বঁড়শি’, ‘পুঁটি মাছের বঁড়শি’ ইত্যাদি। বঁড়শিরও ছিল নানা আকার ও প্রকারভেদ। যেমন হাতে কাটা বঁড়শি, করাত কাটা বঁড়শি, পান দেওয়া বঁড়শি, ডাবল পান দেওয়া বঁড়শি ইত্যাদি। কালবোস মাছের বঁড়শি একটু আলাদা রকমের। সেটাতে সাধারণ বঁড়শির মতো কার্ভেচার থাকত না। টোপের আড়ালে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা হয়। মাছ টোপ গিলে নিয়েই বঁড়শিতে আটকাবে। তাই টোপ তৈরিতে মাছের পছন্দের খাবার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। সেই জন্য প্রজাতি ভেদে মাছের টোপও তৈরি হতো বিভিন্ন উপকরণ ও অনুপাতে। বলা বাহুল্য, ভালো টোপ তৈরিও ছিল একটি বিশেষ শিল্প।
বঁড়শির আর টোপের পর মাছের ‘চার’ বা মশলা নিয়ে খানিক বলতেই হয়। ‘চার’ থেকে নির্গত গন্ধের আকর্ষণে মাছ টোপের কাছাকাছি আসে। মেথি, লতাকস্তুরী, জটামানসী, খলভাজার মতো উপাদান থেকে হাঁড়িয়ে মদ, পিঁপড়ের বাসি ডিম ইত্যাদি নানা জিনিস দিয়ে অভিজ্ঞ মেছোরা চার বানাতেন। অবশ্যই সেই ফর্মুলা থাকত টপ সিক্রেট। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিন ভাই— সারদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন ও কুলদারঞ্জনের ছিল মাছ ধরার নেশা। লীলা মজুমদার শুনেছিলেন যে, জলের ওপর বড় জ্যাঠা, অর্থাৎ সারদারঞ্জনের তৈরি একটু ভালো চার ছড়িয়ে দিলেই পুকুরের চারকোনা থেকে মাছ ছুটে আসত। উনি একটি চার বানিয়ে নাম দিয়েছিলেন— ‘ইধার আও’! সেই চারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার আরও একটি চার বানিয়ে নাম দেন— ‘উধর মৎ যাও’! তবে সারদারঞ্জন ও তাঁর মতো দিগগজ মৎস্য শিকারিরা মনে করতেন যে মশলা দিয়ে ভুলিয়ে, কি আলো দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে মাছ ধরা খুব স্পোর্টিং নয়।
বিখ্যাত রায় পরিবার ছাড়াও মৎস্য শিকারের নেশায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য থেকে শচীন দেববর্মণের মতো বহু খ্যাতিমান বাঙালিও ডুবেছিলেন একসময়। এঁরা দু’জন আবার ছিলেন মাছ ধরার পার্টনার। পরবর্তী সময়ে স্ত্রীর অসুস্থতার সময় মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে শচীন কর্তা পেসেন্স খেলার পাশাপাশি মাছ ধরাও সমান তালে চালিয়ে গিয়েছেন।
তবে মাছ ধরার নেশা যে, একমাত্র বাঙালি বাবুদের একচেটিয়া ছিল, এমন ভাবা ঠিক হবে না। সাহেবরাও রীতিমতো ডুবেছিলেন মাছ ধরার নেশায়। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর শ্বেতাঙ্গ কর্মীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল এই খেলা। মাছ ধরার ক্ষেত্রেও কলকাতা ছিল পুরো ভারতের রাজধানী। ভালো ছিপ, সুতো আর আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের খোঁজে সারা ভারত থেকে এসে সাহেবরা ঢুঁ মারতেন কলকাতার ডি এন বিশ্বাস অ্যান্ড কোং, রদা অ্যান্ড কোং অথবা ম্যান্টন অ্যান্ড কোং-এর মতো সংস্থায়। শিকারের গুলি বন্দুক যে দোকানে পাওয়া যেত, সেখানেই বিক্রি হতো মাছ ধরার সমস্ত সরঞ্জাম। আসলেই দুটোই যে স্পোর্টস!
উনিশ শতকে ভারতে শৌখিন মাছ ধরার নানা খবর নিয়ে প্রথম প্রকাশিত বই লিখতে গিয়ে হেনরি সুলেভান টমাসকে বারবার ফিরে আসতে হয়েছে কলকাতার প্রসঙ্গে। টমাস সাহেব কলকাতার নিকটবর্তী এক মাছ ধরার পুকুরের দুর্দান্ত রক্ষণাবেক্ষণ দেখে তার মালিক জনৈক বাবুর খুব প্রশংসা করায় ভদ্রলোক সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন যে, বাঙালির স্টেক বা কাটলেট— সব কিছুর উৎসই এই পুকুর। সুতরাং যত্ন তো করতেই হবে!
গ্রীষ্মের জ্বালাপোড়া শেষে বঙ্গদেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে টিপ টিপ, টাপুর টুপুর শুরু হয়ে গেলেই শহর-গ্রাম-মফস্সলে মাছ শিকারিদের মধ্যে শুরু যায় হয়ে কর্মচাঞ্চল্য। শিয়ালদা বা হাতিবাগানের মতো পুরনো বাজারে মাছ ধরার সরঞ্জামের দোকানগুলি ঝিম ভাব কাটিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে নতুন ছিপ, বঁড়শি, সুতো আর নানা উপকরণের খোঁজ খবরের আদানপ্রদানে। আমাদের অজান্তেই আজও প্রকৃতির নিয়মেই এসে পড়ে মাছ শিকারের মরশুম।
অন্যদিকে ম্যানেজারবাবু মুখে মুখে হিসেব করলেন— সাড়ে বারোক্কে ছয় আনা হল গিয়ে ছয় বারোং বাহাত্তর আর তিন। মনিব্যাগ খুলে চার টাকা এগারো আনা এগিয়ে দিলেন। সঙ্গে অমায়িক পরামর্শ— ‘বাড়ি যাবার পথে ভালো দেখে একটা কিনে নিয়ে যাবেন, কেমন?’
বাড়িয়ে ধরা টাকার দিকে অতিথিদের ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি থেকে পোড় খাওয়া ম্যানেজার আন্দাজ করলেন, কোথাও যেন ভুল হচ্ছে। তাই বোঝাতে দেরি করলেন না। ‘আরে ছি! ছি! কর্তাবাবু বোধহয় বলতে ভুলে গেছেন যে, আমাদের এখানকার নিয়ম, মাছ ধরা হবে, কিন্তু মারা হবে না। আনন্দটা তো ধরাতেই, মারাতে তো আর নয়। আমরা এই খাতায় মাছদের নম্বর দেখে, ওদের বাড়ের একটা হিসাব পাই।’
লীলা মজুমদারের ‘খেরোর খাতা’ বইতে এমন অহিংস মাছ ধরার গল্প শুনে ‘মৎস্য মারিব খাইব সুখে’ প্রবাদের সত্যতা নিয়ে কারও মনে সংশয়ের উদ্রেক হওয়া ঠিক নয়। কারণ ছিপে খেলিয়ে মাছ ধরে সেই শিকার বাড়ি নিয়ে এসে সৎকার, মানে ভাজা বা ঝোল রান্নার জন্য হস্তান্তর করার তৃপ্তির আর কোনও জুড়ি নেই বাঙালি মাছ শিকারির কাছে।
গত শতকের প্রথম দিকের সময়কাল থেকে যতীন্দ্রমোহন দত্ত সেই রকমই এক গল্প শুনিয়েছেন তাঁর যম দত্তের ডায়েরিতে। তবে শেষে সামান্য টুইস্ট যোগ করেন। বিটি রোড ধরে বারাকপুর যাওয়ার পথেই সুখচর গির্জা মোড়ের লাগোয়া এলাকাটা একসময় আলো করে থাকত পাইকপাড়ার সিংহদের রাজবাড়ি। বাড়ি না বলে একটা ছোটখাট শহর বলাই ভালো। সাড়ে তিনশো ঘর নিয়ে তৈরি কমপ্লেক্সের মধ্যে এক বিশাল পুকুর ছিল। সেই পুকুরে প্রতি বছর গুনতি করে নদীর পোনা ছাড়া হতো। রাজারা পরম বৈষ্ণব হওয়ায় নিজেরা মাছ মারতেন না। তবে এলাকার লোকজনকে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হতো। শুধু অনুমতি নয়, বিকেলে মেছোদের রীতিমতো জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। মাছের বাড়-বৃদ্ধির হিসেব করার উদ্দেশ্যে সেখানেও রাজবাড়ির কর্মচারীরা ধরা পড়া মাছ ওজন করে নোট রাখতেন। এখানে অবশ্য মাছ বাড়ি যাওয়ার অনুমতি ছিল। সন্ধের সময় মৎস্য শিকারিরা বাড়ি যাওয়ার সময় ঘটত আসল মজা। যে যত সের মাছ ধরেছে, তাকে তত পোয়া রাজবাড়ির ঘানির খাঁটি সর্ষের তেল দেওয়া হতো মাছ ভাজার জন্য। রাজারা মনে করতেন যে, রাজবাড়ির পুকুরের মাছ ভাজতে সাধারণ তেলের ব্যবহার একদমই উচিত নয়!
শৌখিন মৎস্য শিকারিদের বঁড়শির বাক্স ছিল এক দেখার মতো জিনিস। ছোট ছোট টিনের খোপে থাকত নানা রকমের বঁড়শি। তিন-চারটি ডালায় ভাগ করা প্রতিটি খোপে টিকিট মারা থাকত— ‘রুই মাছের বঁড়শি’, ‘পুঁটি মাছের বঁড়শি’ ইত্যাদি। বঁড়শিরও ছিল নানা আকার ও প্রকারভেদ। যেমন হাতে কাটা বঁড়শি, করাত কাটা বঁড়শি, পান দেওয়া বঁড়শি, ডাবল পান দেওয়া বঁড়শি ইত্যাদি। কালবোস মাছের বঁড়শি একটু আলাদা রকমের। সেটাতে সাধারণ বঁড়শির মতো কার্ভেচার থাকত না। টোপের আড়ালে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা হয়। মাছ টোপ গিলে নিয়েই বঁড়শিতে আটকাবে। তাই টোপ তৈরিতে মাছের পছন্দের খাবার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। সেই জন্য প্রজাতি ভেদে মাছের টোপও তৈরি হতো বিভিন্ন উপকরণ ও অনুপাতে। বলা বাহুল্য, ভালো টোপ তৈরিও ছিল একটি বিশেষ শিল্প।
বঁড়শির আর টোপের পর মাছের ‘চার’ বা মশলা নিয়ে খানিক বলতেই হয়। ‘চার’ থেকে নির্গত গন্ধের আকর্ষণে মাছ টোপের কাছাকাছি আসে। মেথি, লতাকস্তুরী, জটামানসী, খলভাজার মতো উপাদান থেকে হাঁড়িয়ে মদ, পিঁপড়ের বাসি ডিম ইত্যাদি নানা জিনিস দিয়ে অভিজ্ঞ মেছোরা চার বানাতেন। অবশ্যই সেই ফর্মুলা থাকত টপ সিক্রেট। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিন ভাই— সারদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন ও কুলদারঞ্জনের ছিল মাছ ধরার নেশা। লীলা মজুমদার শুনেছিলেন যে, জলের ওপর বড় জ্যাঠা, অর্থাৎ সারদারঞ্জনের তৈরি একটু ভালো চার ছড়িয়ে দিলেই পুকুরের চারকোনা থেকে মাছ ছুটে আসত। উনি একটি চার বানিয়ে নাম দিয়েছিলেন— ‘ইধার আও’! সেই চারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার আরও একটি চার বানিয়ে নাম দেন— ‘উধর মৎ যাও’! তবে সারদারঞ্জন ও তাঁর মতো দিগগজ মৎস্য শিকারিরা মনে করতেন যে মশলা দিয়ে ভুলিয়ে, কি আলো দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে মাছ ধরা খুব স্পোর্টিং নয়।
বিখ্যাত রায় পরিবার ছাড়াও মৎস্য শিকারের নেশায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য থেকে শচীন দেববর্মণের মতো বহু খ্যাতিমান বাঙালিও ডুবেছিলেন একসময়। এঁরা দু’জন আবার ছিলেন মাছ ধরার পার্টনার। পরবর্তী সময়ে স্ত্রীর অসুস্থতার সময় মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে শচীন কর্তা পেসেন্স খেলার পাশাপাশি মাছ ধরাও সমান তালে চালিয়ে গিয়েছেন।
তবে মাছ ধরার নেশা যে, একমাত্র বাঙালি বাবুদের একচেটিয়া ছিল, এমন ভাবা ঠিক হবে না। সাহেবরাও রীতিমতো ডুবেছিলেন মাছ ধরার নেশায়। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর শ্বেতাঙ্গ কর্মীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল এই খেলা। মাছ ধরার ক্ষেত্রেও কলকাতা ছিল পুরো ভারতের রাজধানী। ভালো ছিপ, সুতো আর আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের খোঁজে সারা ভারত থেকে এসে সাহেবরা ঢুঁ মারতেন কলকাতার ডি এন বিশ্বাস অ্যান্ড কোং, রদা অ্যান্ড কোং অথবা ম্যান্টন অ্যান্ড কোং-এর মতো সংস্থায়। শিকারের গুলি বন্দুক যে দোকানে পাওয়া যেত, সেখানেই বিক্রি হতো মাছ ধরার সমস্ত সরঞ্জাম। আসলেই দুটোই যে স্পোর্টস!
উনিশ শতকে ভারতে শৌখিন মাছ ধরার নানা খবর নিয়ে প্রথম প্রকাশিত বই লিখতে গিয়ে হেনরি সুলেভান টমাসকে বারবার ফিরে আসতে হয়েছে কলকাতার প্রসঙ্গে। টমাস সাহেব কলকাতার নিকটবর্তী এক মাছ ধরার পুকুরের দুর্দান্ত রক্ষণাবেক্ষণ দেখে তার মালিক জনৈক বাবুর খুব প্রশংসা করায় ভদ্রলোক সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন যে, বাঙালির স্টেক বা কাটলেট— সব কিছুর উৎসই এই পুকুর। সুতরাং যত্ন তো করতেই হবে!
গ্রীষ্মের জ্বালাপোড়া শেষে বঙ্গদেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে টিপ টিপ, টাপুর টুপুর শুরু হয়ে গেলেই শহর-গ্রাম-মফস্সলে মাছ শিকারিদের মধ্যে শুরু যায় হয়ে কর্মচাঞ্চল্য। শিয়ালদা বা হাতিবাগানের মতো পুরনো বাজারে মাছ ধরার সরঞ্জামের দোকানগুলি ঝিম ভাব কাটিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে নতুন ছিপ, বঁড়শি, সুতো আর নানা উপকরণের খোঁজ খবরের আদানপ্রদানে। আমাদের অজান্তেই আজও প্রকৃতির নিয়মেই এসে পড়ে মাছ শিকারের মরশুম।
এখনকার দর
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৫.৮৩ টাকা | ৮৭.৫৭ টাকা |
| পাউন্ড | ১০৪.০৫ টাকা | ১০৭.৭৪ টাকা |
| ইউরো | ৮৭.৩০ টাকা | ৯০.৬৫ টাকা |
*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে