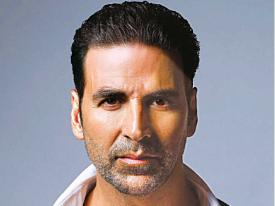প্রায় সম্পূর্ণ কাজে আকস্মিক বিঘ্ন আসতে পারে। কর্মে অধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা। ... বিশদ
তরুণ পুরোহিত প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বিগ্রহের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিনও কিন্তু তিনি সাধক ছিলেন না। তাঁর উপাস্য দেবী দুর্জ্ঞেয়া ভয়ঙ্করী, না কি আলোকময়ী হিতৈষিণী— এসব তাত্ত্বিক ভাবনা সেদিন তাঁর মনে জাগেনি। কালীবিগ্রহ দেখে সেদিন গদাধর অন্তত লালিত নিরবয়ব ঈশ্বরের এক মানবী রূপ খুঁজে পেয়েছিলেন। হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস নিয়ে বিগ্রহকে ‘মা’ বলে ডেকেছিলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়। জগজ্জন যাঁকে অনতিকালে চিনবে শ্রীরামকৃষ্ণ হিসেবে। তাঁর তপস্যার মধ্য দিয়েই বাঙালির কালীসাধনার অভিনব বেদ রচিত হয়েছিল।
দেবীপুজোয় গদাধরের কোনও পরিমিতিবোধ ছিল না। বড় বিচিত্র তাঁর পুজো। দেবীকে প্রসন্না করতে কখনও গান গেয়ে উঠেছেন। কখনও হৃদয়ের ব্যাকুলতায় মা-কে বলছেন, ‘মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, সুখভোগ কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে মা’। প্রার্থনা করতে করতে চোখের জলে বুক ভেসে যেত। মুখ লাল হয়ে উঠত। পুজোয় বসে ভক্তির প্রাবল্যে তিনি যে কী করবেন কেউ জানে না। তিনিও নন। ফুল-বেলপাতার অর্ঘ নিজের পায়ে ঠেকিয়ে দেবীকে নিবেদন করেছেন। পুজোসন ছেড়ে মা-র কাছে গিয়ে তাঁর চিবুক ধরে আদর করেছেন। পরিহাস করেছেন। হাত ধরে নেচেছেন। পুজো না করে ভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন কিংবা নিবেদিত ভোগ নিজের হাতে দেবীকে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়েছেন অথবা নৈবেদ্যর খানিকটা নিজেই খেয়ে উচ্ছিষ্টটা দেবীকে খেতে অনুনয় করেছেন। আবার মাতৃ আদেশ ভেবে মা-র খাটে খানিকক্ষণ শুয়ে থেকেছেন। দিনের পর দিন মায়ের আহার-বিহারে, শয়ন-উত্থানে মায়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জগন্মাতার অস্তিত্ব অনুভব করছিলেন। জননীও নিজের দেহগন্ধে, নিঃশ্বাসবায়ুর উষ্ণতায়, কণ্ঠস্বরের অনুরণনে, স্মিত হাসির মাধুর্যে, নূপুরের রিনঝিন শব্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে আবিষ্ট, সন্মোহিত করে ফেলেছিলেন। মায়ের মুখ তখনও তিনি দেখতে পাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর উপস্থিতির সমস্ত লক্ষণ তিনি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছিলেন। ফলে তাঁর হৃদয়ে মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।
তন্ত্র সাধনা, বৈদান্তিক সাধনার সব রকম সাধনার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। নানা ভাবে নানা পদ্ধতিতে ঈশ্বরের স্বরূপ দশর্নই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম সব পথেই তিনি ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য সাধনা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী পুরুষ কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন, ‘তিনি ধর্মসাধনের জন্য যত ক্লেশ পেয়েছেন আর কোনও সাধক এত ক্লেশ সহ্য করেননি।’ দেবী ভবতারিণীর পাষাণপ্রতিমাকে ‘মা মা’ বলে আপন খেয়ালে তিনি কথা বলতেন। কখনও তাঁর ‘ভাব-সমাধি’ হতো। রামকৃষ্ণের সেই ভাবসমাধি মুহূর্তে মনে করা হতো তিনি স্বয়ং মা-কে প্রত্যক্ষ করছেন। ‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ গ্রন্থে শ্রীম জানিয়েছেন, ঠাকুর বলতেন, ‘এমনি মহামায়ার মায়া/ রেখেছ কী কুহক করে/ ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য/ জীবে কি তা জানতে পারে।’ তাঁর লক্ষ্য: ধর্মসাধনার গভীরে ডুব দিয়ে তুলে আনবেন অনুভবজনিত মণিমাণিক্য। সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই রোমা রল্যাঁর অভিব্যক্তি: ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভারতবর্ষের দু’হাজার বছরের সাধনার ঘনীভূত রূপ।’
শ্রীরামকৃষ্ণ যখনই বাহ্যসংজ্ঞা হারাতেন, অনুভব করতেন, মা-র অভয়মূর্তি সামনে এসে তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হয়েছিল, মা তাঁর উপর ভর করেছেন। ধ্যানে এখন শুধু মা-র অনিন্দ্যসুন্দর হাত-পা-মুখ নয়, পরিপূর্ণ বরাভয়করা চিন্ময়ীমূর্তির নিত্য আবির্ভাব। শুধু চোখ বন্ধ করে কেন, চোখ খুললেও তিনি আছেন। সকালে ফুল তোলা থেকে রাতে শয়ন দেওয়া পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সব কাজেই কালী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন। মন্দিরের পাষাণমূর্তিতে এখন শুধু তাঁর আবির্ভাব নয়, এখন তিনি চিন্ময়ীরূপে স্বয়ং মন্দিরে বিরাজ করেন। কালীর নিত্য সান্নিধ্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় দিনে মন্দিরে এবং রাতে পঞ্চবটীতে আরও আকুল হয়ে প্রার্থনা করতেন। কেঁদে কেঁদে মা-কে ডাকতেন, ভালোবাসা প্রকাশ করতেন, কখনও-বা ধৈর্য হারিয়ে মুখ করতেন মাকেই। এমনই একদিন রামকৃষ্ণের দুই চোখ অশ্রুধারায় সিক্ত, পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা সহনশক্তির প্রান্তসীমায় পৌঁছলো— শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষা। হঠাৎ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক অনির্বচনীয় আলোর উদ্ভাস। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, ‘ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! —যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!... অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূত জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!’
কালীঘরে মা দেখিয়ে দিলেন— সব চিন্ময়। প্রতিমা, বেদি, কোশাকুশি, চৌকাট, মার্বেল পাথর, মানুষ, জীবজন্তু— সব চিন্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মধ্যেও কালীর দুর্বার উপস্থিতি অনুভব করলেন। তিনিই হয়ে উঠলেন কালী। উপলব্ধি হল সকল ধর্মের উদ্দেশ্য এক ঈশ্বরপ্রাপ্তি। তাই সকল ধর্মই সমান ভাবে সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধর্ম কখনওই আচারসর্বস্ব ছিল না। প্রচলিত গড়পড়তা ধর্মাচার্যদের সঙ্গে এখানেই তাঁর প্রভেদ। পরম ঔদার্যে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন ধর্মে ধর্মে বিভেদের খড়ির গণ্ডি। সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তাই তিনিই বলতে পেরেছিলেন ‘যত মত তত পথ’। বারাঙ্গনার মধ্যে তিনি সীতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো এক ইংরেজ যুবকের মধ্যে কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঠাকুর অনুভব করেছিলেন, অগণিত ভক্ত তাঁর কাছে আসছে। এঁদের একদল গৃহী, অন্যদল ত্যাগব্রতে দীক্ষিত সন্ন্যাসী। এঁদের দেখার জন্য ব্যাকুল ঠাকুর কেঁদে কেঁদে ডাক ছেড়ে বলেছিলেন, ‘তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে...।’
শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল তিনটি মূল অস্ত্র। অকপট সত্যানুরাগ, নিপীড়িত মানুষের প্রতি অকৃপণ প্রেম এবং যুক্তিবাদে আস্থা। আচারের চোরাবালিতে যে ধর্মের সমাধি ঘটতে চলেছিল, সত্য ও প্রেমের প্রাণোচ্ছল স্রোতোধারায় তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণই। ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অকাতরে বিলিয়ে দিলেন প্রেম, ভক্তি আর মনুষ্যত্ববোধ। তিনি অবতার শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অবতার। নিজেই ভক্তদের বলেছেন তাঁকে যাচাই করে নিতে। বলেছেন, ‘সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তারপরে বিশ্বাস করবি।’ শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করেই স্বামীজি শ্লোক লিখলেন— “ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে/ অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।’’ সব ধর্ম, সব মত, সব পথই সত্য— কোনওটিই ছোট বা তুচ্ছ নয়, কোনওটি বড়ও নয়। সব ধর্মের প্রধান কথা প্রেম-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ্য এবং শান্তি। কূপমণ্ডূকতা বা মৌলবাদের সংকীর্ণতা বহু যোজন দূরে সরিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের জয়ধ্বজা উড়িয়ে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারণ করলেন ভারতীয় ঐতিহ্যের চিরায়ত, সহজ অথচ সুন্দর, সরল অথচ সুউচ্চ-উদার বাণী। বহুমুখী প্রাণবন্ত সেই কথাটির সার: গ্রহণ, সহন এবং সম্মিলন।
তাঁর শক্তির আধার বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠকরা জানেন কাশীপুরে সেদিন কী হয়েছিল! ঠাকুর তাঁকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। স্বামীজির বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়েছিল। পরে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, ‘আজ তোকে সব দিয়ে আমি ফকির হলুম।’ সেই বিবেকানন্দের সাধনার ভিতর দিয়ে ভবতারিণী বাংলার অসংখ্য বীর বিপ্লবী তরুণের মনে প্রলয়ঙ্করী মহাকালী রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে তাঁরা উদ্দীপ্ত, ‘মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে। নিরানন্দে দুঃখে মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।’ তরুণ হৃদয়ে সাধনার ধারা পাল্টে গেল। বাংলায় কালীশক্তি জাগ্রত হল।
বাংলার রক্তক্ষরা বিপ্লব ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে উঠেছিলেন মহাকালী। তাঁর সমগ্র ভাগবতী প্রকৃতি ঝঞ্ঝারুদ্র কর্মের প্রভায় প্রস্ফুরিত, তিনি রয়েছেন ক্ষিপ্রতার জন্য, সাক্ষাৎ সঘন আঘাতে সব পরাভূত করে সম্মুখ আক্রমণের জন্য। অভয়ের ভগবতী মূর্তি রূপে মহাকালী বাংলার যুবসমাজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কালী অনুধ্যান কালানলের মতো জ্বলে উঠল। বাংলার কালীসাধনার নতুন মহিমা প্রকাশ পেল। আদ্যাশক্তি মহামায়া বীর সন্তানের কাছেও ধরা দিলেন। বাংলার এই বীরভাবের সাধনার রূপটি বিবেকানন্দের কথায় ফুটে উঠেছে— ‘যাঁরা প্রকৃত মায়ের ভক্ত, তাঁরা পাথরের মতো শক্ত, সিংহের মত নির্ভীক। মাকে তোমার কথা শুনতে বাধ্য কর। তাঁর কাছে খোসামোদ কি? জবরদস্তি। তিনি সব করতে পারেন।’
বাংলার কালী মমতাময়ী, মুণ্ডমালিনী। স্নেহময়ী, ভয়ঙ্করী। প্রসন্না, ভ্রুকুটিকুটিলা। সন্তানবৎসলা, বীরের আরাধ্যা অসুরদলনী।





 ১১ নভেম্বর বিচারপতি সঞ্জীব খান্না সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে আসীন হবেন। ১০ নভেম্বর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় অবসর নেবেন। আপাতভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং রুটিন একটি প্রক্রিয়া।
১১ নভেম্বর বিচারপতি সঞ্জীব খান্না সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে আসীন হবেন। ১০ নভেম্বর বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় অবসর নেবেন। আপাতভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং রুটিন একটি প্রক্রিয়া।
 সভ্যতার একেবারে আদিযুগ থেকে মানুষ ক্রমেই উত্তরণের পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। এই উত্তরণ আসলে অন্ধকার থেকে আলোয় উৎসারণের প্রক্রিয়া। মানুষের কাছে আলো তাই একটা শক্তি, প্রতীক। জীবনে আলোর উদ্ভাস এনে সে অন্ধকারকে বা অশুভ শক্তিকে দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে।
সভ্যতার একেবারে আদিযুগ থেকে মানুষ ক্রমেই উত্তরণের পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। এই উত্তরণ আসলে অন্ধকার থেকে আলোয় উৎসারণের প্রক্রিয়া। মানুষের কাছে আলো তাই একটা শক্তি, প্রতীক। জীবনে আলোর উদ্ভাস এনে সে অন্ধকারকে বা অশুভ শক্তিকে দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে।


 মাথা নাড়লেন জওহরলাল নেহরু। ‘কাজটা কঠিন। কারণ, আমাদের কাছে কোনও ডেটা নেই। যে ডেভেলপমেন্টই করতে যাই না কেন, সবটাই অন্ধকারে হাতড়ানো।’ তাহলে উপায় কী? সোভিয়েতের ধাঁচে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করতে চান প্রধানমন্ত্রী।
মাথা নাড়লেন জওহরলাল নেহরু। ‘কাজটা কঠিন। কারণ, আমাদের কাছে কোনও ডেটা নেই। যে ডেভেলপমেন্টই করতে যাই না কেন, সবটাই অন্ধকারে হাতড়ানো।’ তাহলে উপায় কী? সোভিয়েতের ধাঁচে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করতে চান প্রধানমন্ত্রী।

 তথাকথিত একটা নাগরিক আন্দোলন বাম দিকে ঘোরাতে না পারার ব্যর্থতা কুরে কুরে খাচ্ছে। তা নিয়েই ‘ফেসবুকের দল’ সিপিএমের অন্দরে এখন হতাশার ঝড়। একটা দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে বিশ্বজোড়া বাংলা বিরোধী কুৎসা, আর চক্রান্ত করেই ওরা ভেবেছিল খেলা বুঝি শেষ।
তথাকথিত একটা নাগরিক আন্দোলন বাম দিকে ঘোরাতে না পারার ব্যর্থতা কুরে কুরে খাচ্ছে। তা নিয়েই ‘ফেসবুকের দল’ সিপিএমের অন্দরে এখন হতাশার ঝড়। একটা দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে বিশ্বজোড়া বাংলা বিরোধী কুৎসা, আর চক্রান্ত করেই ওরা ভেবেছিল খেলা বুঝি শেষ।
 সিপিআই(এমএল)-এর সঙ্গে জোট করে বঙ্গ সিপিএম বুঝিয়ে দিল, ক্রাচ ছাড়া তারা চলতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করার আশায় ২০১৬ সালে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছিল। ২০২১ সালে তৃণমূলের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ভাঙার জন্য হাত মিলিয়েছিল ‘মৌলবাদী’ আইএসএফের সঙ্গে।
সিপিআই(এমএল)-এর সঙ্গে জোট করে বঙ্গ সিপিএম বুঝিয়ে দিল, ক্রাচ ছাড়া তারা চলতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করার আশায় ২০১৬ সালে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছিল। ২০২১ সালে তৃণমূলের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ভাঙার জন্য হাত মিলিয়েছিল ‘মৌলবাদী’ আইএসএফের সঙ্গে।
 কলকাতা পুলিস খারাপ। রাজ্য সরকার খারাপ। সিবিআই খারাপ। সুপ্রিম কোর্ট খারাপ। মিডিয়া খারাপ। শুধু আমরা ভালো। আমাদের যাঁরাই বিরোধিতা করে কিংবা যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করে, তাঁরাই যেন অশিক্ষিত এবং ধর্ষকের সমর্থক। আমাদের ভিন্ন মত যারা প্রকাশ করে, তারা অ্যাভারেজ বুদ্ধির।
কলকাতা পুলিস খারাপ। রাজ্য সরকার খারাপ। সিবিআই খারাপ। সুপ্রিম কোর্ট খারাপ। মিডিয়া খারাপ। শুধু আমরা ভালো। আমাদের যাঁরাই বিরোধিতা করে কিংবা যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করে, তাঁরাই যেন অশিক্ষিত এবং ধর্ষকের সমর্থক। আমাদের ভিন্ন মত যারা প্রকাশ করে, তারা অ্যাভারেজ বুদ্ধির।
 পারসনা নন গ্রাটা! ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী ইসরায়েল কাটৎসের। বলেছেন, ‘রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেইরেসের ইজরায়েলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি ইজরায়েলে ইরানের ঘৃণ্য হামলার দ্ব্যর্থহীন সমালোচনা করতে পারবেন না, তিনি ইজরায়েলের মাটিতে পা রাখতে পারবেন না।’
পারসনা নন গ্রাটা! ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী ইসরায়েল কাটৎসের। বলেছেন, ‘রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেইরেসের ইজরায়েলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি ইজরায়েলে ইরানের ঘৃণ্য হামলার দ্ব্যর্থহীন সমালোচনা করতে পারবেন না, তিনি ইজরায়েলের মাটিতে পা রাখতে পারবেন না।’
 আজকের জমানা সামনে থেকে দেখলে কি রবি ঠাকুর এই শব্দগুলো একটু অদল বদল করে নিতেন? যেমন, প্রার্থনার বদলে ডিমান্ড? কিংবা মন্থনের জায়গায় ব্ল্যাকমেল? উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ, তিনি নিজে ছাড়া তাঁর সৃষ্টি রিক্রিয়েট করার ক্ষমতা কারও নেই।
আজকের জমানা সামনে থেকে দেখলে কি রবি ঠাকুর এই শব্দগুলো একটু অদল বদল করে নিতেন? যেমন, প্রার্থনার বদলে ডিমান্ড? কিংবা মন্থনের জায়গায় ব্ল্যাকমেল? উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ, তিনি নিজে ছাড়া তাঁর সৃষ্টি রিক্রিয়েট করার ক্ষমতা কারও নেই।


 মেঘের আড়ালে নয়, এবার মুখোমুখি। আর জি কর কাণ্ড ছাপিয়ে আগামী এক মাস বঙ্গ রাজনীতি আন্দোলিত হতে চলেছে ৬ বিধানসভা আসনের উপ নির্বাচন ঘিরে। প্রশ্ন করি, এত কুৎসা, অপপ্রচার, সরকারের বদনামের পরও বিরোধীরা ভোট বাড়াতে পারবেন তো?
মেঘের আড়ালে নয়, এবার মুখোমুখি। আর জি কর কাণ্ড ছাপিয়ে আগামী এক মাস বঙ্গ রাজনীতি আন্দোলিত হতে চলেছে ৬ বিধানসভা আসনের উপ নির্বাচন ঘিরে। প্রশ্ন করি, এত কুৎসা, অপপ্রচার, সরকারের বদনামের পরও বিরোধীরা ভোট বাড়াতে পারবেন তো?