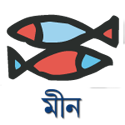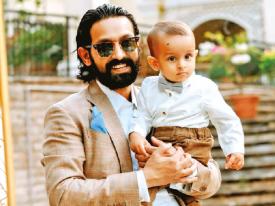জলপথ পরিবহণ কর্মে বিশেষ শুভ। হস্তশিল্পী, হিসাব-শাস্ত্রবিদ প্রমুখের কর্মে উন্নতি ও সুনাম। মানসিক অস্থিরতা থাকবে। ... বিশদ
সাধারণ মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর কথাগুলি বিশ্বাসও করেছেন অনেকে। তবে লক্ষণীয় যে, মিডিয়ার সামনে যেসব মানুষ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁরা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে অবস্থান করেন। এই বাজেটে এক লাফে অনেকখানি আয়কর ছাড়ের যে ঘোষণা শনিবার করা হয়েছে, তা কার্যকর হলে তাঁরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। কর বাবদ যে কয়েক হাজার টাকা তাঁরা বাচাতে পারবেন, তার দু’রকম ব্যবহার সম্ভব—স্বল্প সঞ্চয় এবং ভোগব্যয়। এমনকী সম্পদ সৃষ্টির পক্ষেও সহায়ক হতে পারবে এই অর্থ। যেমন তাঁরা দুই বা চার চাকার গাড়ি ক্রয় করতে পারবেন কিংবা নিতে পারেন বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ইএমআই বাবদ বেশি টাকা পরিশোধের সিদ্ধান্ত। তাঁদের ছেলেমেয়ের শিক্ষাখাতেও অধিক অর্থ খরচের সুযোগ মিলতে পারে। সব মিলিয়ে যে শ্রেণির কথা বলা হচ্ছে, সেই মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত মানুষের সংখ্যা বড়জোর ৮ কোটি। ওষুধ এবং কিছু ভোগ্যপণ্যের দামও আংশিক হ্রাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে চাহিদা কিছুটা বাড়তে পারে এবং উৎপাদন ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আসতে পারে গতি। তবে এই সম্ভাবনাগুলির প্রতিটিই দাঁড়িয়ে আছে একটি ‘যদি’র উপর। ‘যদি’ মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম টানা না-যায়, তবে কয়েক হাজার টাকার করছাড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাস্তবে কিছুই পাবেন না। অগ্নিমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার পর মধ্যবিত্তের হাতে তখন পেন্সিলের বড় কিছুই নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মন পাওয়ার জন্য অভূতপূর্ব কর ছাড়ের রিবেট দিতে গিয়ে কেন্দ্রকে হারাতে হবে বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মত, চড়ের শোধ কান মলেই তুলে নেবে সরকার। যেমন ভর্তুকিতে কোপ ইতিমধ্যেই পড়েছে। সামাজিক পরিষেবা খাতে বাজেট বরাদ্দ কমেছে ১৬ শতাংশ। ৪.৩৮ শতাংশ বরাদ্দ কমানো হয়েছে গৃহনির্মাণে। তফসিলি জাতি ও জনজাতির উন্নয়নে ছাঁটা গিয়েছে ৩ শতাংশ। খাদ্যে ভর্তুকি ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রকল্প (মনরেগা) নিয়ে তীব্র অনীহা দেখিয়েছে এই জনপ্রিয় বাজেট। বাজেটের এই দিকটি প্রদীপের নীচের অন্ধকার বাইকি। এর ফলে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁরা গরিব মানুষ। তাঁরাই জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। অর্থাৎ এই বাজেটের জন্য ৭০-৮০ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে দুর্ভোগে পড়তে পারেন। এরপর আরও একটি আশঙ্কা অর্থনৈতিক মহলকে চিন্তায় রেখেছে যে, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন মেটার পরই মোদি সরকারের নজর পড়তে পারে পেট্রপণ্যের উপর। তারা ফের বাড়িয়ে দিতে পারে রান্নার গ্যাস এবং পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতির দাম। কে না জানে, পেট্রপণ্যের দামবৃদ্ধি পরিবহণ খরচ এবং সমস্ত পণ্যের মূল্যে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
সব মিলিয়ে ‘স্বস্তি’র সাময়িক উচ্ছ্বাস কেটে গেলেই চরম ‘অস্বস্তি’ গ্রাস করতে পারে—সেখানে গরিব আর মধ্যবিত্ত কাউকেই ভিন্ন বন্ধনীতে রাখা সম্ভব হবে না। সবচয়ে বড় প্রশ্ন, বাজেট প্রস্তাবের সবটা কার্যকর হবে তো? বিগত বাজেট বরাদ্দের অনেক টাকাই কিন্তু চলতি অর্থবর্ষে খরচ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেও যে-সরকার ‘ডাবল’ এবং ‘সিঙ্গল’ ইঞ্জিন নামক একটি অবাঞ্ছিত তত্ত্ব আমদানি করতে পারে, সে বৈষম্যের পথ পরিহার করবে, তা কেউ মনে করে না। এই বাজেট প্রস্তাবে প্রকট হয়েছে সেটিও। তৃতীয় মোদি সরকারের ‘প্রাণভোমরা’ বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের খুশি করতে গিয়ে একাধিক বিরোধী রাজ্যের সঙ্গে বঞ্চনা করেছেন মোদি। বঞ্চিত রাজ্যগুলির শীর্ষে রয়েছে বাংলা। মোদিজি, নিশ্চয় এই সত্যটি মাথায় রাখেননি যে বৈষম্যই ভারতের সব রোগের মূলে। প্রদেশে প্রদেশে বিভাজন-বৈষম্য একটি দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ বাংলাসহ কয়েকটি রাজ্য কেন্দ্রীয় নীতির কারণে এগতে না-পারলে, দিনের শেষে, তার মূল্য চোকাতে হবে জাতীয় অর্থনীতিকেই। যে বাজেট প্রস্তাব জাতীয় অর্থনীতিকেই যূপকাষ্ঠে পাঠায়, তাকে নিয়ে গর্বের অবকাশ কোথায়?