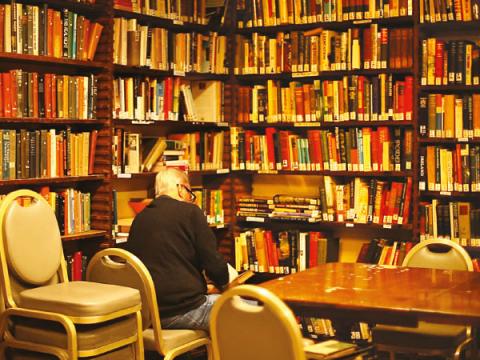কলকাতা, মঙ্গলবার ২৬ নভেম্বর ২০২৪, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
চার বাঙালির হোমিওপ্যাথি চর্চা

সুপ্রিয় নায়েক: সাঁওতাল পরগনার ডাক্তার
শরতের নীল আকাশ। চকচকে কাচের মতো রোদ ছিটকে পড়ছে বাদামি ঘাসে ভরা খোলা জমিতে। তার উপর দিয়ে হন হন করে হেঁটে আসছেন ছোটখাট চেহারার একটি লোক। পরনে ধুতি, গায়ে একখানি ধবধবে চাদর। পায়ে তালতলার মুচির বানানো চটি। মানুষটির দ্রুত হাঁটার ছন্দের সঙ্গে বুঝি যেন তাল রাখতে পারছে না বাতাসও। মানুষটির বয়স প্রায় ষাট। রোদ লেগে গিয়েছে গায়ের রং পুড়ে। চওড়া কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। হাতে একখানি পাথরের বাটি। ভদ্রলোকের নাম বিদ্যাসাগর।
১৮৭৮ সাল। শরীর খারাপ। তাই লখনউ যাওয়ার পথে কয়েকটা দিন কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের বাংলো বাড়িতে এসেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। একদিন সকালের দিকে উধাও হয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রীমশাই তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন, বাড়ির পিছনের দিকের দরজা হাট করে খোলা। নজর পড়ল আলপথ ধরে হেঁটে আসছেন বিদ্যাসাগর। তাঁকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিদ্যাসাগর বললেন, ‘তুই এখানে কেন?’
‘আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন?’
‘ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি করিয়া নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা তো মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না।’
‘ক’তদূর গিয়াছিলেন?’
‘ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে।’
স্বাস্থ্য ফেরানোর চেষ্টায় মাঝেমধ্যে কর্মাটাঁড়ে গিয়ে থাকতেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিশ্রাম নেবেন কী! কর্মাটাঁড়ে গেলেই তাঁর বাংলোয় ভিড় করত অভুক্ত সাঁওতাল রমণী ও পুরুষরা। তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হতো। কেউ অসুস্থ হলেই সেবার দায়িত্ব তুলে নিতেন নিজের কাঁধে! পথ্য দিতেন রোগীর মুখে। করতেন সেবা শুশ্রূষা। শয্যাগত ব্যাধিগ্রস্তের মুখে যত্ন করে ঢেলে দিতেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ।
জানা যায়, হোমিওপ্যাথিতে বিদ্যাসাগরের অগাধ আস্থা ছিল। তাই নিজের গরজে শিখে নিয়েছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। তাঁর সেই শিক্ষা পরবর্তীকালে বাংলায় তো বটেই, ভারতেও হোমিওপ্যাথির প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের হোমিওপ্যাথি শিক্ষার কাহিনিটিও ভারী মজার।
নানা পন্থায় চিকিৎসা করিয়েও বিদ্যাসাগরের দীর্ঘদিনের মাথাব্যথা সারছিল না। অবশেষে বউবাজারের মলিঙ্গা নিবাসী ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে সেরে যায় তাঁর ক্রনিক শিরঃপীড়া। বিদ্যাসাগরের এক ঘনিষ্ঠ ভুগছিলেন তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায়। তাও সেরে যায় হোমিওপ্যাথির বিন্দুপানে। ঘটনাটি সম্ভবত ১৮৬৩ সালের। আশ্চর্য উপশমের পর বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলাল দত্তের কাছে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি এতখানি উৎসাহী হয়েছিলেন যে, বিলেতে থেকে ‘থ্যাকার কোম্পানি’কে অর্ডার দিয়ে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথি বই আনিয়েছিলেন।
পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের ছোট মেয়ের এক দুরারোগ্য অসুখও সেরে উঠেছিল হোমিওপ্যাথিতে। সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় বিদ্যাসাগরের। তাঁর পরামর্শে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হয়েছিলেন।
বিদ্যাসাগর শুনেছিলেন শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা ব্যর্থ! তাই তিনি বেশ কতকগুলি নরকঙ্কাল কেনেন। তাঁকে অ্যানাটমি শেখানোর দায়িত্ব নেন সুকিয়া স্ট্রিট নিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ। নিয়মিত তাঁর বাড়িতেই শিক্ষা নিতে যেতেন বিদ্যাসাগর!
আবার এও শোনা যায়, চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঝগড়া না হলে নাকি রামকৃষ্ণের চিকিৎসক হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিসই শুরু করতেন না!
শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক
১৮৬৩ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমডি পাশ করা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের তখন প্রবল প্রতিপত্তি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এবং চিকিৎসকদের উপর বিষম বিদ্বেষ তাঁর।
একদিন বিদ্যাসাগর এবং মহেন্দ্রবাবু হাইকোর্টের জজ অসুস্থ দ্বারকানাথ মিত্রকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা ফিরছিলেন গাড়িতে। সেই গাড়ির মধ্যেই ঘোরতর বাদানুবাদ শুরু হয় মহেন্দ্রলাল ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে। গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নও। দু’জনের তর্কাতর্কিতে তিনি বলে ওঠেন— ‘মহাশয়! আমাকে নাবাইয়া দেন। আপনাদের বিবাদে আমার কর্ণে তালা লাগিল।’
বিদ্যাসাগরের মতো মহেন্দ্রলালও ছোটবেলায় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন। অল্পবয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে মানুষ হয়েছেন মামারবাড়িতে। মহেন্দ্রলালকেও রাস্তার আলোতেই পড়াশোনা চালাতে হতো। ভয়ঙ্কর অর্থাভাব সত্ত্বেও হেয়ার স্কুল থেকে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন এবং হিন্দু কলেজে পড়তে ঢোকেন। হিন্দু কলেজ থেকে সিনিয়র বৃত্তি লাভ করে ১৮৫৪ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।
বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি ছিলেন একরোখা। নিজের যুক্তিতে অটল। তবু যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রতি খানিক সম্ভ্রমেই সম্ভবত মহেন্দ্রবাবু তাঁর কথা শিরোধার্য করে বলেন— ‘আমি এক্ষণে আর হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিব না; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব ইহার কী গুণ।’ অতঃপর শুরু হয় মহেন্দ্রলালের হোমিওপ্যাথি চর্চা। অল্প দিনেই তিনি এই চিকিৎসা পদ্ধতির যশস্বী হয়ে ওঠেন। তাঁর যশঃপ্রভায় বিদেশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের প্রতিপত্তি পড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে!
তবে, কোনও কোনও পণ্ডিতের দাবি, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তর্কের ওই ঘটনার পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা মহেন্দ্রলালকে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র নিয়ে কৌতূহলী করে তুলেছিল।
এক প্রবন্ধে ডাঃ সরকার নিজেই জানিয়েছিলেন, সমালোচনা লেখার জন্য তিনি ডাক্তার মরগ্যানের লেখা ‘ফিলোজফি অব হোমিওপ্যাথি’ বইটি পড়ছিলেন। বইটি পড়তে পড়তেই ক্রমশ তাঁর ‘হোমিওপ্যাথি’কে বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। হোমিওপ্যাথি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করেন। প্রত্যক্ষ করেন রোগীর উপর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল। নিজেও কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি করেন ও রোগীর উপর প্রয়োগ করেন। হোমিওপ্যাথি নিয়ে কাজ শুরু করায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। তবে মহেন্দ্রলাল ছিলেন একবগ্গা। ফলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালানোর পাশাপাশি ১৮৬৮ সালের প্রথম দিক থেকে ‘ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন’ নামে চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন।
১৮৭৬ সালে তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠা হয় ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স’। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারেই কাজ করে নোবেল প্রাইজ পান সি ভি রমন।
বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার কারণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়েও মহেন্দ্রলালের কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তার এই স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ রয়েছে ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে লেখা দু’টি চিঠিতে। সেখানে তিনি হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা পদ্ধতি সহ ভিন্ন ধারার চিকিৎসা দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন— ‘হ্যানিম্যান বিশ্বাস করেন, রোগমুক্তির একটিমাত্র পথ, অন্য পথ নেই। এই ধরনের ভাবনা কিন্তু ঠিক নয়। বিভিন্ন পথেও রোগ মুক্তি ঘটে।’ ম্যালেরিয়া হলে তখন হ্যানিম্যানের পথ নয়, বরং কুইনাইনই একমাত্র চিকিৎসা বলে তাঁর মত ছিল। একইরকমভাবে পৃথক ধারার চিকিৎসকদের কাছেও তাঁর নিবেদন ছিল, হোমিওপ্যাথিকে অগ্রাহ্য করার কোনও কারণ নেই। তাঁর কাছে কোন পথে চিকিৎসা হচ্ছে তা জরুরি নয়, সর্বাগ্রে জরুরি রোগীর পীড়ার উপশম। তাই স্বল্প খরচের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি যে, দেশের দরিদ্র মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠবে, তা তাঁর বিশ্লেষণধর্মী মন নির্ণয় করে ফেলেছিল।
ডাঃ সরকার পরমহংসদেবকে রানি রাসমণির জামাই মথুরামোহন বিশ্বাসের সময় থেকেই চিনতেন। সেই সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবুর শাঁখারিটোলার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন আলাপ সেইভাবে জমেনি অবশ্য।
শ্যামপুকুরে শিবু ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে আসার অনুরোধ করা হয়। সেটা ১৮৮৫ সালের শেষদিক। সেখানেই পরমহংসদেবের ভক্তদলের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশ ঘোষের মতো ব্যক্তিকে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হন।
ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মহেন্দ্রলালের সম্পর্ক অন্য মাত্রা পায়। তিনিই হয়ে ওঠেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান চিকিৎসক। অবস্থা এমনটাই দাঁড়ায় যে, ‘প্রত্যহ দুই প্রহরের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন’... তাঁর সঙ্গে তর্কও জুড়তেন নানা গূঢ় বিষয় নিয়ে। আবার প্রয়োজন অনুসারে পরীক্ষা করে দেখতেন রামকৃষ্ণদেবকে। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োগ করতেন ‘নাক্স ভোমিকা’, ‘কোনিয়াম’, ‘লাইকোপোডিয়াম ২০০’। পরমহংসের সংস্পর্শে নীরস, গম্ভীর এই চিকিৎসকের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্যামপুকুরের বাড়ি থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেও নিয়মিত যেতেন মহেন্দ্রলাল।
কবির ডাক্তারি
ডাক্তারদের প্রতি বরাবর দুর্বল ছিলেন কবিগুরু। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু। গভীর সখ্যতা ছিল ডাঃ নীলরতন সরকারের সঙ্গে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহীও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেই লিখেছেন— ‘চেষ্টা করলে ভালো ডাক্তার হতে পারতুম।’ একসময় হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদের গভীরে প্রবেশ করেছেন। শেষদিকে পড়েছেন বায়োকেমিক শাস্ত্রও। ১৯০০ সালের কথা। এক চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথি প্রীতির কথা জানা যায়— ‘আমার ছোট ছেলে (শমীন্দ্রনাথ) কয়েকদিন জ্বর ও কাশিতে ভুগিতেছিল। আমি তাহাকে অ্যাকোনাইট-৩০ ও বেলাডোনা-৩০ পর্যায়ক্রমে দিয়া আরাম করিয়া তুলিয়াছি।’ লন্ডন থেকে ছোট মেয়ে মীরা দেবীকে লিখছেন, ‘তোর খোকার Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস।... তাড়াতাড়ি একজিমা সারানো ভালো নয়। সালফা ২৬০ আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস... একজিমা যদি বসে গিয়ে থাকে সালফার সেই দোষ নিবারণ করবে।’
‘রবি ঠাকুরের ডাক্তারি’ বইটিতে ‘চিকিৎসক’ হিসেবে তাঁর বেশ কয়েকবার অব্যর্থভাবে রোগ সারানোর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন— ১৯১৫ সালের মে মাসের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চলে গিয়েছেন রামগড় পাহাড়ের ‘হৈমন্তী’ বাড়িতে। কবিপুত্র সদ্য রথীন্দ্রনাথ কিনেছেন ওই বাড়ি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পেয়েছেন সাম্মানিক ‘ডক্টরেট’ উপাধি। রামগড়ের ঠিকানায় যা যা চিঠি পৌঁছচ্ছে, সেই সব চিঠির খামের উপর লেখা থাকছে ‘ডক্টর রবীন্দ্রনাথ টেগোর’। ব্যস! রামগড়ের পোস্টমাস্টার তাই দেখে কবিকে ডাক্তার ঠাওড়ালেন এবং ফলাও করে সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন, কলকাতা থেকে এক বড় ডাক্তার এসেছেন। সরল পাহাড়ি মানুষগুলোও বিশ্বাস করে বসল সে কথা।
ওদিকে হয়েছেটা কী, কয়েকদিন আগেই হৈমন্তীর ছাদ সারাই করতে এসেছিল এক ছুতোর। হঠাৎ একদিন তার অস্বাভাবিক রকমের কাঁপুনি দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ ততদিনে মেটেরিয়া মেডিকা গুলে খেয়েছেন। দেখেই বুঝতে পারলেন কাঠ মিস্ত্রি ‘সেন্ট ভিটাস ডান্স’ রোগে আক্রান্ত। হোমিওপ্যাথি ওষুধও দিলেন তাকে। কয়েকদিন পর তার ওই ব্যামো সম্পূর্ণ সেরে গেল। এদিকে, দাবানলের মতো সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে। দলে দলে পাহাড়ি মানুষ তাদের রোগ সারাতে আসতে শুরু করল কবির কাছে। রোজ সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টা রোগী দেখতেন তিনি। দিতেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ।
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায় রয়েছে আরও একটি ঘটনা। রবীন্দ্রজীবনী রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাই আক্রান্ত হয়েছিলেন ইরিসিপেলাম অসুখে। জটিল এক চর্মব্যাধি। অত্যন্ত ছোঁয়াচে। রবীন্দ্রনাথ সেই রোগীকেও দিলেন ওষুধ। এমন এক জটিল রোগে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ওষুধে জাদুর মতো কাজ হল।
ডাক্তারি করা নিয়ে বিশেষ গৌরব বোধ করতেন কবি। তিনি মনে করতেন পারিশ্রমিক নেন না বলেই কেউ তাঁকে বড় চিকিৎসক হিসেবে মানতে চায় না! পশুপতি ডাক্তারকে একবার বলেওছিলেন সে কথা— ‘আমি ফি নিই না, তাই ডাক্তার নই। যদি মোটা ফি নিতাম তাহলে সবাই বলত, এ একজন মস্ত বড় ডাক্তার!’
১৯৩৮ সাল। সবে কালিম্পং থেকে ফিরেছেন শান্তিনিকেতনে। সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দার্জিলিং থেকে ফিরেছেন তাঁদের বরাহনগরের বাড়িতে। সপ্তাহখানেক বাদে মারাত্মক জ্বরে পড়লেন রানি মহলানবিশ (ভালো নাম নির্মলকুমারী)। ‘প্রথমদিনেই উঠে গেল একশো সাড়ে চার-পাঁচ...’। দু’দিন যায়, তিনদিন যায়, জ্বর নামে না। প্রশান্তচন্দ্রের মেজমামা ডাক্তার নীলরতন সরকার এলেন দেখতে। ধরা পড়ল টাইফয়েড। টাইফয়েড সারানোর কোনও অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তখনও ছিল না। ওদিকে রানির শরীর খুব খারাপ। ...এমন সময় রানির অবস্থা জানিয়ে প্রশান্তচন্দ্র চিঠি দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। পরের দিন দুপুরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হাজির হলেন বরাহনগরে। পকেট থেকে শিশি বের করে ওষুধ মুখে দিয়ে বললেন, এই ওষুধ দিয়ে গেলুম। তিন ঘণ্টার পর থেকে তোমার জ্বর নামতে থাকবে। ৭ দিন বাদে তোমার জ্বর নর্মাল হবে।’ ঘটনাক্রমে হলও তাই। সকলেই অবাক।
কবির সেক্রেটারি অনিল চন্দের স্ত্রী রানি চন্দের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ‘গুরুদেবের গানের বা কবিতার প্রশংসার চেয়ে হাজারগুণ খুশি হতেন তিনি, কেউ এসে যদি বলতো যে গুরুদেবের ওষুধে তার অমুক অসুখটা সেরে গেছে।’
শিলাইদহে বসবাসকালীন সময়েও মাঝিদের শরীর খারাপ হলে তিনিই হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন। গরিব প্রজারাও কেউ কেউ ওষুধ নিতে আসত। আসলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাধি পীড়িত মানুষের কথা তাঁকে ভাবাত। আর একবারের কথা, বোলপুরের আশপাশে অনেক সাঁওতাল গ্রাম ছিল। ওই গ্রামগুলোতে দেখা দিল এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধি। এক সাঁওতাল মহিলা কবিকে বললেন, ‘বুড়োবাবা, তুই আমার ছেলের জন্য ওষুধ দে। ছেলেটার বড্ড জ্বর।’ কবির তখন কলকাতা যাওয়ার তাড়া। তা সত্ত্বেও সাঁওতাল মায়ের চোখে ব্যাকুল আর্তি এড়াবেন কী করে কবি? খুলে বসলেন হোমিওপ্যাথির বই। ছেলের কী কী কষ্ট, কী উপসর্গ জেনে নিয়ে ওষুধের বাক্স থেকে একটা মিলিয়ন ডাইল্যুশনের পুরিয়া গুঁজে দিলেন সাঁওতাল মায়ের হাতে। বললেন ‘যা এখনি গিয়ে ছেলেটাকে খাইয়ে আয়। দেরি করিস না।’ মহিলা চলে যাওয়ার পর রওনা হলেন কবি। মনে তাঁর ওই জ্বরের রোগীকে নিয়ে তীব্র উদ্বেগ। অথচ কলকাতা না গেলেও নয়। রবীন্দ্রনাথের মনে হল, ‘যেন পালিয়ে যাচ্চি।’ সপ্তাহ দু’য়েক পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে দেখা হল সেই সাঁওতাল মায়ের সঙ্গে। মহিলা বললেন— ‘ছেলেটা ভালো হয়ে গেছে বাবা। তোর ওষুধ একটাই দিয়েছিলাম। কী যে তোর ওষুধ!’
কথাশিল্পীর হোমিওপ্যাথি
চিকিৎসক হয়ে দেশের উন্নতি করবেন এমনতরো ভাবনা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছিল বললে কি বাড়িয়ে বলা হবে? কেরানির চাকরি ছেড়ে ১৯১৬ সালের মে মাসে বর্মা ছেড়ে কলকাতা চলে এলেন শরৎচন্দ্র । বাসা করলেন বাজেশিবপুরে।
বিস্তর টাকা খরচ করে ভালো ভালো বই কিনে হোমিওপ্যাথি বিদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলেন। একবার এক ঘনিষ্ঠকে বলেছিলেন, ‘বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেল কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর— পেসেন্ট খুঁজতে লাগলুম। বাড়ীতে যারা আসে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগেস করি তাদের কিছু অসুখ হয়েছে কি না। সবাই বলে না কোনও অসুখই হয়নি। বেজায় দমে গেলুম— কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে! যাই হোক অনেক চেষ্টাচরিত্তিরের পর বাড়ীর পিছনদিকে এক গয়লানীর অসুখ হতে একদিন আমার কাছে এলো। খুব ভালো করে দেখেশুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু’একদিন পরেই এসে আবার ওষুধ নিয়ে যেও বাছা— আর যদি কেউ জানাশুনো থাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো— অমনি ওষুধ দেব। কিন্তু সেই যে সে গেল আর আসে না। একদিন বাড়ির পিছন দিকের জানলাটি খুলে দেখি সে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। তাকে ডেকে বললুম, হাঁ বাছা— তোমার সেই যে কি অসুখ করেছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে—আর আসো না কেন? গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছি আর দরকার নেই। যা বাবা— এত পড়লুম অমনি চিকিৎসা করব ওষুধ দেব তাতেও রুগী জুটল না, যাও বা জুটল তাকে আর চিকিৎসা করতে হলো না, এক ওষুধে সেরে গেল!’
এটা যদি মজার গল্প হয় তাহলে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের কোমল দিকটিও প্রকাশ করার প্রয়োজন। পাণিত্রাস গোবিন্দপুরের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর বিয়ে হয়েছে। কবি নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: ‘শরৎচন্দ্র, তাঁর দিদি ও ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখুয্যে মহাশয়ের অনুরোধে পাণিত্রাসে সামতাবেড় গ্রামে বাটী নির্মাণ করে বসবাস করেছিলেন।’ রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড় এলাকাটি ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত। বেছে বেছে সেখানেই বাড়ি করলেন কেন শরৎচন্দ্র? কারণ বাড়ি করলে গ্রামের লোকেরা সকলেই কিছু না কিছু কাজ পাবে। তাতে তাদের রোজগার হবে। কিছুটা হলেও কষ্ট লাঘব হবে!
‘সামতাবেড় দরিদ্র গ্রাম। একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না সহজে। শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা যত্ন করে শিখেছিলেন দরিদ্রের সেবা করবার জন্য।’
ঠিক এই জায়গাতেই কী অদ্ভুত মিল বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের। প্রত্যেকেই হোমিপ্যাথি শিখেছেন, জেনেছেন— তা পসার জমাতে নয়, তাঁরা জানতেন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অপুষ্টিলাঞ্ছিত স্বদেশের মানুষের কথা। অর্থাভাবের কারণে সেইসব দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের থেকে যদি অন্য চিকিৎসা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর হোমিওপ্যাথি খানিক বাঁচার আশা দিতে পারে— তাতে আপত্তি কোথায়?
শরতের নীল আকাশ। চকচকে কাচের মতো রোদ ছিটকে পড়ছে বাদামি ঘাসে ভরা খোলা জমিতে। তার উপর দিয়ে হন হন করে হেঁটে আসছেন ছোটখাট চেহারার একটি লোক। পরনে ধুতি, গায়ে একখানি ধবধবে চাদর। পায়ে তালতলার মুচির বানানো চটি। মানুষটির দ্রুত হাঁটার ছন্দের সঙ্গে বুঝি যেন তাল রাখতে পারছে না বাতাসও। মানুষটির বয়স প্রায় ষাট। রোদ লেগে গিয়েছে গায়ের রং পুড়ে। চওড়া কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। হাতে একখানি পাথরের বাটি। ভদ্রলোকের নাম বিদ্যাসাগর।
১৮৭৮ সাল। শরীর খারাপ। তাই লখনউ যাওয়ার পথে কয়েকটা দিন কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের বাংলো বাড়িতে এসেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। একদিন সকালের দিকে উধাও হয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রীমশাই তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন, বাড়ির পিছনের দিকের দরজা হাট করে খোলা। নজর পড়ল আলপথ ধরে হেঁটে আসছেন বিদ্যাসাগর। তাঁকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিদ্যাসাগর বললেন, ‘তুই এখানে কেন?’
‘আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন?’
‘ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি করিয়া নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা তো মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না।’
‘ক’তদূর গিয়াছিলেন?’
‘ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে।’
স্বাস্থ্য ফেরানোর চেষ্টায় মাঝেমধ্যে কর্মাটাঁড়ে গিয়ে থাকতেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিশ্রাম নেবেন কী! কর্মাটাঁড়ে গেলেই তাঁর বাংলোয় ভিড় করত অভুক্ত সাঁওতাল রমণী ও পুরুষরা। তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হতো। কেউ অসুস্থ হলেই সেবার দায়িত্ব তুলে নিতেন নিজের কাঁধে! পথ্য দিতেন রোগীর মুখে। করতেন সেবা শুশ্রূষা। শয্যাগত ব্যাধিগ্রস্তের মুখে যত্ন করে ঢেলে দিতেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ।
জানা যায়, হোমিওপ্যাথিতে বিদ্যাসাগরের অগাধ আস্থা ছিল। তাই নিজের গরজে শিখে নিয়েছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। তাঁর সেই শিক্ষা পরবর্তীকালে বাংলায় তো বটেই, ভারতেও হোমিওপ্যাথির প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের হোমিওপ্যাথি শিক্ষার কাহিনিটিও ভারী মজার।
নানা পন্থায় চিকিৎসা করিয়েও বিদ্যাসাগরের দীর্ঘদিনের মাথাব্যথা সারছিল না। অবশেষে বউবাজারের মলিঙ্গা নিবাসী ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে সেরে যায় তাঁর ক্রনিক শিরঃপীড়া। বিদ্যাসাগরের এক ঘনিষ্ঠ ভুগছিলেন তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায়। তাও সেরে যায় হোমিওপ্যাথির বিন্দুপানে। ঘটনাটি সম্ভবত ১৮৬৩ সালের। আশ্চর্য উপশমের পর বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলাল দত্তের কাছে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি এতখানি উৎসাহী হয়েছিলেন যে, বিলেতে থেকে ‘থ্যাকার কোম্পানি’কে অর্ডার দিয়ে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথি বই আনিয়েছিলেন।
পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের ছোট মেয়ের এক দুরারোগ্য অসুখও সেরে উঠেছিল হোমিওপ্যাথিতে। সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় বিদ্যাসাগরের। তাঁর পরামর্শে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হয়েছিলেন।
বিদ্যাসাগর শুনেছিলেন শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা ব্যর্থ! তাই তিনি বেশ কতকগুলি নরকঙ্কাল কেনেন। তাঁকে অ্যানাটমি শেখানোর দায়িত্ব নেন সুকিয়া স্ট্রিট নিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ। নিয়মিত তাঁর বাড়িতেই শিক্ষা নিতে যেতেন বিদ্যাসাগর!
আবার এও শোনা যায়, চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঝগড়া না হলে নাকি রামকৃষ্ণের চিকিৎসক হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিসই শুরু করতেন না!
শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক
১৮৬৩ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমডি পাশ করা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের তখন প্রবল প্রতিপত্তি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এবং চিকিৎসকদের উপর বিষম বিদ্বেষ তাঁর।
একদিন বিদ্যাসাগর এবং মহেন্দ্রবাবু হাইকোর্টের জজ অসুস্থ দ্বারকানাথ মিত্রকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা ফিরছিলেন গাড়িতে। সেই গাড়ির মধ্যেই ঘোরতর বাদানুবাদ শুরু হয় মহেন্দ্রলাল ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে। গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নও। দু’জনের তর্কাতর্কিতে তিনি বলে ওঠেন— ‘মহাশয়! আমাকে নাবাইয়া দেন। আপনাদের বিবাদে আমার কর্ণে তালা লাগিল।’
বিদ্যাসাগরের মতো মহেন্দ্রলালও ছোটবেলায় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন। অল্পবয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে মানুষ হয়েছেন মামারবাড়িতে। মহেন্দ্রলালকেও রাস্তার আলোতেই পড়াশোনা চালাতে হতো। ভয়ঙ্কর অর্থাভাব সত্ত্বেও হেয়ার স্কুল থেকে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন এবং হিন্দু কলেজে পড়তে ঢোকেন। হিন্দু কলেজ থেকে সিনিয়র বৃত্তি লাভ করে ১৮৫৪ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।
বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি ছিলেন একরোখা। নিজের যুক্তিতে অটল। তবু যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রতি খানিক সম্ভ্রমেই সম্ভবত মহেন্দ্রবাবু তাঁর কথা শিরোধার্য করে বলেন— ‘আমি এক্ষণে আর হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিব না; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব ইহার কী গুণ।’ অতঃপর শুরু হয় মহেন্দ্রলালের হোমিওপ্যাথি চর্চা। অল্প দিনেই তিনি এই চিকিৎসা পদ্ধতির যশস্বী হয়ে ওঠেন। তাঁর যশঃপ্রভায় বিদেশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের প্রতিপত্তি পড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে!
তবে, কোনও কোনও পণ্ডিতের দাবি, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তর্কের ওই ঘটনার পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা মহেন্দ্রলালকে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র নিয়ে কৌতূহলী করে তুলেছিল।
এক প্রবন্ধে ডাঃ সরকার নিজেই জানিয়েছিলেন, সমালোচনা লেখার জন্য তিনি ডাক্তার মরগ্যানের লেখা ‘ফিলোজফি অব হোমিওপ্যাথি’ বইটি পড়ছিলেন। বইটি পড়তে পড়তেই ক্রমশ তাঁর ‘হোমিওপ্যাথি’কে বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। হোমিওপ্যাথি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করেন। প্রত্যক্ষ করেন রোগীর উপর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল। নিজেও কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি করেন ও রোগীর উপর প্রয়োগ করেন। হোমিওপ্যাথি নিয়ে কাজ শুরু করায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। তবে মহেন্দ্রলাল ছিলেন একবগ্গা। ফলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালানোর পাশাপাশি ১৮৬৮ সালের প্রথম দিক থেকে ‘ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন’ নামে চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন।
১৮৭৬ সালে তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠা হয় ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স’। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারেই কাজ করে নোবেল প্রাইজ পান সি ভি রমন।
বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার কারণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়েও মহেন্দ্রলালের কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তার এই স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ রয়েছে ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে লেখা দু’টি চিঠিতে। সেখানে তিনি হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা পদ্ধতি সহ ভিন্ন ধারার চিকিৎসা দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন— ‘হ্যানিম্যান বিশ্বাস করেন, রোগমুক্তির একটিমাত্র পথ, অন্য পথ নেই। এই ধরনের ভাবনা কিন্তু ঠিক নয়। বিভিন্ন পথেও রোগ মুক্তি ঘটে।’ ম্যালেরিয়া হলে তখন হ্যানিম্যানের পথ নয়, বরং কুইনাইনই একমাত্র চিকিৎসা বলে তাঁর মত ছিল। একইরকমভাবে পৃথক ধারার চিকিৎসকদের কাছেও তাঁর নিবেদন ছিল, হোমিওপ্যাথিকে অগ্রাহ্য করার কোনও কারণ নেই। তাঁর কাছে কোন পথে চিকিৎসা হচ্ছে তা জরুরি নয়, সর্বাগ্রে জরুরি রোগীর পীড়ার উপশম। তাই স্বল্প খরচের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি যে, দেশের দরিদ্র মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠবে, তা তাঁর বিশ্লেষণধর্মী মন নির্ণয় করে ফেলেছিল।
ডাঃ সরকার পরমহংসদেবকে রানি রাসমণির জামাই মথুরামোহন বিশ্বাসের সময় থেকেই চিনতেন। সেই সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবুর শাঁখারিটোলার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন আলাপ সেইভাবে জমেনি অবশ্য।
শ্যামপুকুরে শিবু ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে আসার অনুরোধ করা হয়। সেটা ১৮৮৫ সালের শেষদিক। সেখানেই পরমহংসদেবের ভক্তদলের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশ ঘোষের মতো ব্যক্তিকে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হন।
ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মহেন্দ্রলালের সম্পর্ক অন্য মাত্রা পায়। তিনিই হয়ে ওঠেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান চিকিৎসক। অবস্থা এমনটাই দাঁড়ায় যে, ‘প্রত্যহ দুই প্রহরের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন’... তাঁর সঙ্গে তর্কও জুড়তেন নানা গূঢ় বিষয় নিয়ে। আবার প্রয়োজন অনুসারে পরীক্ষা করে দেখতেন রামকৃষ্ণদেবকে। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োগ করতেন ‘নাক্স ভোমিকা’, ‘কোনিয়াম’, ‘লাইকোপোডিয়াম ২০০’। পরমহংসের সংস্পর্শে নীরস, গম্ভীর এই চিকিৎসকের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্যামপুকুরের বাড়ি থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেও নিয়মিত যেতেন মহেন্দ্রলাল।
কবির ডাক্তারি
ডাক্তারদের প্রতি বরাবর দুর্বল ছিলেন কবিগুরু। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু। গভীর সখ্যতা ছিল ডাঃ নীলরতন সরকারের সঙ্গে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহীও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেই লিখেছেন— ‘চেষ্টা করলে ভালো ডাক্তার হতে পারতুম।’ একসময় হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদের গভীরে প্রবেশ করেছেন। শেষদিকে পড়েছেন বায়োকেমিক শাস্ত্রও। ১৯০০ সালের কথা। এক চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথি প্রীতির কথা জানা যায়— ‘আমার ছোট ছেলে (শমীন্দ্রনাথ) কয়েকদিন জ্বর ও কাশিতে ভুগিতেছিল। আমি তাহাকে অ্যাকোনাইট-৩০ ও বেলাডোনা-৩০ পর্যায়ক্রমে দিয়া আরাম করিয়া তুলিয়াছি।’ লন্ডন থেকে ছোট মেয়ে মীরা দেবীকে লিখছেন, ‘তোর খোকার Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস।... তাড়াতাড়ি একজিমা সারানো ভালো নয়। সালফা ২৬০ আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস... একজিমা যদি বসে গিয়ে থাকে সালফার সেই দোষ নিবারণ করবে।’
‘রবি ঠাকুরের ডাক্তারি’ বইটিতে ‘চিকিৎসক’ হিসেবে তাঁর বেশ কয়েকবার অব্যর্থভাবে রোগ সারানোর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন— ১৯১৫ সালের মে মাসের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চলে গিয়েছেন রামগড় পাহাড়ের ‘হৈমন্তী’ বাড়িতে। কবিপুত্র সদ্য রথীন্দ্রনাথ কিনেছেন ওই বাড়ি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পেয়েছেন সাম্মানিক ‘ডক্টরেট’ উপাধি। রামগড়ের ঠিকানায় যা যা চিঠি পৌঁছচ্ছে, সেই সব চিঠির খামের উপর লেখা থাকছে ‘ডক্টর রবীন্দ্রনাথ টেগোর’। ব্যস! রামগড়ের পোস্টমাস্টার তাই দেখে কবিকে ডাক্তার ঠাওড়ালেন এবং ফলাও করে সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন, কলকাতা থেকে এক বড় ডাক্তার এসেছেন। সরল পাহাড়ি মানুষগুলোও বিশ্বাস করে বসল সে কথা।
ওদিকে হয়েছেটা কী, কয়েকদিন আগেই হৈমন্তীর ছাদ সারাই করতে এসেছিল এক ছুতোর। হঠাৎ একদিন তার অস্বাভাবিক রকমের কাঁপুনি দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ ততদিনে মেটেরিয়া মেডিকা গুলে খেয়েছেন। দেখেই বুঝতে পারলেন কাঠ মিস্ত্রি ‘সেন্ট ভিটাস ডান্স’ রোগে আক্রান্ত। হোমিওপ্যাথি ওষুধও দিলেন তাকে। কয়েকদিন পর তার ওই ব্যামো সম্পূর্ণ সেরে গেল। এদিকে, দাবানলের মতো সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে। দলে দলে পাহাড়ি মানুষ তাদের রোগ সারাতে আসতে শুরু করল কবির কাছে। রোজ সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টা রোগী দেখতেন তিনি। দিতেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ।
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায় রয়েছে আরও একটি ঘটনা। রবীন্দ্রজীবনী রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাই আক্রান্ত হয়েছিলেন ইরিসিপেলাম অসুখে। জটিল এক চর্মব্যাধি। অত্যন্ত ছোঁয়াচে। রবীন্দ্রনাথ সেই রোগীকেও দিলেন ওষুধ। এমন এক জটিল রোগে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ওষুধে জাদুর মতো কাজ হল।
ডাক্তারি করা নিয়ে বিশেষ গৌরব বোধ করতেন কবি। তিনি মনে করতেন পারিশ্রমিক নেন না বলেই কেউ তাঁকে বড় চিকিৎসক হিসেবে মানতে চায় না! পশুপতি ডাক্তারকে একবার বলেওছিলেন সে কথা— ‘আমি ফি নিই না, তাই ডাক্তার নই। যদি মোটা ফি নিতাম তাহলে সবাই বলত, এ একজন মস্ত বড় ডাক্তার!’
১৯৩৮ সাল। সবে কালিম্পং থেকে ফিরেছেন শান্তিনিকেতনে। সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দার্জিলিং থেকে ফিরেছেন তাঁদের বরাহনগরের বাড়িতে। সপ্তাহখানেক বাদে মারাত্মক জ্বরে পড়লেন রানি মহলানবিশ (ভালো নাম নির্মলকুমারী)। ‘প্রথমদিনেই উঠে গেল একশো সাড়ে চার-পাঁচ...’। দু’দিন যায়, তিনদিন যায়, জ্বর নামে না। প্রশান্তচন্দ্রের মেজমামা ডাক্তার নীলরতন সরকার এলেন দেখতে। ধরা পড়ল টাইফয়েড। টাইফয়েড সারানোর কোনও অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তখনও ছিল না। ওদিকে রানির শরীর খুব খারাপ। ...এমন সময় রানির অবস্থা জানিয়ে প্রশান্তচন্দ্র চিঠি দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। পরের দিন দুপুরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হাজির হলেন বরাহনগরে। পকেট থেকে শিশি বের করে ওষুধ মুখে দিয়ে বললেন, এই ওষুধ দিয়ে গেলুম। তিন ঘণ্টার পর থেকে তোমার জ্বর নামতে থাকবে। ৭ দিন বাদে তোমার জ্বর নর্মাল হবে।’ ঘটনাক্রমে হলও তাই। সকলেই অবাক।
কবির সেক্রেটারি অনিল চন্দের স্ত্রী রানি চন্দের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ‘গুরুদেবের গানের বা কবিতার প্রশংসার চেয়ে হাজারগুণ খুশি হতেন তিনি, কেউ এসে যদি বলতো যে গুরুদেবের ওষুধে তার অমুক অসুখটা সেরে গেছে।’
শিলাইদহে বসবাসকালীন সময়েও মাঝিদের শরীর খারাপ হলে তিনিই হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন। গরিব প্রজারাও কেউ কেউ ওষুধ নিতে আসত। আসলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাধি পীড়িত মানুষের কথা তাঁকে ভাবাত। আর একবারের কথা, বোলপুরের আশপাশে অনেক সাঁওতাল গ্রাম ছিল। ওই গ্রামগুলোতে দেখা দিল এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধি। এক সাঁওতাল মহিলা কবিকে বললেন, ‘বুড়োবাবা, তুই আমার ছেলের জন্য ওষুধ দে। ছেলেটার বড্ড জ্বর।’ কবির তখন কলকাতা যাওয়ার তাড়া। তা সত্ত্বেও সাঁওতাল মায়ের চোখে ব্যাকুল আর্তি এড়াবেন কী করে কবি? খুলে বসলেন হোমিওপ্যাথির বই। ছেলের কী কী কষ্ট, কী উপসর্গ জেনে নিয়ে ওষুধের বাক্স থেকে একটা মিলিয়ন ডাইল্যুশনের পুরিয়া গুঁজে দিলেন সাঁওতাল মায়ের হাতে। বললেন ‘যা এখনি গিয়ে ছেলেটাকে খাইয়ে আয়। দেরি করিস না।’ মহিলা চলে যাওয়ার পর রওনা হলেন কবি। মনে তাঁর ওই জ্বরের রোগীকে নিয়ে তীব্র উদ্বেগ। অথচ কলকাতা না গেলেও নয়। রবীন্দ্রনাথের মনে হল, ‘যেন পালিয়ে যাচ্চি।’ সপ্তাহ দু’য়েক পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে দেখা হল সেই সাঁওতাল মায়ের সঙ্গে। মহিলা বললেন— ‘ছেলেটা ভালো হয়ে গেছে বাবা। তোর ওষুধ একটাই দিয়েছিলাম। কী যে তোর ওষুধ!’
কথাশিল্পীর হোমিওপ্যাথি
চিকিৎসক হয়ে দেশের উন্নতি করবেন এমনতরো ভাবনা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছিল বললে কি বাড়িয়ে বলা হবে? কেরানির চাকরি ছেড়ে ১৯১৬ সালের মে মাসে বর্মা ছেড়ে কলকাতা চলে এলেন শরৎচন্দ্র । বাসা করলেন বাজেশিবপুরে।
বিস্তর টাকা খরচ করে ভালো ভালো বই কিনে হোমিওপ্যাথি বিদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলেন। একবার এক ঘনিষ্ঠকে বলেছিলেন, ‘বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেল কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর— পেসেন্ট খুঁজতে লাগলুম। বাড়ীতে যারা আসে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগেস করি তাদের কিছু অসুখ হয়েছে কি না। সবাই বলে না কোনও অসুখই হয়নি। বেজায় দমে গেলুম— কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে! যাই হোক অনেক চেষ্টাচরিত্তিরের পর বাড়ীর পিছনদিকে এক গয়লানীর অসুখ হতে একদিন আমার কাছে এলো। খুব ভালো করে দেখেশুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু’একদিন পরেই এসে আবার ওষুধ নিয়ে যেও বাছা— আর যদি কেউ জানাশুনো থাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো— অমনি ওষুধ দেব। কিন্তু সেই যে সে গেল আর আসে না। একদিন বাড়ির পিছন দিকের জানলাটি খুলে দেখি সে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। তাকে ডেকে বললুম, হাঁ বাছা— তোমার সেই যে কি অসুখ করেছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে—আর আসো না কেন? গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছি আর দরকার নেই। যা বাবা— এত পড়লুম অমনি চিকিৎসা করব ওষুধ দেব তাতেও রুগী জুটল না, যাও বা জুটল তাকে আর চিকিৎসা করতে হলো না, এক ওষুধে সেরে গেল!’
এটা যদি মজার গল্প হয় তাহলে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের কোমল দিকটিও প্রকাশ করার প্রয়োজন। পাণিত্রাস গোবিন্দপুরের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর বিয়ে হয়েছে। কবি নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: ‘শরৎচন্দ্র, তাঁর দিদি ও ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখুয্যে মহাশয়ের অনুরোধে পাণিত্রাসে সামতাবেড় গ্রামে বাটী নির্মাণ করে বসবাস করেছিলেন।’ রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড় এলাকাটি ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত। বেছে বেছে সেখানেই বাড়ি করলেন কেন শরৎচন্দ্র? কারণ বাড়ি করলে গ্রামের লোকেরা সকলেই কিছু না কিছু কাজ পাবে। তাতে তাদের রোজগার হবে। কিছুটা হলেও কষ্ট লাঘব হবে!
‘সামতাবেড় দরিদ্র গ্রাম। একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না সহজে। শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা যত্ন করে শিখেছিলেন দরিদ্রের সেবা করবার জন্য।’
ঠিক এই জায়গাতেই কী অদ্ভুত মিল বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের। প্রত্যেকেই হোমিপ্যাথি শিখেছেন, জেনেছেন— তা পসার জমাতে নয়, তাঁরা জানতেন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অপুষ্টিলাঞ্ছিত স্বদেশের মানুষের কথা। অর্থাভাবের কারণে সেইসব দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের থেকে যদি অন্য চিকিৎসা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর হোমিওপ্যাথি খানিক বাঁচার আশা দিতে পারে— তাতে আপত্তি কোথায়?
গ্রাফিক্স : সোমনাথ পাল
সহযোগিতায় : স্বাগত মুখোপাধ্যায়
সহযোগিতায় : স্বাগত মুখোপাধ্যায়
এখনকার দর
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৩.৫৩ টাকা | ৮৫.২৭ টাকা |
| পাউন্ড | ১০৪.৪৮ টাকা | ১০৮.২০ টাকা |
| ইউরো | ৮৬.৮২ টাকা | ৯০.১৭ টাকা |
*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে