কর্ম, বিদ্যা ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। আয় ব্যয় ক্ষেত্রে সমতার অভাব। স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও আঘাতযোগ থাকায় ... বিশদ
‘বৌমা... নিশ্চিত করে বলছি, বর্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বিভূতিভূষণ উপন্যাস লিখেছেন। দু’হাজার বছর আগে জন্মালে উনি উপনিষদ রচনা করতেন।’ মৃত্যুর আগে টেলিফোনে বিভূতি-পত্নী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একথা বলেছিলেন স্বয়ং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বিভূতিভূষণ! নামটা শুনলেই মনে পড়ে যায় গোপালনগর, বনগাঁ, ভাগলপুর, ঘাটশিলার কথা। তিনি নিজেকে ভাবতেন ‘বেজুকভ’। রুশ সাহিত্যিক তলস্তয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর নায়ক। বাইরে নরম-কোমল হলেও ভিতরে বেশ শক্ত মনের মানুষ ছিলেন। কখনও কখনও আপনজনের কাছেও উদাসীন হয়ে যেতেন। ছোটবেলা কিংবা চাকরি জীবনের শুরুতেও লেখক হওয়ার কথা ভাবেননি। কিন্তু হয়ে গেলেন।
লেখায় ‘উপেক্ষিতা’
বিভূতিভূষণ তখন হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পাঁচুগোপাল (যতীন্দ্রমোহন রায়) নামের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। দু’জনে আলাদা ঘরে ভাড়া থাকতেন। স্কুলের বাইরে বেশিরভাগ সময়ই কাটত একসঙ্গে। বয়স অল্প হলেও পাঁচুগোপাল লেখালিখি করেন। মাঝেমধ্যেই বিভূতিভূষণকে লেখার প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রতিবারই এড়িয়ে যান তিনি। কানে তোলেন না। উপায়ান্তর না দেখে বিকল্প রাস্তা নিলেন পাঁচুগোপাল। তাঁরই কারসাজিতে হঠাৎই একদিন হরিনাভি স্কুলের দেওয়ালজুড়ে বিভূতিভূষণের নামে লেখা হল বিজ্ঞাপন। ‘শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে... শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে উপন্যাস।’ বিজ্ঞাপন দেখে হতবাক বিভূতিভূষণ। এরপর থেকে রাস্তায়, বাজারে, স্কুলে তাঁর কাছে সকলেরই এক প্রশ্ন ‘কবে বেরচ্ছে উপন্যাস?’ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ। শেষপর্যন্ত রাগ করে লিখে ফেললেন আস্ত একটা গল্প। ডাকযোগে পাঠিয়েও দিলেন কলকাতার একটি মাসিক পত্রিকার ঠিকানায়। ভেবেছিলেন লেখাটি মনোনীত হবে না। কিন্তু কয়েক মাস পরে পত্রিকা দপ্তর থেকে এল একটি খাম। ভিতরে ছোট্ট চিঠি, ‘আপনার রচনা মনোনীত হয়েছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।’ অবশেষে ‘প্রবাসী’ (মাঘ, ১৩২৮) পত্রিকায় প্রকাশিত হল বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প ‘উপেক্ষিতা’। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন, ‘ছেলেটি বোধহয় ঈশ্বরের দূত হয়ে সেদিন আমার কাছে এসেছিল। ওই বিজ্ঞাপন কাণ্ডটি না ঘটলে কোনওদিন লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম না।’
গৌরীদেবীর মৃত্যু ও প্রেমপত্র
বসিরহাটের মেয়ে গৌরীদেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিভূতিভূষণের। সালটা ১৯১৯। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হয় গৌরীদেবীর। বিভূতিভূষণও পড়াশোনায় ইতি টানেন। শিক্ষকের চাকরি নেন হুগলির জাঙ্গিপাড়া মাইনর স্কুলে। অতঃপর ওই চাকরি ছেড়ে চলে যান হরিনাভি স্কুলে। সাহিত্যিক হিসেবে নাম হওয়ার পরে মাঝেমধ্যে প্রেমপত্র পেতেন বিভূতিভূষণ। মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে বসে সখা নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে এসব নিয়ে রসিকতা করতেও ছাড়তেন না।
হরিনাভিতে তাঁর এলোমেলো ঘরদোর গুছিয়ে দিত এক বিবাহযোগ্য ব্রাহ্মণ কন্যা। আড়ালে আবডালে তাঁর খেয়ালও রাখত। এমন আদর-যত্ন ভালোই লাগত বিভূতিভূষণের। ‘আমি আপনার দাসী’ সম্বোধন করে সে কয়েকটি প্রেমপত্রও পাঠিয়েছিল। মেয়েটির উপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লেও বিভূতিভূষণ শেষপর্যন্ত পালিয়ে আসেন। কারণ, মেয়েটি ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর সমগোত্রীয় ছিল না। সাতপাঁচ ভেবে হরিনাভি স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি।
নিষিদ্ধ পল্লিতে মায়ের খোঁজে
বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই প্রথমবার কলকাতায় পা রাখা বিভূতিভূষণের। বয়স তখন ৪ কি ৫। অভাবী মহানন্দ ছেলেকে নিয়ে উঠেছিলেন নিষিদ্ধ পল্লির এক বস্তিতে। সেই ঘরের পাশেই থাকতেন এক মহিলা। তাঁর সঙ্গে এতটাই ভাব হয়েছিল যে, গল্পে, আদর-যত্নে মায়ের অভাব পূরণ হয়ে যেত। তাঁকেই মা ভেবে নিয়েছিলেন ছোট্ট বিভূতিভূষণ।
মধ্য বয়সে হঠাৎই একদিন ওই মায়ের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। তিনি খুঁজতে যান ওই নিষিদ্ধ পল্লিতে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ধরেন অল্পবয়সি চার-পাঁচ জন দেহোপজীবিনী। সকলেই চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে। লেখক বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন, মাতৃসম ওই মহিলাকে খুঁজতে এসেছেন। কিন্তু দেহোপজীবিনীরা তা শুনতে নারাজ। সেযাত্রায় পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি।
বিভূতিভূষণ ও নীরদচন্দ্র
একইসঙ্গে এম এ এবং ল’ পড়ার সময় নীরদচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ। বিভূতিভূষণ নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। নীরদচন্দ্র উচ্চ মধ্যবিত্তের গরিমায় গর্বিত। কিন্তু সাহিত্যপ্রেমকে কেন্দ্র করে ক্রমে গাঢ় হয় এই বন্ধুত্ব। নীরদচন্দ্র অবিবাহিত, বিভূতিভূষণ বিপত্নীক। প্রায়ই সন্ধ্যায় একইসঙ্গে সময় কাটাতেন। তিন বছরের ছোট-বড় দু’জনের বন্ধুত্বের কথা নীরদচন্দ্র লিখেছেন ‘দ্য হ্যান্ড, গ্রেট অ্যানার্ক!’ গ্রন্থে। তিনি শুধু লেখা শেষ করার জন্য তাগাদা দেননি, ‘পথের পাঁচালী’ বই আকারে ছাপানোর জন্য প্রকাশকও খুঁজে দিয়েছিলেন। আসলে বিভূতিভূষণকে খুবই ভালোবাসতেন নীরদচন্দ্র। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে যেতেন বিভূতিভূষণ।
পরবর্তীতে নীরদচন্দ্র বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও সখ্য গড়ে ওঠে বিভূতিভূষণের। নীরদচন্দ্র লিখেছেন ‘... কিন্তু বৈঠকখানায় না বসিয়া তিনি নির্বিকার, শান্তভাবে বিড়ি টানিতে টানিতে সোজা তাঁহার শয়ন কক্ষে চলিয়া যাইতেন এবং সূচী-শিল্প করা চাদরের উপর বসিয়া, দুর্গন্ধময় নিম্ন মধ্যবিত্ত গন্ধ ছড়াইতেন। আমার স্ত্রী তাঁহাকে বিড়ি ফেলিতে বাধ্য করিয়া, ভৃত্যকে দিয়া এক প্যাকেট খ্যাতনামা সিগারেট আনাইয়া দিতেন।’
দশ বছরের সংসার
১৯৩৯ সাল। ইছামতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেলেন জাহ্নবী। বোনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন বিভূতিভূষণ। কথাটি জানাজানি হতেই দু’দিন পর ছুটে এলেন ফরিদপুরের ছয়গাঁও নিবাসী ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা রমাদেবী। উদ্দেশ্য অটোগ্রাফ নেওয়া। মনেপ্রাণে ভারাক্রান্ত সাহিত্যিক। তবু অটোগ্রাফ দেওয়ার পাশাপাশি খাতায় লিখে দিলেন, ‘গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু’।
মেয়েটিকে ভালো লেগে গেল বিভূতিভূষণের। তাঁদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল বছর ঊনত্রিশের। তবু চিঠি চালাচালির মাধ্যমে সম্পর্ক ক্রমশ গাঢ় হতে লাগল। শেষমেশ একদিন রমাদেবীই বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। নিজেকে সংযত রেখে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন বিভূতিভূষণ... নিজের বয়সের কথা, প্রথম স্ত্রী গৌরীদেবীর কথা। কিন্তু রমাদেবী নাছোড়বান্দা। বিভূতিভূষণকে জানালেন, ‘আপনাকে মাত্র দশ দিনের জন্য স্বামী হিসেবে পেলে আমি ধন্য।’ অবশেষে ১৯৪০ সালের ৩ ডিসেম্বর বিয়ে হল দু’জনের। বিয়ের সাত বছর পর জন্ম হল একমাত্র পুত্র তারাদাসের। দশ বছরের মাথায়, ১৯৫০ সালে বিভূতিভূষণ নিজেই চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। তার আগেই অবশ্য একটা চিঠিতে রমাদেবীকে লিখেছিলেন, ‘এখন মনে হচ্ছে হয়তো অনেক জন্মের বন্ধন ছিল তোমার সঙ্গে—নয়তো এমন হবে কেন? কল্যাণী, তুমি আমার অনেক দিনের পরিচিতা, এবার এত দেরিতে দেখা হল কেন জানিনে, আরও কিছুকাল আগে দেখা হলে ভাল হতো।’
রবীন্দ্রনাথ নিজে ডেকেছিলেন
‘পথের পাঁচালী’ লেখা শেষ হল। পড়ে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ। ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লিখলেন, ‘তাঁর লেখায় পাড়াগাঁয়ের কথা, সেও অচেনা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।’ উপন্যাস নিয়ে মতামত দিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিভূতিভূষণকে ডেকেছিলেন বরানগরে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে।
১৯৪১ সাল। বাংলা ক্যালেন্ডারে দিনটা ২২ শ্রাবণ। বিভূতিভূষণ তখন শিক্ষকতা করছেন ধর্মতলার কাছে, খেলাতচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে। মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে বসে শুনলেন, রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ। খানিক বাদেই খবর এল, মারা গিয়েছেন কবিগুরু। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পৌঁছলেন জোড়াসাঁকোয়। তখন প্রচণ্ড ভিড় আর ঠেলাঠেলি। বিভূতিভূষণকে শোকাতুর জনতা ঠেলতে ঠেলতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে পাঠিয়ে দিল। অনেক চেষ্টার পর রবীন্দ্রনাথকে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সেদিনই বনগাঁর বাড়িতে ফিরে যান। ট্রেনে জানলার ধারে বসে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের উপরে নীলাকাশ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল—‘গগনে গগনে নবনব দেশে রবি/ নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি।’
কল্যাণীর বিভূতিভূষণ
জন্মের পর বিভূতিভূষণকে তাঁর বাবা-মা ডাকতেন ‘খোকা’ বলে। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে অপুকে ‘খোকা’ নামে ডাকার মধ্যে দিয়ে সেই ধারা স্পষ্ট। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনের অনেকটা অংশ কেটেছে মুরাতিপুরে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, মুরাতিপুর জায়গাটা আসলে কোথায়? এখন যেখানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, অতীতে তারই নাম ছিল মুরাতিপুর। এখানেই মামার বাড়িতে মৃণালিনী দেবীর কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ। দিনটা ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। বাবা মহানন্দ দিনলিপির পাতায় লিখেছেন, ‘শুক্লপক্ষ ১৩০১ সাল, ২৮শে ভাদ্র, বুধবার দিবা সাড়ে দশ ঘণ্টার সময় আমার বিভূতিভূষণ পুত্রের জন্ম হয় মুরাতিপুর গ্রামে।’ প্রাথমিক পাঠও শুরু সেখানে, বিপিন মাস্টারের পাঠশালায়। ‘পথের পাঁচালী’তে গুরুমশাইয়ের আসল নাম প্রসন্ন মোদক। ছোটবেলায় তাঁর পাঠশালাতেও যেতেন বিভূতিভূষণ। দুই মামা, শরৎকুমার ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাঁধে চেপে ঘুরতেন। বড় হয়েও বারবার ছুটে এসেছেন জন্মভূমিতে। স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘আজ সকালে বনগাঁ থেকে ট্রেনে বার হয়ে রানাঘাটে সাড়ে দশটায় শান্তিপুর লোকাল ধরলুম। দোলের মেলায় আসতে হল বেলা সাড়ে বারোটায়। দুপুরের রোদে বাঁশবাগান আমার বড় ভালো লাগে—আর এইসব বাঁশবাগানের সঙ্গে আমার আশৈশব সম্বন্ধ।’
প্রতি বছর বিভূতিভূষণের জন্মদিনে তাঁর বারাকপুরের বাড়িতে সাহিত্যসভা হয়। ইছামতীর ঘাটে বসে বিভূতিমেলা। দূর-দূরান্ত থেকে দোকানিরা এসে দোকান পাতেন। ছোটদের খেলনা, পাঁপড় ভাজা, জিলিপির রেকাবি ঘিরে ভিড় থাকে দিনভর। তাছাড়া যাত্রাগান, পুতুল নাচ, সার্কাস এসব তো আছেই। কিন্তু ক’জন জানে বিভূতিভূষণের শৈশব-কৈশোরের মুরাতিপুরের কথা? গৌরীদেবীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরও একাধিকবার তিনি এসেছেন এখানে। বিভূতিভূষণ নিজেই লিখেছেন, ‘মামার বাড়ি গিয়ে নিচুতলার দিকে দরজা খুলে ছাদের উপর গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে ছাদের ওপারে। নীচের ছোট ঘরটা বা যে ঘরে গৌরী বসে পান সাজত, সে সব বেড়িয়ে এলুম।’
এখন আর তাঁর মামার বাড়ির কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু জায়গাটিকে চিহ্নিত করেছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে ১৯৯৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, বিভূতিভূষণের জন্মদিনে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ওই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় সেখানে। বসে আলোচনাসভা, সঙ্গীতের আসর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ভাবতে অবাক লাগে, বিভূতিভূষণ মারা গেলেন ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর। ঠিক দশ বছর পর, ১ নভেম্বরই পত্তন হয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের।
পত্নী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘কল্যাণী’ নামে ডাকতেন বিভূতিভূষণ। তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন সেই স্ত্রীর নামেই নিজের জন্মভিটেয় একদিন গড়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়? এটা কি নিছকই কাকতালীয়? নাকি যুগ-যুগান্তরের অতীন্দ্রিয় ভালোবাসার অমোঘ যোগ!
পথের পাঁচালী এবং...
নৈঃশব্দ্যের ভাষা চিনতেন তিনি। পথে হাটে ছড়িয়ে থাকা বনচালতে, বনকলমি, সোঁদালি, তিত্তিরাজের ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে পেতেন। ‘আরণ্যক’-এ লিখেছেন, ‘চাঁদের ফলা যখন বাড়ে কমে, তখন জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম শব্দ হয়।’ ‘দৃষ্টি প্রদীপ’ উপন্যাসে আবার— ‘নীল আকাশের দেবতা, যার ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়...।’ ডাকে নিয়মিত আসা ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফি’ ও ‘ওয়াইল্ড ওয়ার্ল্ড’ পড়ে লিখে ফেলেছিলেন ‘চাঁদের পাহাড়’।
বাবা মহানন্দ মহাআনন্দে ঘুরে বেড়াতেন। কথকতার সূত্রে মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা—এমনকী পেশোয়ারেও। সেই স্বভাব পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। গাছের ডালে বসে আকাশের বদলাতে থাকা রং দেখতেন। গভীর রাতে দেখতেন নিকষ কালো আকাশ। পথের সৌন্দর্যই তাঁর মনে প্রকৃতির প্রতি প্রেম জাগিয়ে তুলেছিল। প্রকৃতির সঙ্গে কোথাও যেন আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলেছিলেন। অনেকে তাঁকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বললে কিছুতেই রাজি হননি তিনি। বলতেন, ‘আমি কেন কারও মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে যাব? যেতে হলে সরাসরিই যাব।’
‘পথের পাঁচালী’ যখন লেখা শুরু করেন, তখন বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার হাত দিয়েই উপন্যাসটির কথা ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। পরে তো সত্যজিৎ রায় ‘পথের পাঁচালী’-র হাত ধরে আন্তর্জাতিক হয়েছেন। উপন্যাসটি ছাপার আগে বিভূতিভূষণ ঠিক করেছিলেন পাণ্ডুলিপিটি দেখাবেন রবীন্দ্রনাথকে। সঙ্গে চাইবেন আশীর্বাদ। সেই মতো জমিদারির সেরেস্তা থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতা যাওয়ার কথা। ট্রেন ধরার আগে ভাগলপুরের নির্জন পথে দেখলেন আট-দশ বছরের এক কিশোরীকে। বিভূতিভূষণের মনে হয়েছিল, ওই কিশোরীর মনের ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে একটা ব্যথাভরা জগৎ। রবীন্দ্রনাথের কাছে আর যাওয়া হল না। জমিদারির সেরেস্তায় ফিরে ছিঁড়ে ফেললেন পাণ্ডুলিপি। নতুন করে লিখতে বসলেন ‘পথের পাঁচালী’। অপুর সঙ্গে এই উপন্যাসে চলে এল দুর্গা। সাদা কাশবনের মধ্যে অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার ছবি বাঙালি জীবনে নস্টালজিক হয়ে রইল।
কল্যাণীতে বিভূতিভূষণের মূর্তি উন্মোচনে এসে পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘সন্ধেবেলা বাবা আমাকে কোলে বসিয়ে নক্ষত্র চেনাতেন। দুপুরে কাঁধে চড়িয়ে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন ইছামতী নদীতে।’ বিভূতিভূষণকে টানত আষাঢ়ু গ্রামের সোনাডাঙার মাঠ। এখানেই রাঙি গায়ের বাছুর খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল অপু-দুর্গা। অপুদের গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর থেকে ট্রেনে কাশী যাওয়ার পথে মাঝেরপাড়ায় ডিসট্যান্স সিগন্যালখানা মনে করিয়ে দেবে অযত্ন অবহেলায় মরে যাওয়া পাড়াগেঁয়ে মেয়ে দুর্গার কথা। ‘অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?’ নস্টালজিয়ায় ভেসে উঠবে অপুর মনের না বলা কথা, ‘আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি। ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।’
অঙ্কন : সুব্রত মাজী





 কবি, গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীতকার... কোনও বিশেষণই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি সলিল চৌধুরী। শতাব্দী পেরিয়েও বাঙালি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে তাঁর গান। জন্মশতবর্ষের সূচনায় ‘গুরুবন্দনা’য় কলম ধরলেন দেবজ্যোতি মিশ্র
কবি, গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীতকার... কোনও বিশেষণই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি সলিল চৌধুরী। শতাব্দী পেরিয়েও বাঙালি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে তাঁর গান। জন্মশতবর্ষের সূচনায় ‘গুরুবন্দনা’য় কলম ধরলেন দেবজ্যোতি মিশ্র



 ‘ইফ হি উইনস’, এই শিরোনামেই টাইম ম্যাগাজিন গত মে মাসে সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। সেই সংখ্যায় সাংবাদিক এরিক কোর্টেলেসা জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে বহুযোজন এগিয়ে গিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
‘ইফ হি উইনস’, এই শিরোনামেই টাইম ম্যাগাজিন গত মে মাসে সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। সেই সংখ্যায় সাংবাদিক এরিক কোর্টেলেসা জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে বহুযোজন এগিয়ে গিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
 এই গ্রুপটাকে সবাই একটু ভয় পায়। কলেজের মধ্যে এই চারজন সর্বদাই একসঙ্গে থাকে। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে চলে আসে দুপুর গড়াতেই। আর সেখানেই তাদের ঘোরাফেরা সবথেকে বেশি। হুড খোলা একটা মাহিন্দ্রা জিপ চালায় যে, তার আসল নাম বলকারান ব্রার।
এই গ্রুপটাকে সবাই একটু ভয় পায়। কলেজের মধ্যে এই চারজন সর্বদাই একসঙ্গে থাকে। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে চলে আসে দুপুর গড়াতেই। আর সেখানেই তাদের ঘোরাফেরা সবথেকে বেশি। হুড খোলা একটা মাহিন্দ্রা জিপ চালায় যে, তার আসল নাম বলকারান ব্রার।
 ভয়ে হোক বা ভক্তিতে, মা কালীর মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। যে কারণে কেরেস্তানি কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি সাহেবের লেখা পদেও ‘শ্যামা সর্বনাশী’কে পাওয়া যায়, শোনা যায় ‘জয় কালীর ডঙ্কা’। আবার ত্রিপুরার নারায়ণপুরের মৃজা হুসেন আলিকে জয় কালীর নামে যমকেও তাচ্ছিল্য করতে দেখি।
ভয়ে হোক বা ভক্তিতে, মা কালীর মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। যে কারণে কেরেস্তানি কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি সাহেবের লেখা পদেও ‘শ্যামা সর্বনাশী’কে পাওয়া যায়, শোনা যায় ‘জয় কালীর ডঙ্কা’। আবার ত্রিপুরার নারায়ণপুরের মৃজা হুসেন আলিকে জয় কালীর নামে যমকেও তাচ্ছিল্য করতে দেখি।
 বিজয়ার থেকেই ধীরে ধীরে দিনগুলো, রাতগুলো কেমন অদ্ভুত ঝিমধরা ক্লান্ত লাগে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যেন এবার আরও অনেক কিছু করার ছিল, জীবনপাত্র উছলিয়া ভরার ছিল। ভরা হল না।
বিজয়ার থেকেই ধীরে ধীরে দিনগুলো, রাতগুলো কেমন অদ্ভুত ঝিমধরা ক্লান্ত লাগে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যেন এবার আরও অনেক কিছু করার ছিল, জীবনপাত্র উছলিয়া ভরার ছিল। ভরা হল না।
 ১৯৮৬। তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। ছুটিতে দু’বেলা আর অন্যান্য দিন সন্ধ্যায় পড়তে বসা— এই ছিল রোজের রুটিন। পুজোর অপেক্ষায় থাকতাম সারা বছর। কারণ, আমাদের বাড়িতে নিয়ম ষষ্ঠী থেকে নবমী বই ছোঁয়া যাবে না। দশমীর দিন যাত্রা করে আবার পড়া শুরু।
১৯৮৬। তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। ছুটিতে দু’বেলা আর অন্যান্য দিন সন্ধ্যায় পড়তে বসা— এই ছিল রোজের রুটিন। পুজোর অপেক্ষায় থাকতাম সারা বছর। কারণ, আমাদের বাড়িতে নিয়ম ষষ্ঠী থেকে নবমী বই ছোঁয়া যাবে না। দশমীর দিন যাত্রা করে আবার পড়া শুরু।
 মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা! বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মহাকাব্য—সর্বত্র তাঁর মহিমার জয়গান। মতভেদও কম নেই। আর তা শুধু আবির্ভাব নয়, গাত্রবর্ণ নিয়েও। বেদ-পুরাণের বর্ণনায় দেবী গৌরবর্ণা, স্বর্ণবর্ণা, পীতবর্ণা, অতসীবর্ণা।
মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা! বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মহাকাব্য—সর্বত্র তাঁর মহিমার জয়গান। মতভেদও কম নেই। আর তা শুধু আবির্ভাব নয়, গাত্রবর্ণ নিয়েও। বেদ-পুরাণের বর্ণনায় দেবী গৌরবর্ণা, স্বর্ণবর্ণা, পীতবর্ণা, অতসীবর্ণা।
 মহালয়ার ভোর। ঘুম থেকে উঠেই ঘরে চালিয়ে দিয়েছি ‘বীরেনবাবু স্পেশাল’। বেশ জোরে। খানিক পরেই দরজায় টোকা। খুলতেই দেখি, আমার ডানপাশের ঘরের জোসেফ ও বাঁ পাশের ঘর থেকে ফাউস্টো ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকল দু’জনে।
মহালয়ার ভোর। ঘুম থেকে উঠেই ঘরে চালিয়ে দিয়েছি ‘বীরেনবাবু স্পেশাল’। বেশ জোরে। খানিক পরেই দরজায় টোকা। খুলতেই দেখি, আমার ডানপাশের ঘরের জোসেফ ও বাঁ পাশের ঘর থেকে ফাউস্টো ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকল দু’জনে।

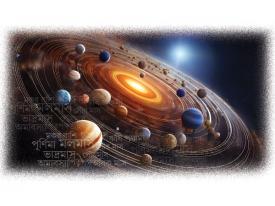 জিন্স পরিহিতা রীতিমতো আধুনিকা বললেন, ‘ঠাকুরমশাই, গৃহপ্রবেশে কোনও ত্রুটি রাখতে চাই না। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হলে আমাদের খুব সুবিধা হয়।’ অফিসের ফোন আসায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন সঙ্গী যুবক। এবার ফোনটা মিউট করে সুবেশ ছেলেটি বললেন, ‘তারপরেই আসলে আবার আমাদের অস্ট্রেলিয়া ফিরতে হবে তো!
জিন্স পরিহিতা রীতিমতো আধুনিকা বললেন, ‘ঠাকুরমশাই, গৃহপ্রবেশে কোনও ত্রুটি রাখতে চাই না। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হলে আমাদের খুব সুবিধা হয়।’ অফিসের ফোন আসায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন সঙ্গী যুবক। এবার ফোনটা মিউট করে সুবেশ ছেলেটি বললেন, ‘তারপরেই আসলে আবার আমাদের অস্ট্রেলিয়া ফিরতে হবে তো!
 সারা বাড়ি আনন্দে গমগম করছে। আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়ে যেন উৎসবের হাট বসেছে। বাড়ির একমাত্র ছেলে শুভদীপের বিয়ে। বিয়ের দিন সবাই সেজেগুজে প্রস্তুত। এখনই বর বেরবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাবা তাড়া দিচ্ছে শুভদীপকে। ‘তাড়াতাড়ি বেরো। এতটা পথ যেতে হবে। সময়মতো পৌঁছতে না পারলে সমস্যা হয়ে যাবে।’
সারা বাড়ি আনন্দে গমগম করছে। আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়ে যেন উৎসবের হাট বসেছে। বাড়ির একমাত্র ছেলে শুভদীপের বিয়ে। বিয়ের দিন সবাই সেজেগুজে প্রস্তুত। এখনই বর বেরবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাবা তাড়া দিচ্ছে শুভদীপকে। ‘তাড়াতাড়ি বেরো। এতটা পথ যেতে হবে। সময়মতো পৌঁছতে না পারলে সমস্যা হয়ে যাবে।’


































































